গণতন্ত্র- রাজনৈতিক গোষ্ঠীতন্ত্র ও গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ by রেহমান সোবহান
স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে এ রকম জাতীয় সংসদ নির্বাচন খুব কমই হয়েছে, যার প্রক্রিয়া বা ফলাফলের বৈধতা প্রশ্নের মুখোমুখি হয়নি।
গণতান্ত্রিক
অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সাম্রাজ্যবাদী শাসকের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামের
মধ্য দিয়ে জন্মগ্রহণকারী একটি দেশের জন্য এ রকম নজির বেদনাদায়ক। এই দেশটির
জন্মের পর থেকে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি দেশের স্থপতি ও তাঁর প্রধান রাজনৈতিক
সহকর্মীদের হত্যাকাণ্ড, সামরিক শাসকদের ক্ষমতা দখল এবং ক্ষমতা চিরস্থায়ী
করার উদ্দেশ্যে একের পর এক স্বৈরতান্ত্রিক শাসকের নির্বাচনী ব্যবস্থার
অপব্যবহার। ওই স্বৈরশাসকদের শেষজনকে উৎখাতের জন্য ১৯৯০ সালের শেষ দিকে দেশে
যে জাতীয় রাজনৈতিক সংহতি গড়ে ওঠে, তাকে দেখা হয়েছিল দ্বিতীয় স্বাধীনতা
হিসেবে।
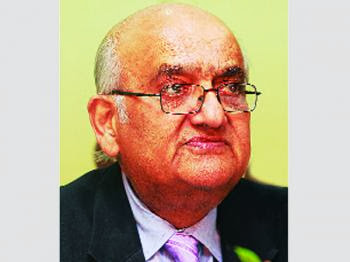
মনে করা হয়েছিল, একটি নতুন গণতান্ত্রিক পুনর্জাগরণের সুযোগ সৃষ্টি হলো। ধারণা করা হয়েছিল, স্বৈরতন্ত্রের তিক্ত অভিজ্ঞতার বদৌলতে এবার আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অধিকতর টেকসই রূপ নেবে। আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)—এ প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলকে নিয়ে একটি প্রকৃত দ্বিদলীয় ব্যবস্থার আবির্ভাব আমাদের আশা বাড়িয়ে দিয়েছিল। এই দল দুুটি স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে পরিপক্বতা অর্জন করেছে। উভয়ের ছিল শক্তিশালী রাজনৈতিক গণভিত্তি। সম্প্রদায় ও জাতিগত বৈচিত্র্যপূর্ণ ও আঞ্চলিকভাবে বিভক্ত দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় আমরা একটি মূলত সমজাতীয় সমাজব্যবস্থা পেয়েছি। এ বিষয়টি গণতন্ত্রের ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বাড়তি আশাবাদের সঞ্চার করেছিল। শেষত, ১৯৯৬ সালে অস্থায়ীভাবে নির্বাচন পরিচালনার জন্য সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে যে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়, তা বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামরত দেশগুলোর জন্য বাংলাদেশের বড় উপহার হিসেবে বিবেচনা করা হতে থাকে।
বাংলাদেশের আদলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা চালু হয়েছে নেপাল ও পাকিস্তানে। আর শ্রীলঙ্কাসহ অন্যান্য অঞ্চলের কয়েকটি দেশ এ ধরনের সরকার চালু করা যায় কি না, তা খতিয়ে দেখছে। পাকিস্তানে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পার্লামেন্ট নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে বেলুচিস্তানের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে। এতে ক্ষমতাসীন দল পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) পরাজিত ও নওয়াজ শরিফের নেতৃত্বাধীন প্রধান বিরোধী দল মুসলিম লিগ (পিএমএল-এন) বিজয়ী হয়। নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন নওয়াজ শরিফ। সব বিচারেই ওই নির্বাচন আপাতদৃষ্টিতে কোনো ধরনের দৃশ্যমান সামরিক প্রভাব ছাড়াই অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে।
গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের পর দুই দশকে পথভ্রষ্ট পরিস্থিতির ধারাবাহিকতায় আমরা আমাদের রাজনৈতিক সম্পদগুলোকে বড় দায়ে রূপান্তরিত করেছি, যা আমাদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে টেকসই রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করছে। আজ আমাদের একসময়ের ঈর্ষণীয় দ্বিদলীয় ব্যবস্থা একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠীতন্ত্রে পরিণত হয়েছে, যার অনমনীয়তা রুয়ান্ডার হুতু ও তুতসিদের মধ্যকার বিভেদের তুলনায় কোনো অংশে কম নয়। ওই দুটি পক্ষের তিক্ত বিরোধের চূড়ান্ত পরিণতি ছিল ভয়াবহ জাতিগত রক্তপাত। আমরা, বাংলাদেশিরা, যারা আত্মপরিচয়ের বিভেদ একেবারেই কম বলে নিজেদের নিয়ে গর্ব করতাম, তারাই বছর বছর প্রধান দুই দলের মধ্যে রাজনৈতিক বিভক্তিকে তীব্রতর করেছি। এই রাজনৈতিক গোষ্ঠীতন্ত্র আমাদের সামাজিক জীবনেও ঢুকে পড়েছে, যেখানে দুই দলের সদস্যরা (যাঁদের সামাজিক ও শিক্ষাগত প্রেক্ষাপট মূলত অভিন্ন) পরস্পরের বিয়েশাদি এমনকি শেষকৃত্যেও কমই যোগ দিয়ে থাকেন।
নিজ নিজ দলকে তিন দশকের বেশি সময় ধরে নেতৃত্ব দিচ্ছেন আওয়ামী লীগ ও বিএনপির শীর্ষ দুই নেতা। তাঁরা দুই দশকের বেশি সময় ধরে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সংলাপ দূরে থাক, কোনো রাজনৈতিক আলাপচারিতায়ও অংশগ্রহণ না করার মাধ্যমে সব রাজনৈতিক ইতিহাসের বই ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাঠ্যবইয়ে নিজেদের নাম অন্তর্ভুক্ত করেছেন। দুই গোষ্ঠীপ্রধানের মধ্যে বিভেদের এই সুকঠিন লৌহ যবনিকার কারণে সংশ্লিষ্ট দুটি দলের মধ্যে স্বাভাবিক রাজনৈতিক যোগাযোগেরও সব চেষ্টা ব্যাহত হয়েছে। দল দুটি এখন নিজ নিজ শীর্ষ নেতার অনুমতি ছাড়া পরস্পরের সঙ্গে সাধারণ রাজনৈতিক কথাবার্তা বলতেও শঙ্কিত বোধ করে, আনুষ্ঠানিক আলোচনার তো প্রশ্নই ওঠে না।
এই বিভক্তির গভীরতা এত বেশি যে রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর মানে বিদায়ী দলটির জন্য কেবল ক্ষমতা হারানোই নয়, বরং ‘বিজয়ীরই সব পাওয়ার’ প্রচলিত রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে অর্থনৈতিক সুযোগ হারানোও বটে। তবে অর্থনৈতিক জীবিকা হারানোই একমাত্র বিপদ নয়, বরং এর সঙ্গে যোগ হয় নিরাপত্তাহীনতা এমনকি প্রাণহানির ঝুঁকি। ক্ষমতা থেকে বিদায়ী দলের লোকজন সব সময় কারাবন্দী হওয়ার আতঙ্কের পাশাপাশি সহিংসতার শিকার হওয়া এমনকি মৃত্যুর আশঙ্কা করতে থাকেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেতাকে দলীয় নেতা-কর্মীসহ ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট এক জনসভায় হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল। এ ভয়াবহ অপরাধে পরোক্ষ সমর্থন না হলেও অন্তত ধামাচাপা দেওয়ার ব্যাপারে তৎকালীন সরকারের রহস্যজনক চেষ্টার স্মৃতি আওয়ামী লীগের প্রত্যেকের মনে এখনো সতেজ, বিশেষ করে যাঁরা শরীরে গ্রেনেডের ভগ্নাংশ বয়ে বেড়াচ্ছেন। সাবেক অর্থমন্ত্রী এস এ এম এস কিবরিয়া ও একজন শ্রদ্ধাভাজন সাংসদ আহসান উল্লাহ মাস্টারের হত্যাকাণ্ড মনে করিয়ে দেয় ক্ষমতা ছেড়ে গেলে কতটা চড়া মূল্য দিতে হয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে এটা মোটেও বিস্ময়কর নয় যে ক্ষমতাসীন দলগুলো অনির্দিষ্টকাল ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে চাইবে এবং সব ধরনের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে (বিশেষ করে জাতীয় নির্বাচন) দেখা হবে জীবন-মরণ লড়াই হিসেবে। গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক লেনদেন হিসেবে নয়, যাতে কেউ বিজয়ী আর কেউ পরাজিত হয়।
গোষ্ঠীতান্ত্রিক এই রাজনীতি একপর্যায়ে শাসনব্যবস্থাকেও গোষ্ঠীতান্ত্রিক করেছে। তার ফলে পেশাগত অগ্রগতি—সেটা প্রশাসন বা সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেখানেই হোক কিংবা সরকারি টেন্ডারের প্রতিযোগিতা অথবা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা সংশ্লিষ্ট রয়েছে এমন অন্য কোনো ক্ষেত্রে উন্নতি—এসবই নির্ভর করছে গোষ্ঠীতান্ত্রিক আনুগত্যের ওপর। পরিণামে সুশাসন, সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান, ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা ও আইনের চোখে সাম্যের নীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দুর্নীতির বিস্তার ঘটেছে।
আমাদের একসময়কার অন্যতম রাজনৈতিক সম্পদ হিসেবে বিবেচিত নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার অবমূল্যায়নকেও অবশ্যই এই গোষ্ঠীতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিণাম হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। প্রতিষ্ঠার সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার মূল ধারণাটির পেছনেই কিন্তু সক্রিয় ছিল আমাদের রাজনীতির ক্রমবর্ধমান গোষ্ঠীতান্ত্রিকতা। ১৯৯১ সালের শুরুর দিকে সূচিত হওয়া এ ধারণাটিকে পরে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়। তখন কোনো দলই জাতীয় নির্বাচন পরিচালনার ব্যাপারে প্রতিপক্ষের ওপর বিশ্বাস করতে পারছিল না। বিশেষ করে এ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার আলোকে যে, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে কোনো ক্ষমতাসীন দল নিজেদের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠান করে ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি। স্থানীয় নির্বাচনগুলো যতই অবাধ ও সুষ্ঠু হোক, সেগুলো কখনোই জাতীয় নির্বাচনের জন্য নজির হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না, যার ফল পরাজিত দলের জন্য জীবন-মরণ সমস্যা তৈরি করতে পারে। যে বিভক্তি ও অবিশ্বাসের পরিণামে ত্রয়োদশ সংশোধনী হয় তা গত ১৫ বছরে আরও ঘনীভূত হয়েছে এবং এ রকম একটি নির্বাচনে জয়-পরাজয়ের মূল্য অনেক গুণ বেড়েছে। বর্তমান বিভেদমূলক রাজনৈতিক পরিবেশে ক্ষমতাসীন দল যতই সদিচ্ছা পোষণ করুক এবং তাদের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে যত জোরালো সাংবিধানিক যুক্তিই তুলে ধরা হোক না কেন, যে বিশ্বাসের ঘাটতির কারণে বিরোধী দল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে মাঠে নেমেছে, সেই অবিশ্বাসের বাধা অতিক্রম করার আশা তারা করতে পারে না।
এই পরিস্থিতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের পক্ষে ও বিপক্ষের রাজনৈতিক বিতর্ক বধিরদের সংলাপে পরিণত হয়েছে। যদি ক্ষমতাসীন জোট বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন আয়োজনের ব্যাপারে আন্তরিকই হয় তাহলে তাদের উচিত হবে বাগাড়ম্বরপূর্ণ বিবৃতি এবং পঞ্চদশ সংশোধনীর পক্ষে যুক্তি তুলে ধরার পেছনে এত সময় ব্যয় না করা। বিরোধী দলের কাছে এসব যুক্তির কোনো গুরুত্ব নেই। ভোটারদের কাছেও এর আবেদন সামান্যই। কারণ, সমসাময়িক যুক্তির চেয়ে অতীত অভিজ্ঞতা তাঁদের বেশি টানে। ক্ষমতাসীন জোটের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত তাদের সদুদ্দেশ্যের ব্যাপারে বিরোধীদের আস্থা অর্জন করা। আর এটা করার জন্য উভয় পক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের দলের মধ্যে অব্যাহত আলোচনা প্রয়োজন। তা একান্ত বা প্রকাশ্য যেকোনো ফোরামে হতে পারে। অর্থপূর্ণ সংলাপের পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে দুই পক্ষের মধ্যে যোগাযোগ পুনঃস্থাপন করতে এ ধরনের আলোচনা খুবই প্রয়োজন। এটি সংসদ ও সংসদের বাইরে উভয় স্থানেই হতে হবে। এর মধ্যে যেকোনো একটি বা নির্দিষ্ট কোনো স্থানের ব্যাপারে জোরাজুরি করা আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের ব্যাপারে কম আগ্রহেরই লক্ষণ।
একবার উভয় পক্ষের মধ্যে এ ধরনের যোগাযোগ স্থাপিত হয়ে গেলে এমনকি সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যেও সমাধান খুঁজে পাওয়া কোনো জটিল ব্যাপার হবে না। এটি সব রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণে একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ প্রক্রিয়ায় আগামী নির্বাচনের অনুষ্ঠান নিশ্চিত করবে। এ ক্ষেত্রে মূল বিষয়টি হবে যে উভয় পক্ষকেই ক্ষমতায় যাওয়া বা ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য রাজপথে সংঘর্ষের চেয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের জন্য আগ্রহী হতে হবে।
কিন্তু আমরা দেখছি, সমাধানের সীমিত সুযোগের বাতায়নটি ক্রমেই রুদ্ধ হয়ে আসছে। একটি পরিপূর্ণ অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য পরস্পরের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি ব্যবস্থা নিয়ে মতৈক্যে পৌঁছাতে অর্থপূর্ণ আলোচনার জন্য ন্যূনতম বিশ্বাস স্থাপনের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বিরোধী দল বিএনপির কাছে ‘সাজানো’ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার রাজনীতি করা নতুন কিছু নয়। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ধাতই হলো এ রকম যে দলটিকে অবশ্যই নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসতে বা ক্ষমতা ধরে রাখতে হবে, যে নির্বাচনে দলটি তার প্রধান প্রতিপক্ষকে স্পষ্টভাবে হারাতে পারে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীও বারবার এ প্রস্তাবটিই তুলে ধরেছেন। কিন্তু তাঁর সরকারকে এর অন্তর্নিহিত অর্থটি বাস্তব কাজের মাধ্যমে তুলে ধরতে হবে। সরকারকে এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে সব দলের জন্য সমান সুযোগের ব্যবস্থা করে আগামী নির্বাচনে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
সরকারি দল যদি আত্মবিশ্বাসী হয় যে বিদায়ী মেয়াদের সাফল্য আগামী নির্বাচনেও তাদের বিজয় নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট, তাহলে তাদের উচিত প্রধান বিরোধী দল বিএনপিকে নির্বাচনে আনার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করা। সেখানে আওয়ামী লীগ তাদের অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পরাজিত করার চেষ্টা করতে পারবে।
ক্ষমতাসীন দলের একতরফা নির্বাচনের মাধ্যমে বিজয় বাংলাদেশের জনগণের কাছে এমনকি খোদ আওয়ামী লীগের কাছেও গ্রহণযোগ্য হবে না। এতে দলটির রাজনৈতিক আত্মমর্যাদাবোধ আহত হবে। ফলে একটি ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচনের প্রতিক্রিয়ায় যে গণপ্রতিরোধের সৃষ্টি হবে তা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের সামর্থ্যকে দুর্বল করবে। বাংলাদেশের সব রাজনৈতিক সংগ্রামে ভ্যানগার্ড (অগ্রবর্তী বাহিনী) হিসেবে কাজ করা ৬০ বছরের ইতিহাসসমৃদ্ধ দল হিসেবে আওয়ামী লীগ এমন কিছু করতে পারে না, যা আগামী পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকার জন্য প্রয়োজনীয়তার রাজনৈতিক বৈধতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।
বাংলাদেশের জন্য দুর্ভাগ্যজনক যে আগামী নির্বাচনের ফলাফল যা-ই হোক না কেন, এমন কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে না যে প্রধান দুটি দলের কোনোটিই তাদের দু-দুবারের মেয়াদ থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণ করেছে। গত কয়েক বছরে আমরা কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ইস্যু (কয়েকটি যৌক্তিক, যেমন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার আর কিছু সম্পূর্ণ এড়ানোর মতো বিষয় যেমন: ড. মুহাম্মদ ইউনূস, পদ্মা সেতু ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা) নিয়ে এতই ব্যস্ত থেকেছি যে আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সংক্রমিত করে এমন আরও বড় সমস্যাগুলোর প্রতি কোনো নজরই দেওয়া হয়নি। এই উপেক্ষার পরিণতি হবে অপরিমেয়।
বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সামাজিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা দেখিয়েছে। এর পেছনে কাজ করেছে এ দেশের কৃষক সমাজের সামলে নেওয়ার ক্ষমতা, প্রবাসী শ্রমিক ও কর্মজীবী নারীদের কঠোর পরিশ্রম, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন অংশের উদ্যোগ, বেসরকারি সংস্থাগুলোর সামাজিক কর্মসূচি, সুশীল সমাজের বিভিন্ন তৎপরতা এবং নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সরকারের ইতিবাচক ভূমিকা। ক্ষমতার লড়াইয়ের চেয়ে নীতিগত ইস্যুকে অগ্রাধিকার দেয় এমন একটি সমঝোতামূলক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এসব ইতিবাচক শক্তিকে কাজে লাগাতে পারলে আমরা একটি সুশাসিত সমাজের অবকাঠামো গড়ে তুলতে পারতাম। আর তখনই কেবল এ দেশের বঞ্চিত গণমানুষ প্রকৃত ‘দিনবদলের’ স্বাদ পেত।
আজ নির্বাচন নিয়ে অচলাবস্থা নিরসনে ব্যর্থতা সমাজের সব স্তরে উদ্বেগ ছড়িয়ে দিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে তুলনা করা যেতে পারে একটি জ্বলন্ত ট্রেনের সঙ্গে, যা কি না নিশ্চিত এক গভীর খাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরোধিতা থেকে উৎসারিত ক্রমবর্ধমান সহিংসতা ট্রেনের আগুনকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। এখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যুতে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে, তার শান্তিপূর্ণ সমাধান না হলে এই অগ্নিকুণ্ড আমাদের গ্রাস করবে। বিষয়টি নিয়ে শুধু দেশে নয়, আমাদের বিদেশি বন্ধুদের মধ্যেও উদ্বেগ বাড়ছে।
জাতীয় বিপদের এই ক্ষণে যাঁরা স্বাধীনতাসংগ্রামের চেতনার সঙ্গে একাত্মতা বোধ করেন এবং যাঁরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সক্ষমতার প্রতি এখনো প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তাঁদের উচিত ঐক্যবদ্ধ হয়ে এ সংকটের মোকাবিলা ও সমাধানে উদ্যোগী হওয়া। শত্রুকে বন্ধু থেকে পৃথক করতে না পারার ব্যর্থতা এবং সমঝোতার বদলে বিভেদ সৃষ্টি করা আমাদের নেতাদেরও ক্ষতি করেছে। তবে নৈরাশ্যের অতলে আমাদের অবনমন রোধের জন্য সম্মিলিত উদ্যোগ না নিলে শেষ পর্যন্ত চরম মূল্যটি দিতে হবে দেশকেই।
এহেন পরিস্থিতিতে এ বিপর্যয় এড়ানোর প্রধান দায়িত্ব আমাদের দুই প্রধান দলের প্রধান ও জ্যেষ্ঠ নেতাদের ওপর। আমাদের দুই প্রধান দল সাম্প্রতিক কয়েক বছরে পরস্পরের সঙ্গে রুয়ান্ডার হুতু ও তুতসিদের মতো আচরণ করলেও আমাদের এ কথা স্বীকার করতে হবে যে বাংলাদেশিরা গোত্রভিত্তিক সমাজে বাস করে না। বরং তাদের রয়েছে এক অভিন্ন সংস্কৃতি ও ইতিহাস। দলীয় রাজনীতির বাধ্যবাধকতা তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করত...
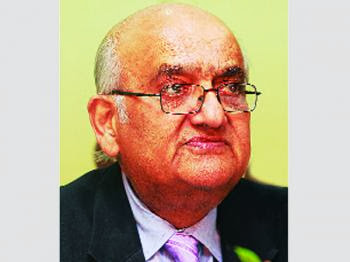
মনে করা হয়েছিল, একটি নতুন গণতান্ত্রিক পুনর্জাগরণের সুযোগ সৃষ্টি হলো। ধারণা করা হয়েছিল, স্বৈরতন্ত্রের তিক্ত অভিজ্ঞতার বদৌলতে এবার আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অধিকতর টেকসই রূপ নেবে। আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)—এ প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলকে নিয়ে একটি প্রকৃত দ্বিদলীয় ব্যবস্থার আবির্ভাব আমাদের আশা বাড়িয়ে দিয়েছিল। এই দল দুুটি স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে পরিপক্বতা অর্জন করেছে। উভয়ের ছিল শক্তিশালী রাজনৈতিক গণভিত্তি। সম্প্রদায় ও জাতিগত বৈচিত্র্যপূর্ণ ও আঞ্চলিকভাবে বিভক্ত দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় আমরা একটি মূলত সমজাতীয় সমাজব্যবস্থা পেয়েছি। এ বিষয়টি গণতন্ত্রের ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বাড়তি আশাবাদের সঞ্চার করেছিল। শেষত, ১৯৯৬ সালে অস্থায়ীভাবে নির্বাচন পরিচালনার জন্য সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে যে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়, তা বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামরত দেশগুলোর জন্য বাংলাদেশের বড় উপহার হিসেবে বিবেচনা করা হতে থাকে।
বাংলাদেশের আদলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা চালু হয়েছে নেপাল ও পাকিস্তানে। আর শ্রীলঙ্কাসহ অন্যান্য অঞ্চলের কয়েকটি দেশ এ ধরনের সরকার চালু করা যায় কি না, তা খতিয়ে দেখছে। পাকিস্তানে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পার্লামেন্ট নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে বেলুচিস্তানের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে। এতে ক্ষমতাসীন দল পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) পরাজিত ও নওয়াজ শরিফের নেতৃত্বাধীন প্রধান বিরোধী দল মুসলিম লিগ (পিএমএল-এন) বিজয়ী হয়। নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন নওয়াজ শরিফ। সব বিচারেই ওই নির্বাচন আপাতদৃষ্টিতে কোনো ধরনের দৃশ্যমান সামরিক প্রভাব ছাড়াই অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে।
গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের পর দুই দশকে পথভ্রষ্ট পরিস্থিতির ধারাবাহিকতায় আমরা আমাদের রাজনৈতিক সম্পদগুলোকে বড় দায়ে রূপান্তরিত করেছি, যা আমাদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে টেকসই রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করছে। আজ আমাদের একসময়ের ঈর্ষণীয় দ্বিদলীয় ব্যবস্থা একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠীতন্ত্রে পরিণত হয়েছে, যার অনমনীয়তা রুয়ান্ডার হুতু ও তুতসিদের মধ্যকার বিভেদের তুলনায় কোনো অংশে কম নয়। ওই দুটি পক্ষের তিক্ত বিরোধের চূড়ান্ত পরিণতি ছিল ভয়াবহ জাতিগত রক্তপাত। আমরা, বাংলাদেশিরা, যারা আত্মপরিচয়ের বিভেদ একেবারেই কম বলে নিজেদের নিয়ে গর্ব করতাম, তারাই বছর বছর প্রধান দুই দলের মধ্যে রাজনৈতিক বিভক্তিকে তীব্রতর করেছি। এই রাজনৈতিক গোষ্ঠীতন্ত্র আমাদের সামাজিক জীবনেও ঢুকে পড়েছে, যেখানে দুই দলের সদস্যরা (যাঁদের সামাজিক ও শিক্ষাগত প্রেক্ষাপট মূলত অভিন্ন) পরস্পরের বিয়েশাদি এমনকি শেষকৃত্যেও কমই যোগ দিয়ে থাকেন।
নিজ নিজ দলকে তিন দশকের বেশি সময় ধরে নেতৃত্ব দিচ্ছেন আওয়ামী লীগ ও বিএনপির শীর্ষ দুই নেতা। তাঁরা দুই দশকের বেশি সময় ধরে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সংলাপ দূরে থাক, কোনো রাজনৈতিক আলাপচারিতায়ও অংশগ্রহণ না করার মাধ্যমে সব রাজনৈতিক ইতিহাসের বই ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাঠ্যবইয়ে নিজেদের নাম অন্তর্ভুক্ত করেছেন। দুই গোষ্ঠীপ্রধানের মধ্যে বিভেদের এই সুকঠিন লৌহ যবনিকার কারণে সংশ্লিষ্ট দুটি দলের মধ্যে স্বাভাবিক রাজনৈতিক যোগাযোগেরও সব চেষ্টা ব্যাহত হয়েছে। দল দুটি এখন নিজ নিজ শীর্ষ নেতার অনুমতি ছাড়া পরস্পরের সঙ্গে সাধারণ রাজনৈতিক কথাবার্তা বলতেও শঙ্কিত বোধ করে, আনুষ্ঠানিক আলোচনার তো প্রশ্নই ওঠে না।
এই বিভক্তির গভীরতা এত বেশি যে রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর মানে বিদায়ী দলটির জন্য কেবল ক্ষমতা হারানোই নয়, বরং ‘বিজয়ীরই সব পাওয়ার’ প্রচলিত রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে অর্থনৈতিক সুযোগ হারানোও বটে। তবে অর্থনৈতিক জীবিকা হারানোই একমাত্র বিপদ নয়, বরং এর সঙ্গে যোগ হয় নিরাপত্তাহীনতা এমনকি প্রাণহানির ঝুঁকি। ক্ষমতা থেকে বিদায়ী দলের লোকজন সব সময় কারাবন্দী হওয়ার আতঙ্কের পাশাপাশি সহিংসতার শিকার হওয়া এমনকি মৃত্যুর আশঙ্কা করতে থাকেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেতাকে দলীয় নেতা-কর্মীসহ ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট এক জনসভায় হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল। এ ভয়াবহ অপরাধে পরোক্ষ সমর্থন না হলেও অন্তত ধামাচাপা দেওয়ার ব্যাপারে তৎকালীন সরকারের রহস্যজনক চেষ্টার স্মৃতি আওয়ামী লীগের প্রত্যেকের মনে এখনো সতেজ, বিশেষ করে যাঁরা শরীরে গ্রেনেডের ভগ্নাংশ বয়ে বেড়াচ্ছেন। সাবেক অর্থমন্ত্রী এস এ এম এস কিবরিয়া ও একজন শ্রদ্ধাভাজন সাংসদ আহসান উল্লাহ মাস্টারের হত্যাকাণ্ড মনে করিয়ে দেয় ক্ষমতা ছেড়ে গেলে কতটা চড়া মূল্য দিতে হয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে এটা মোটেও বিস্ময়কর নয় যে ক্ষমতাসীন দলগুলো অনির্দিষ্টকাল ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে চাইবে এবং সব ধরনের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে (বিশেষ করে জাতীয় নির্বাচন) দেখা হবে জীবন-মরণ লড়াই হিসেবে। গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক লেনদেন হিসেবে নয়, যাতে কেউ বিজয়ী আর কেউ পরাজিত হয়।
গোষ্ঠীতান্ত্রিক এই রাজনীতি একপর্যায়ে শাসনব্যবস্থাকেও গোষ্ঠীতান্ত্রিক করেছে। তার ফলে পেশাগত অগ্রগতি—সেটা প্রশাসন বা সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেখানেই হোক কিংবা সরকারি টেন্ডারের প্রতিযোগিতা অথবা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা সংশ্লিষ্ট রয়েছে এমন অন্য কোনো ক্ষেত্রে উন্নতি—এসবই নির্ভর করছে গোষ্ঠীতান্ত্রিক আনুগত্যের ওপর। পরিণামে সুশাসন, সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান, ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা ও আইনের চোখে সাম্যের নীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দুর্নীতির বিস্তার ঘটেছে।
আমাদের একসময়কার অন্যতম রাজনৈতিক সম্পদ হিসেবে বিবেচিত নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার অবমূল্যায়নকেও অবশ্যই এই গোষ্ঠীতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিণাম হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। প্রতিষ্ঠার সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার মূল ধারণাটির পেছনেই কিন্তু সক্রিয় ছিল আমাদের রাজনীতির ক্রমবর্ধমান গোষ্ঠীতান্ত্রিকতা। ১৯৯১ সালের শুরুর দিকে সূচিত হওয়া এ ধারণাটিকে পরে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়। তখন কোনো দলই জাতীয় নির্বাচন পরিচালনার ব্যাপারে প্রতিপক্ষের ওপর বিশ্বাস করতে পারছিল না। বিশেষ করে এ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার আলোকে যে, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে কোনো ক্ষমতাসীন দল নিজেদের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠান করে ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি। স্থানীয় নির্বাচনগুলো যতই অবাধ ও সুষ্ঠু হোক, সেগুলো কখনোই জাতীয় নির্বাচনের জন্য নজির হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না, যার ফল পরাজিত দলের জন্য জীবন-মরণ সমস্যা তৈরি করতে পারে। যে বিভক্তি ও অবিশ্বাসের পরিণামে ত্রয়োদশ সংশোধনী হয় তা গত ১৫ বছরে আরও ঘনীভূত হয়েছে এবং এ রকম একটি নির্বাচনে জয়-পরাজয়ের মূল্য অনেক গুণ বেড়েছে। বর্তমান বিভেদমূলক রাজনৈতিক পরিবেশে ক্ষমতাসীন দল যতই সদিচ্ছা পোষণ করুক এবং তাদের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে যত জোরালো সাংবিধানিক যুক্তিই তুলে ধরা হোক না কেন, যে বিশ্বাসের ঘাটতির কারণে বিরোধী দল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে মাঠে নেমেছে, সেই অবিশ্বাসের বাধা অতিক্রম করার আশা তারা করতে পারে না।
এই পরিস্থিতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের পক্ষে ও বিপক্ষের রাজনৈতিক বিতর্ক বধিরদের সংলাপে পরিণত হয়েছে। যদি ক্ষমতাসীন জোট বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন আয়োজনের ব্যাপারে আন্তরিকই হয় তাহলে তাদের উচিত হবে বাগাড়ম্বরপূর্ণ বিবৃতি এবং পঞ্চদশ সংশোধনীর পক্ষে যুক্তি তুলে ধরার পেছনে এত সময় ব্যয় না করা। বিরোধী দলের কাছে এসব যুক্তির কোনো গুরুত্ব নেই। ভোটারদের কাছেও এর আবেদন সামান্যই। কারণ, সমসাময়িক যুক্তির চেয়ে অতীত অভিজ্ঞতা তাঁদের বেশি টানে। ক্ষমতাসীন জোটের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত তাদের সদুদ্দেশ্যের ব্যাপারে বিরোধীদের আস্থা অর্জন করা। আর এটা করার জন্য উভয় পক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের দলের মধ্যে অব্যাহত আলোচনা প্রয়োজন। তা একান্ত বা প্রকাশ্য যেকোনো ফোরামে হতে পারে। অর্থপূর্ণ সংলাপের পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে দুই পক্ষের মধ্যে যোগাযোগ পুনঃস্থাপন করতে এ ধরনের আলোচনা খুবই প্রয়োজন। এটি সংসদ ও সংসদের বাইরে উভয় স্থানেই হতে হবে। এর মধ্যে যেকোনো একটি বা নির্দিষ্ট কোনো স্থানের ব্যাপারে জোরাজুরি করা আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের ব্যাপারে কম আগ্রহেরই লক্ষণ।
একবার উভয় পক্ষের মধ্যে এ ধরনের যোগাযোগ স্থাপিত হয়ে গেলে এমনকি সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যেও সমাধান খুঁজে পাওয়া কোনো জটিল ব্যাপার হবে না। এটি সব রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণে একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ প্রক্রিয়ায় আগামী নির্বাচনের অনুষ্ঠান নিশ্চিত করবে। এ ক্ষেত্রে মূল বিষয়টি হবে যে উভয় পক্ষকেই ক্ষমতায় যাওয়া বা ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য রাজপথে সংঘর্ষের চেয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের জন্য আগ্রহী হতে হবে।
কিন্তু আমরা দেখছি, সমাধানের সীমিত সুযোগের বাতায়নটি ক্রমেই রুদ্ধ হয়ে আসছে। একটি পরিপূর্ণ অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য পরস্পরের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি ব্যবস্থা নিয়ে মতৈক্যে পৌঁছাতে অর্থপূর্ণ আলোচনার জন্য ন্যূনতম বিশ্বাস স্থাপনের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বিরোধী দল বিএনপির কাছে ‘সাজানো’ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার রাজনীতি করা নতুন কিছু নয়। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ধাতই হলো এ রকম যে দলটিকে অবশ্যই নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসতে বা ক্ষমতা ধরে রাখতে হবে, যে নির্বাচনে দলটি তার প্রধান প্রতিপক্ষকে স্পষ্টভাবে হারাতে পারে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীও বারবার এ প্রস্তাবটিই তুলে ধরেছেন। কিন্তু তাঁর সরকারকে এর অন্তর্নিহিত অর্থটি বাস্তব কাজের মাধ্যমে তুলে ধরতে হবে। সরকারকে এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে সব দলের জন্য সমান সুযোগের ব্যবস্থা করে আগামী নির্বাচনে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
সরকারি দল যদি আত্মবিশ্বাসী হয় যে বিদায়ী মেয়াদের সাফল্য আগামী নির্বাচনেও তাদের বিজয় নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট, তাহলে তাদের উচিত প্রধান বিরোধী দল বিএনপিকে নির্বাচনে আনার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করা। সেখানে আওয়ামী লীগ তাদের অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পরাজিত করার চেষ্টা করতে পারবে।
ক্ষমতাসীন দলের একতরফা নির্বাচনের মাধ্যমে বিজয় বাংলাদেশের জনগণের কাছে এমনকি খোদ আওয়ামী লীগের কাছেও গ্রহণযোগ্য হবে না। এতে দলটির রাজনৈতিক আত্মমর্যাদাবোধ আহত হবে। ফলে একটি ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচনের প্রতিক্রিয়ায় যে গণপ্রতিরোধের সৃষ্টি হবে তা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের সামর্থ্যকে দুর্বল করবে। বাংলাদেশের সব রাজনৈতিক সংগ্রামে ভ্যানগার্ড (অগ্রবর্তী বাহিনী) হিসেবে কাজ করা ৬০ বছরের ইতিহাসসমৃদ্ধ দল হিসেবে আওয়ামী লীগ এমন কিছু করতে পারে না, যা আগামী পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকার জন্য প্রয়োজনীয়তার রাজনৈতিক বৈধতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।
বাংলাদেশের জন্য দুর্ভাগ্যজনক যে আগামী নির্বাচনের ফলাফল যা-ই হোক না কেন, এমন কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে না যে প্রধান দুটি দলের কোনোটিই তাদের দু-দুবারের মেয়াদ থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণ করেছে। গত কয়েক বছরে আমরা কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ইস্যু (কয়েকটি যৌক্তিক, যেমন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার আর কিছু সম্পূর্ণ এড়ানোর মতো বিষয় যেমন: ড. মুহাম্মদ ইউনূস, পদ্মা সেতু ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা) নিয়ে এতই ব্যস্ত থেকেছি যে আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সংক্রমিত করে এমন আরও বড় সমস্যাগুলোর প্রতি কোনো নজরই দেওয়া হয়নি। এই উপেক্ষার পরিণতি হবে অপরিমেয়।
বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সামাজিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা দেখিয়েছে। এর পেছনে কাজ করেছে এ দেশের কৃষক সমাজের সামলে নেওয়ার ক্ষমতা, প্রবাসী শ্রমিক ও কর্মজীবী নারীদের কঠোর পরিশ্রম, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন অংশের উদ্যোগ, বেসরকারি সংস্থাগুলোর সামাজিক কর্মসূচি, সুশীল সমাজের বিভিন্ন তৎপরতা এবং নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সরকারের ইতিবাচক ভূমিকা। ক্ষমতার লড়াইয়ের চেয়ে নীতিগত ইস্যুকে অগ্রাধিকার দেয় এমন একটি সমঝোতামূলক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এসব ইতিবাচক শক্তিকে কাজে লাগাতে পারলে আমরা একটি সুশাসিত সমাজের অবকাঠামো গড়ে তুলতে পারতাম। আর তখনই কেবল এ দেশের বঞ্চিত গণমানুষ প্রকৃত ‘দিনবদলের’ স্বাদ পেত।
আজ নির্বাচন নিয়ে অচলাবস্থা নিরসনে ব্যর্থতা সমাজের সব স্তরে উদ্বেগ ছড়িয়ে দিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে তুলনা করা যেতে পারে একটি জ্বলন্ত ট্রেনের সঙ্গে, যা কি না নিশ্চিত এক গভীর খাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরোধিতা থেকে উৎসারিত ক্রমবর্ধমান সহিংসতা ট্রেনের আগুনকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। এখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যুতে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে, তার শান্তিপূর্ণ সমাধান না হলে এই অগ্নিকুণ্ড আমাদের গ্রাস করবে। বিষয়টি নিয়ে শুধু দেশে নয়, আমাদের বিদেশি বন্ধুদের মধ্যেও উদ্বেগ বাড়ছে।
জাতীয় বিপদের এই ক্ষণে যাঁরা স্বাধীনতাসংগ্রামের চেতনার সঙ্গে একাত্মতা বোধ করেন এবং যাঁরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সক্ষমতার প্রতি এখনো প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তাঁদের উচিত ঐক্যবদ্ধ হয়ে এ সংকটের মোকাবিলা ও সমাধানে উদ্যোগী হওয়া। শত্রুকে বন্ধু থেকে পৃথক করতে না পারার ব্যর্থতা এবং সমঝোতার বদলে বিভেদ সৃষ্টি করা আমাদের নেতাদেরও ক্ষতি করেছে। তবে নৈরাশ্যের অতলে আমাদের অবনমন রোধের জন্য সম্মিলিত উদ্যোগ না নিলে শেষ পর্যন্ত চরম মূল্যটি দিতে হবে দেশকেই।
এহেন পরিস্থিতিতে এ বিপর্যয় এড়ানোর প্রধান দায়িত্ব আমাদের দুই প্রধান দলের প্রধান ও জ্যেষ্ঠ নেতাদের ওপর। আমাদের দুই প্রধান দল সাম্প্রতিক কয়েক বছরে পরস্পরের সঙ্গে রুয়ান্ডার হুতু ও তুতসিদের মতো আচরণ করলেও আমাদের এ কথা স্বীকার করতে হবে যে বাংলাদেশিরা গোত্রভিত্তিক সমাজে বাস করে না। বরং তাদের রয়েছে এক অভিন্ন সংস্কৃতি ও ইতিহাস। দলীয় রাজনীতির বাধ্যবাধকতা তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করত...






















No comments