বৌদ্ধদের ধর্মীয়, সামাজিক কুসংস্কার ও লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান by ড. জগন্নাথ বড়ুয়া
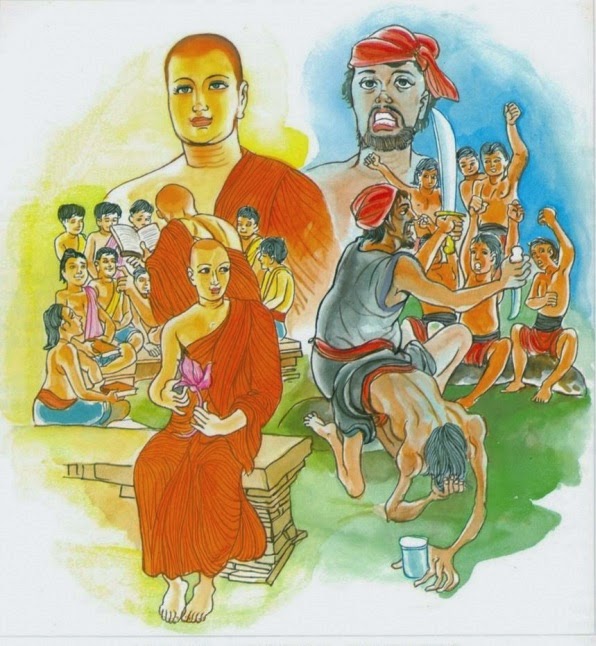
সারসংক্ষেপ: প্রাচীন কাল থেকে বাংলাদেশে বাঙালি বড়ুয়া বৌদ্ধ ও বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক বৌদ্ধ সম্প্রদায় চাকমা, মারমা, রাখাইন, চাক, ম্রো, খুমি, খিয়াং প্রমুখ বৌদ্ধ জনগোষ্ঠি বসবাস করে আসছে। বৌদ্ধরা এদেশের সচেতন ও শান্তিপ্রিয় নাগরিক। চিরাচরিত নিয়ম নীতি ও ধর্মীয় বিধি বিধানে বৌদ্ধরা সকল কাজকর্ম ও নিত্য নৈমিত্তিক জীবনযাত্রা অতিবাহিত করে থাকে। বলতে গেলে বৌদ্ধরা আদর্শিক জীবন গঠনে দৃঢ় প্রত্যয়ী। কোন রকম ধর্মীয়, সামাজিক কুসংস্কার ও লৌকিক আচার অনুষ্ঠানে বিশ্বাসী নয়। তবুও দেখা যায় ধর্মীয় ও সামাজিক ক্রিয়াকর্মে বিভিন্ন কুসংস্কার ও লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান প্রচলিত। এগুলো নানাভাবে ধর্মীয় পূজা-অর্চনা এবং সামাজিক লোকাচার ও সংস্কৃতির সাথে আবিষ্ট হয়ে আছে। ইতিহাস মতে, প্রাচীন কাল থেকে বৌদ্ধদের মধ্যে নানা কুসংস্কার, লোকবিশ্বাস, লৌকিক সংস্কৃতি ও আচার-অনুষ্ঠানসমূহের গোড়াপত্তন হয়েছিল। এদেশের বৌদ্ধদের জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ ইত্যাদিতে বিভিন্ন ধর্মীয় নিয়ম-নীতি ও লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান করার প্রথা প্রচলিত আছে। যেমন – সাধভণ, সন্তানের জন্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাসন, বিদ্যারম্ভ, দীক্ষাগ্রহণ, কর্ণ ও নাসিকাছেদন, আবাহ-বিবাহ, শবসৎকার, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, পরিত্রাণ দেশনা প্রভৃতি। প্রান্তিক বৌদ্ধ জনজাতিসত্তার মধ্যে মূর্তিপূজা, বুদ্ধপূজা, সিবলী পূজা, মাজার পূজা, বৃপূজা, মানত করা, সত্যপীরের সিন্নি, আল্পলানী, নদীতে স্নান, জীন ভূত পরীতে পাওয়া, বাণটোনা বৈদ্য, মনসা পূজা, দেবদেবী প্রভৃতি কুসংস্কার, রীতি-নীতি ও লৌকিক সংস্কারও বিদ্যমান রয়েছে। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক বৌদ্ধ জনগোষ্ঠির মধ্যে প্রচলিত রয়েছে আরো অনেক স্বজাত লোকাচার, লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কৃতি। আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলাদেশের বৌদ্ধ জনগোষ্ঠির মধ্যে প্রচলিত ধর্মীয় ও সামাজিক লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান এবং নানাবিধ কুসংস্কার বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে।
ভূমিকা:
বাংলাদেশ তথা বৃহত্তর চট্টগ্রামের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন পূজা অর্চনা, লোক সংস্কৃতি ও আচার অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। এ সকল ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার, পূজা-পার্বণ ও লোকাচারসমূহ সাধারণত পুরনো আস্তর নামে খ্যাত হয়ে থাকে। এটি শাস্ত্র শব্দের বিকৃত রূপ (হাস্তর>শাস্তর>শাস্ত্র)। প্রাচীন কালে এখানকার বৌদ্ধ অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত লৌকিক সংস্কৃতির আচার অনুষ্ঠানসমূহ শাস্ত্র বাক্য জ্ঞানে একান্ত ভাবে বিশ্বাস ও আচরণ করা হত বলে শাস্ত্র শব্দটি আঞ্চলিক উচ্চারণে ‘হাস্তর’ রূপ প্রাপ্ত হয়েছিল এবং তা প্রাচীন কাল থেকে পুরানো শব্দটি যুক্ত হয়ে ‘পুরানো হাস্তর’ নামে খ্যাত হয়ে এসেছে। খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগ হতে বড়ুয়া বৌদ্ধদের আর্যধর্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতি, ভাষা ও লিপি প্রচারিত হয়। বাঙালি বড়ুয়া ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের মতে, প্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন কুসংস্কার, লোকবিশ্বাস, লোক সংস্কৃতি ও আচার অনুষ্ঠানসমূহের প্রথম গোড়াপত্তন হয়েছিল।১
সহজ সত্য চিরকালই এক, কিন্তু সেই সহজ সত্যই মানুষ বারংবার ভুলে যায়। তথাগত বুদ্ধ সেই বিস্মৃত সত্য সরল ও হৃদয়স্পর্শী কথায় বলেছেন, সুবিজ্ঞভুত ক্রিয়াকর্মের আবর্জনা উড়িয়ে দিয়ে মানুষকে সত্যের উজ্জ্বল মুক্তি দেখিয়েছিলেন।২ ধর্মের প্রাণ হচ্ছে ‘বিশুদ্ধ বিশ্বাস’ (belief) । এই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই আসে সামাজিক জীবনাচরণ ও সংঘবদ্ধতা। ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনকে ধর্মীয় দিক থেকে সংহিত করার জন্য প্রতিটি সমাজেই ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানের প্রয়োজন। প্রত্যেক ধর্মেরই ধর্মীয় গ্রন্থ আছে (কখনো মৌখিক), আছে তার পবিত্র ভাষা, আছে মন্ত্র স্তোত্র ইত্যাদি। বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি যেহেতু প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে তাই তখনকার যুগ আর এখনকার যুগ এবং জ্ঞান মেধা ও প্রজ্ঞায় পার্থক্য দেখা যায়। এ সময় মানুষ আদিম (Primitive) কুসংস্র (Superstition) ও লৌকিক (Earthly) সংস্কৃতির বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল কিন্তু সেই কুসংস্কার অনিয়ম অপসংস্কৃতিগুলো আজো ধর্ম ও সমাজে বিদ্যমান। এগুলো সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে। বৌদ্ধ সমাজে বিশেষত Religious Rituals and Falk Belief ব্যাপক ভাবে প্রচলিত রয়েছে।
একবিংশ শতাব্দীতে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার লাভ ও চর্চার ফলে তার আড়ষ্টতা কিছুটা শিথিল হলেও এখনকার লোকজীবন থেকে তা একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। তাই সমগ্র বৌদ্ধধর্মে তথা বাঙালি বড়ুয়া বৌদ্ধদের মধ্যে লোক সংস্কৃতি ও আচার অনুষ্ঠানের প্রভাব ল্য করা যায়। একটু সচেতন ভাবে দেখলে বুঝতে পারা যায় যে, বাঙালি বড়ুয়া ও পার্বত্য বৌদ্ধদের আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মীয় ও সামাজিক লোক সংস্কৃতির প্রতিটি বিষয়ে লৌকিকতা বিদ্যমান। বাংলাদেশের বৌদ্ধেরা সেকালের যুগে ধ্যান-জ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষা ও শিল্পকলায় অগ্রসর ছিল ঠিক কিন্তু তারা লৌকিকতা (Worldlienss) বর্জিত ছিলেন না। সেকালের প্রাপ্ত লোক সংস্কৃতি ও আচার অনুষ্ঠানগুলো থেকে আমরা মুক্ত হতে পারছি না, পারছি না ছাড়তে, পারছি না পরিহার করতে। খ্রিষ্ঠপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতের চিন্তারাজ্যে এক তুমুল বিপ্লব ঘটেছিল। বহু শতাব্দী ধরে এদেশের হিন্দু আর্যগণ যে ধর্মীয় প্রভাব গড়ে তুলে ছিল তার আমূল পরিবর্তন সাধন করেন গৌতম বুদ্ধ। মূলত আধুনিক কালে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের প্রভাব এবং সামাজিক লোকাচার ও সংস্কৃতির ধারা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান ও রীতি-নীতি সরব হয়ে উঠে।
বর্তমান বাঙালি হিন্দু সমাজের অধিকাংশ লৌকিক দেবদেবী ও আচার অনুষ্ঠান আজ বৌদ্ধদের ঘরোয়া আচারে ও প্রাচীন ধর্মীয় সংস্কারে রয়ে গেছে। প্রচলিত অনেকগুলি আবার হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি রেওয়াজ।৩ বর্তমান বিশ্বায়ন হল যুক্তি তত্ত্ব ও কম্পিউটার বিজ্ঞান প্রযুক্তির যুগ। এ যুগের মানুষ বস্তুবাদে বিশ্বাসী, বাস্তবতায় বিশ্বাসী। বৌদ্ধধর্ম শাস্ত্রে লৌকিকতা ও অলৌকিকত্বকে সহজে মেনে নিতে পারে না। বাংলাদেশের বৌদ্ধরা থেররাদ আদর্শের অনুসারী। থেরবাদে প্রতিষ্ঠিত হলেও বৌদ্ধদের প্রকৃত আচরণে, বিনয় বিধানের অন্তরালে থাকে বিভিন্ন কুসংস্কার, লোক বিশ্বাস, আচার-আচরণ, পূজা-পার্বণ ও লৌকিক সংস্কৃতি। এমন কি ধর্মের তত্ত্বাশ্রিত আবেদন লৌকিক ধারায় নেমে এসে ধর্মের অলৌকিকত্বের বেড়া ভেঙ্গে জীবনাশ্রিত সংস্কৃতি হিসেবে রূপ লাভ করেছে। এর অসংখ্য উদাহরণ সমতলি বাঙালি বড়–য়া ও পার্বত্য নৃতাত্ত্বিক ক্ষুদ্র আদিবাসী বৌদ্ধদের মধ্যে সচরাচর বিদ্যমান।৪
ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে বাংলাদেশের বৌদ্ধরা বুদ্ধের প্রকৃত ধর্মদর্শন ও বিনয়নীতি সম্বন্ধে মোটেই অবহিত ছিলেন না। পাল ও গুপ্ত যুগের পরে বৌদ্ধধর্ম ক্রমশ নিজ বৈশিষ্ট্য হারিয়ে নানা কুসংস্কার ও লৌকিকতায় বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিল – এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বৌদ্ধধর্মের তাদৃশ বিপর্যয় বৌদ্ধদের ধর্ম ও সমাজ জীবনে দারুণভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। উল্লেখ যে বেন্ডেল সাহেবের মতে, ১৪৪৬ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশে প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম পুঁথি লিখিত হয়েছিল।৫ বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রধান দুটি ধারা থেরবাদ ও মহাযান প্রভাবান্বিত ছিল। বিশেষত লৌকিকতা ও বিভিন্ন মতাদর্শের কারণে পাল ও চন্দ্র বংশের রাজাদের রাজত্ব কালে বাংলাদেশে মহাযান ধর্মের প্রসার ঘটে। এই সময় তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের চারটি বিশেষ শাখা – বজ্রযান, কালচক্রযান, মন্ত্রযান, তন্ত্রযান ও সহজযান বাংলাদেশে নিজ নিজ প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করে। বর্তমান বিশ্বে মূলত হীনযান ও মহাযান এ দুটি ধারা বিদ্যমান। বাংলাদেশে মূলত থেরবাদ আদর্শের সংঘরাজ নিকায় ও মহাস্থবির নিকায় এ দু’সংঘ ধারা প্রচলিত আছে। এ শুধু বৌদ্ধধর্মে নয় প্রত্যেক ধর্ম এ রকম শ্রেণিভেদ ল্য করা যায়। যেমন- হিন্দুধর্মে শাক্ত ও বৈষ্ণব, মুসলিম ধর্মের শিয়া ও সুন্নি এবং খ্রিষ্টান ধর্মে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্ট।৬ এ সমস্ত শাখা প্রশাখা ও মতভেদের জন্য এ সমস্ত লৌকিক ক্রিয়াকলাপ, আচার ও সংস্কৃতি সৃষ্টি হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।
এবার বুদ্ধপূজা, বুদ্ধমূর্তি পূজা সম্পর্কে আলোচনা করা যায়, খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের প্রথম দিকেই বুদ্ধের মূর্তি তৈরি প্রথা আরম্ভ হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে তাঁর পূজার প্রচলনও আরম্ভ হয়েছিলো। পার্শ্ববর্তী ব্রাহ্মণদের ধর্মায়তন প্রভাবের ফলেই অলে কখন ভক্তদের মধ্যে বুদ্ধ পূজার প্রচলন আরম্ভ হয়েছিল তা বলা অত্যন্ত শক্ত ব্যাপার।৭
বুদ্ধপূজা : ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, ব্যাপক ভাবে বুদ্ধপূজার প্রচলন হয় কুষাণ যুগে, প্রথম খ্রিষ্টীয় শতাব্দীতে মহারাজ কনিষ্কের রাজত্ব কালে। উপাসকগণের মধ্যে এক শ্রেণির লোক যখন বুদ্ধের মূর্তি তৈরি করে বুদ্ধের পূজা করতে আরম্ভ করেছিল তখনই তাকে স্বগোত্রে অপর শ্রেণীর উপাসকগণ বুদ্ধ নিদ্দিষ্ট পার্থক্যেই দৃঢ় ভাবে অবলম্বন করে থাকলেন। প্রাচীন বৌদ্ধধর্মে বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ ত্রিশরণ মন্ত্র রূপে গৃহীত হয়েছিল। পরবর্তী যুগে বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ জ্ঞান-কল্যাণ-শক্তির প্রতীক রূপে ত্রিমূর্তি ধারণা করে বুদ্ধ বৌদ্ধদের পূজার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। কালক্রমে বৌদ্ধগণ কেবল বুদ্ধ ধর্ম সংঘের প্রতীক পূর্ণ করে সন্তুষ্ট হলেন না। ত্রিরতœ কে মানবীর মূর্তিতে রূপায়িত করে দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত করে নিলেন। পণ্ডিত সিদ্ধ হর্ষের সংগৃহিত ধাতব মূর্তি ক্রয়ের একটি ধর্মদেবতার প্রতিমা। এখানে ধর্ম বুদ্ধ দেবতার দেিণ পদ্মাসনে চতুর্ভূজা নারী মূর্তি উপবিষ্টা।৮
পুরাতত্ত্ববিদ Sir Cunningham এর মহাবোধি চিত্রে দেখা যায়- বুদ্ধদেবের বামে সংঘ ত্রিভূজা নারী মূর্তিতে এবং ধর্ম পুরুষ রূপে বুদ্ধের দক্ষিণ পার্শ্বে আসন গ্রহণ করেছে।৯ তার ধর্ম মতে যাগ, যজ্ঞ, ফেস প্রভৃতি পূজার কোন নির্দ্দেশ নেই। তাকে দেবতার আসনে বসিয়ে পূজার ব্যবস্থাও তিনি নিষেধ করে দিয়েছিলেন। বুদ্ধ নিজে কখনো তান্ত্রিক ভাবধারাকে স্বীকার করেননি। এ মতের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন বিখ্যাত বৌদ্ধ যোগচারী সন্ন্যাসী অসঙ্গ। প্রকৃত পে বৌদ্ধ অর্চনা হীনযানে ছিলই না। বুদ্ধের পরিনির্বাণের ৪/৫ শত বৎসর পরে বুদ্ধমূর্তি বিহারে প্রতিষ্ঠিত হয়। কারো কারো মতে, খ্রিষ্টীয় শতাব্দীর প্রথম শতকে মূর্তি নির্মিত হয়। ক্রমে আসতে লাগলো এক একটি ধ্যানী বুদ্ধ। প্রথম অভিতাভ, তার পর আেভ্য, বৈরোচন, রতœসম্ভব, তার পর অমো সিদ্ধি। বৌদ্ধধর্মে তখন ব্রাহ্মণ্য মতের তান্ত্রিক ভাবধারা প্রবল ভাবে প্রবেশ করেছিল। কারণ শেষে তারাদেবী, ডাক, ডাকিনী, পেত, যোগধ্যানী, হারতি, বৌদ্ধ শ্যামা দেবী প্রভৃতির উপাসনা করা হতো। ইহা নিঃসন্দেহে এই সকল পাপাচার চরিত্রহীন দেবদেবী। বৌদ্ধগণের ক্রিয়াকাণ্ডে লোক সাধারণের মনে বৌদ্ধ সমাজের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে ছিল এবং বৌদ্ধ সমাজ ধর্মহীন ভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এই প্রসঙ্গে ঝরৎ ঈযধৎষবং ঊষরড়ঃ তাঁর প্রণীত ঐরহফঁরংস ধহফ ইঁফফযরংস গ্রন্থে বলেছেন,Sir Charles Eliot Zuvi cÖYxZ Hinduism and Buddhism MÖ‡š’ e‡j‡Qb, The aberration of Indian religion is not due to its inherent depravity but to its Universality. In Europe those who follow dis-reputable occupation rarely suppose that they have anything to do with church. In India robbers murderer’s gamblers, prostitutes and maniwes all have their appropriate gods.10
বৌদ্ধরা ধর্ম বিশ্বাসে বৌদ্ধ ছিল কিন্তু ধর্মীয়, সামাজিক ও বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠনে তাদের বৌদ্ধ বলা অযৌক্তিক হবে। কারণ তারা বৌদ্ধধর্মের, বৌদ্ধ সংঘের বাহিরে তাদের সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য রার বিরোধী হয়। স্যার চার্লস ইলিয়াড লিখেছেন, It aimed not at founding a seat but at including all the world as lay believers of easy farms. This ascendant but its effect was disastrous when decline began. The line dividing Buddhist lay man from ordinary thirds became less and less marked.
ত্রিপিটকের সুত্ত নিপাত গ্রন্থে বুদ্ধ একস্থানে উপ শিব-এর প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, যিনি নির্বাণ প্রাপ্ত হন কোন ভাবেই তাকে পরিমাপ করা যায় না। তার আকৃতি নির্দেশ করা যায় না। যখন সমস্ত উপকরণ সরে যায় তখন তিনি অস্তিত্বে লীন হন। অস্তিত্বের এই উপকরণ হচ্ছে ধর্ম। চূড়ান্ত নির্বাণের পর এগুলো থাকে না। তখন নির্বাণ প্রাপ্ত ব্যক্তি আকিঞ্জন হয়ে যান। বুদ্ধ আরো বলেছেন যে, নির্বাণ প্রাপ্তকে পূজা দিতে হয় না। কারণ নির্বাণ প্রাপ্তগণ পূজা পান না। সুতরাং বুদ্ধের কোন ছবি বা মূর্তি তৈরি করে খাদ্য ভোজ্য আহার, বাতি, ধূপ, ফুল ও সুগন্ধী দ্রব্যাদি দ্বারা পূজা করা প্রকৃত অর্থে লোকাচার। উল্লেখ্য যে সাঁচীর বৌদ্ধ স্তূপ পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপো পরিচিত। সাঁচী ভারতবর্ষের মধ্য প্রদেশে অবস্থিত। বুদ্ধমূর্তি নির্মাণের উপকরণ হিসেবে কখনও কাঠ ব্যবহার হয়েছে, কখনও পাথর, কখনও ব্রোঞ্জ, কখনও স্বর্ণ বা অন্য কোন ধাতু। আবার দেয়াল গাত্রের ফ্রেসকো হিসেবে বুদ্ধমূর্তি তৈরি হয়েছে।
মহাপরিনির্বাণ সূত্রে বুদ্ধ এসব কিছুর পূজা করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেও বৌদ্ধদের অনাড়ম্ভরপূর্ণ উৎসব ও পূজা পার্বণ। যেমন বুদ্ধমূর্তি, স্তূপ, বোধিবৃ, বুদ্ধাস্থি, কৃত্রিম বুদ্ধ পদচিহ্ন ইত্যাদি প্রচলিত আছে। আর এ সব বুদ্ধ জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন পবিত্র বিষয় বলে বিহারে থাকে। বৌদ্ধরা এগুলোর পূজা করে থাকে।১১ এসব প্রচার অনুষ্ঠান নির্বাণকামী ব্যক্তিদের অপ্রয়োজনীয় হলেও ধর্মীয় আবেগ পূর্ণ করার ল্েয এগুলোর গুরুত্ব ও মূল্য অপরিসীম।
পদ্মসূত্রের কথা : বুদ্ধ নিজেকে সর্বদাই মানুষ হিসেবে ঘোষণা করেছেন এবং কখনও ঈশ্বর বা দিব্য পুরুষ বলে ঘোষণা করেননি। তিনি (বুদ্ধ) শিষ্যদের সম্যক উপদেশ প্রদান করেছেন। কিন্তু কালজয়ী মহাযানী পদ্মসূত্রে বুদ্ধের মতের বিরোধী বক্তব্য রয়েছে। এতে বলা হয়েছে, এই ত্রিজগৎ আমারই কর্মত্রে। এর সমস্ত প্রাণী আমারই সন্তান। কিন্তু এই পৃথিবী দুঃখময় এবং কেবল মাত্র আমিই তোমাদের বাঁচাতে এবং রা করতে পারি। বুদ্ধের কর্মবাদী ধর্মে, কখনও এসব কথা নেই, কিন্তু মূল নিক্কোও নিওয়ানো অনুবাদ করতে গিয়ে জ্ঞান বিকাশ বড়–য়া ‘শান্তির জন্য নিবেদিত’ গ্রন্থে ৩৯ পৃষ্ঠায় এমন লৌকিক অবাস্তব স্ববিরোধী কথার অবতারণা করেছেন। এ বক্তব্য যদি ঠিক হয় তাহলে বুদ্ধের ধর্মদর্শন ঈশ্বরবাদী বা একেশ্বরবাদী ধর্মের মাপকাটিতে পড়ে। ইহা আসলে লোকাচার দৃষ্টিভঙ্গি।
মাজার পূজা বা জেয়রত : ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায় যে, বৌদ্ধধর্মের সমাজ সংস্কৃতিতে বর্তমান সময়ে ইসলাম ধর্মের লৌকিক ক্রিয়াকর্মের মাজার জেয়ারত প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু সেই মাজার জেয়ারত বড়ুয়া ও পার্বত্য বৌদ্ধরা মাঝে মধ্যে করে থাকে। সময়ের বিবর্তনে ইসলাম ভাবাদর্শী মাজার জেয়ারত বৌদ্ধধর্মের এক বিশেষ করণীয় পূজা হয়। বৌদ্ধ ধর্মীয় ত্রিপিটক সাহিত্যের কোথায়ও মাজার পূজা সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায় না। তা সত্ত্বেও কিন্তু বড়ুয়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কাছে জনমনে মাজার পূজা আছে। কালের বিবর্তনে বৌদ্ধধর্মের পতন ও বিলুপ্ত প্রায় হয়েছিল একথা নিঃসন্দেহ। কিন্তু তারই সুবাধে বৌদ্ধধর্মের মধ্যে নয়; বরং বড়ুয়া বৌদ্ধ সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে সর্বোপরি মানুষের অন্তরে এই মাজার পূজা বা মাজার জেয়ারত কালক্রমে বড়ুয়া বৌদ্ধদের একটি প্রথায় পরিণত হয়।১২
সেই ছিন্ন লোকরীতি মাজার পূজা বাঙালি বড়ুয়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুল ভাবে প্রচলিত। লোকচার ও কুসংস্কার আদৃত কাল্পনিক এই মাজার পূজা বা জেয়ারত। একটু সচেতন ভাবে ল্য করলে দেখা যাবে যে, এই মাজার বা দরগাগুলো বিশেষ করে গড়ে উঠেছে প্রায় নির্জন বনে জঙ্গলে কিংবা অজ্ঞ অশিতি দারিদ্র নিরান্ন এলাকায় বা কোন যাতায়াত ব্যবস্থার মাঝে মাঝে এলাকা জুড়ে। মহাকারুণিক গৌতম বুদ্ধ প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম শাস্ত্র ত্রিপিটকে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, এসো, দেখ, পর্যালোচনা কর, নিজে জানো, সমালোচনা কর এবং নিজেকে প্রশ্ন কর। যদি গ্রহণীয় হয় তাহলে গ্রহণ কর আর যদি বর্জনীয় হয় তাহলে বর্জন কর। এছাড়া মহাপরিনির্বাণ সূত্রে তিনি বলেছেন যে, বৌদ্ধধর্মের মধ্যে যা কিছু গ্রহণীয় তা রা কর আর কোন কিছু যদি তোমরা সম্যক ভাবে পরিবর্তন চাও তাহলে তা সম্যকভাবে বিচার বিবেচনা করে সংস্কারযোগ্য হলে সংস্কার কর। গ্রহণযোগ্য হলে গ্রহণ কর। তাই বৌদ্ধধর্মের সার্বিক মতাদর্শ সকলের নিকট গ্রহণীয়। এতে কুসংস্কারের কোন স্থান নেই। তাই বড়ুয়া বৌদ্ধরা যে মাজার পূজা করে তা লৌকিক পূজা বা লোকধর্ম।
মাজারে যিনি খাদেম থাকেন, তিনি মানুষকে নানাভাবে কুসংস্কারের পন্থায় উৎসাহিত করে থাকেন। যে সব বিভিন্ন পন্থার কথা মাজারের পীর সম্পর্কে বলে থাকেন আর যে উদ্দেশ্যে মানুষ যায় তাহলো- ক) সকলে পীরের মাজারে বা দরগায় আসে মানত করে ও মানসিক পরিশুদ্ধতা লাভের আশায়। খ) গাছ গাছড়া জাতীয় ঔষধ ও মাদলী কবচ প্রভৃতি দিয়ে থাকেন। গ) জল পড়া, তেল পড়া, ডাব পড়া প্রভৃতিও দেওয়া হয় আগত লোক সাধারণকে। ঘ) পীরের দরগায় ফুল, ধূপ, দীপ, বাতিসহ শিরনী দেওয়া হয়। ঙ) সন্তান কামনায়, ব্যবসায় সফলতার জন্য, রোগ নিরাময় কমনায় দরগায় ইট বাধা হয়, ফুল প্রদত্ত হয় ও তাবিজ নেয়া হয়। চ) গরু, ছাগল, মুরগী প্রভৃতি পীরের স্মরণে উদ্যাপন করে তা পরে হাজত মুক্ত করে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়ে থাকে। ছ) গরু, ছাগল, মুরগী প্রভৃতি পীরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে পরে রান্না করে সকলে খেয়ে থাকেন।
মানত করা : মানুষের মধ্যে মানত করার প্রবণতা প্রতিনিয়ত ল্য করা যায়। মানত সকলের চেনা-জানা শব্দ ও বিষয়। কি হিন্দু, কি মুসলিম, কি খ্রিষ্টান দেখা যায় বৌদ্ধদের মাঝেও মানত করার প্রথা প্রচলিত আছে। তাদের সকলের বিশ্বাস যে তার দ্বারা মানুষের মঙ্গল হয়; সফলতা লাভ হয়। উল্লেখ্য যে, তাদের কোন কিছু কাজ কর্ম, লেখা পড়া, ব্যবসা বাণিজ্য, মনের ইচ্ছায় যদি সফলকাম হয় তাহলে তারা কোন দরগা, মসজিদ, মন্দির সেবাখোলা বা চার রাস্তার মাথায় গিয়ে গরু, ছাগল, মুরগি, কবুতর ইত্যাদি মানতের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেবেন। তাদের মনের ইচ্ছা পূর্ণ হলে মানত করা জিনিস সেখানে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে থাকেন। এটাও আসলে হিন্দু, মুসলিম সমাজের তথা বড়ুয়া বৌদ্ধদেরও এক ধরনের কুসংস্কার। এটা আসলে কাল্পনিক লৌকিকতা, কারণ এসব মানত করার পেছনে বাস্তবভিত্তিক চিন্তা ধারার কিছুই প্রতীয়মান হয় না। আমরা জানি বৌদ্ধরা যে সকল ক্রিয়াকর্ম করে আর পূজা পার্বণ করে তা শুধু বৌদ্ধধর্ম ভিত্তিক যুক্তিনির্ভর ও স্বয়ং বুদ্ধ নির্দেশিত। আর এ মানত করার প্রথা বা কর্মবাদী বৌদ্ধধর্মের শাস্ত্রে কোথাও উল্লেখ নেই। তাই এ মানত করার প্রবণতা বাস্তবে লোকধর্ম ছাড়া আর কিছু নয়।
সত্যপীরের সিন্নি : বড়ুয়া বৌদ্ধদের ধর্মীয় বা সমাজ সংস্কৃতিতে মুসলিম সমাজে সত্যপীরের সিন্নি নামে একটি বিশেষ প্রথা প্রচলিত। এছাড়াও মানিকপীর, বদরপীর সাহেব ও মর্জ্জির সিন্নি দিয়ে থাকেন। সত্যপীর মুসলমানদের অবতার কিনা তানিয়ে অনেক মতানৈক্য আছে। এ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন, মুসলিম সমাজের অবতার বিশেষ সম্প্রদায়েরও সত্যপীর বহুদিন হতে ‘সত্য নারায়ণ’ আখ্যায় হিন্দু সম্প্রদায়েরও পূজা লাভ করে আসছেন। উভয় সমাজেই এই শ্রেণির মিশ্র পূজা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন কবি ফকির দাস উদার প্রাণে লিখেছেন-
‘দেখো থাকে পুরাণে, কোরান থাকে দেখো
জোই রাম রহিম দোনাহি হোয়ে একো।’
ক্রমে ক্রমে তা বৌদ্ধ বড়ুয়া সমাজে প্রবেশ করে। বৌদ্ধদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। লোক মুখে প্রচলিত আছে যে, যদি কারো অভাব বা দুঃখ বা কোন কাজে অমঙ্গল দেখা দেয় তাহলে সে যদি এই সত্যপীরকে স্মরণ করে বা মানত করে সিন্নি দেয়। তাহলে তার অভাব, অনটন, দুঃখ, দুর্দশা আর থাকে না। এই সিন্নি জাতীয় লৌকিক অপসংস্কৃতিক পূজা অর্চনাদি বড়–য়া বৌদ্ধদের মধ্যে দেখা যায়। বড়ুয়া ও পার্বত্য বৌদ্ধদের মধ্যে লৌকিক অপসংস্কৃতির প্রবণতা প্রায় বেশী ল্য করা যায়। প্রকৃত পে অশিতি, অজ্ঞ লোকের মধ্যে এ ধরনের লৌকিক কুসংস্কার প্রচলিত আছে। মূর্খ মানুষের মধ্যে লৌকিক কুসংস্কারসমূহ বাসা বেধে থাকে। বুদ্ধের প্রদত্ত উপদেশ ও বাণীসমূহের মধ্যে এবং বৌদ্ধধর্মের কোন শাস্ত্রে এ সত্যপীরের সিন্নির উপমা নেই। তদ্সত্ত্বেও বৌদ্ধরা লৌকিকভাবে এ সত্যপীরের সিন্নি বা পূজা করে থাকে। অধ্যাপক দিলীপ কুমার বড়ুয়া তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ‘সোয়া সের দুগ্ধ লাগে সোয়া সের আটা,
সুপক্ক কদলি লাগে সোয়া সের মিটা।’১৩
সত্যপীরের সিন্নির উপকরণ সমূহ- চাউল ১ পোয়া, কলা ৯টি (বিজোড়), দুটি পাত্র, দই, গুড়, নারিকেল, মোমবাতি, ধূপ, ফুল ইত্যাদি।
জীনভূত বা পরীতে পাওয়া : লোক সমাজের মধ্যে জিনভূত বা পরীতে পাওয়ার কুসংস্কার দেখা যায়। তারা মনে করে থাকে যে, রাতে বা ভর দুপুরে গাছ তলায় বা পুকুর পাড়ে গেলে মানুষের বা গর্ভবতী নারীকে পরীতে পাবে, ভূতে পাবে, জিনে পাবে। প্রত্যেক ধর্মে তার প্রথা প্রচলিত আছে। এই প্রোপটে হঠাৎ যদি কেউ অসুস্থ বা অন্য কোন কারণে দ্বায়ী কোন কিছু হয় তাহলে তাকে বলা হয়ে থাকে জিনে পেয়েছে, ভূতে পেয়েছে, পরীতে পেয়েছে ইত্যাদি। আর তাকে ভাল বা সুস্থ করা জন্য প্রয়োজন হয় বৈদ্য, গাছা, ফকির, ভিক্ষু, মৌলভি ইত্যাদি।
বাণ টোনা ও বৈদ্য: বাংলাদেশে প্রাচীন কাল থেকে প্রতিটি ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বহুলভাবে প্রচলিত হয়ে আসছে বাণটোনা, বৈদ্য ইত্যাদি কুসংস্কার ও লৌকিক কাজ কর্ম। লোক সমাজ বিশেষ করে বৌদ্ধ সমাজে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নিকট তা ওতপ্রতোভাবে জড়িত এবং বহুল জন সমাজে পরিচিত। বিশেষ করে মগ, মারমা, রাখাইন ও চাকমা বৌদ্ধরা সব সময় করে এবং করে আসছে। এ বাণটোনা ও বৈদ্য এর সম্পর্কে মানুষের লৌকিক ধারণা ও দুর্বলতা আছে। যেমন :
কোন লোকের সাথে যদি কারো শত্রুতা থাকে তার বিনষ্ট বা তি সাধন কিংবা অমঙ্গল অবনতি ইত্যাদি করার জন্য মিথ্যা কুসংস্কারের আশ্রয় নিয়ে করা হয় বান টোনা। বাণটোনা যে ফল দেয় তা লোক মনে প্রচলিত আছে। তারা মনে করে-বাণটোনা দ্বারা শত্রুদের তি হয়। এ বাণটোনা করার অজ্ঞাত ধারণা প্রবল বিশ্বাস বিশেষ করে গ্রামের অশিতি সমাজে বিদ্যমান। এর আবার আর একটি ব্যাপার হল বৈদ্য দ্বারা অশুভ বাণটোনা থেকে রা পাওয়া। বাঙালি বৌদ্ধ সমাজে এ ধরনের বৈদ্যের আনাগোনা দেখা যায়। তারা বলে বাণটোনা থেকে রা করতে পারবে, রোগের উন্নতি করে দিতে পারবে। এ ছাড়া বৈদ্যেরা কোন লোকের রোগ হলে, হারানো গেলে, মানুষের অমঙ্গল দেখা দিলে নানা বিষয় সম্পর্কে হুবহু বলে দিতে পারে। এরা আবার ভালো করার জন্য নানান কথা বলে থাকে।১৩ বৈদ্যরা বাণটোনা কেটে রোগ ভালো করার জন্য প্রথমে কি হয়েছে দেখার জন্য নিবে কিছু টাকা, তার পরিমাণ এ ধরনের – ১.২৫, ৩.২৫, ৫.৫০ ইত্যাদি হারে। রোগ নির্ণয় করে পরে যা উপকরণ প্রয়োজন হয় কলার মোয়া, কচি ডাব, মোমবাতি, ধূপকাটি, কলা, মরিচ, পেঁয়াজ, রসুন, আদা .৫০ অথবা ১ কেজি, ১ ছটাক ভালো সরিষার তৈল, কদু বা লাউ, গৃহের কোণের শন ইত্যাদি ইত্যাদি।
নানা রোগের জন্য বৈদ্য নানা উপকরণ দিয়ে থাকেন। আর শরীরের সাথে দেওয়া হবে তার কাল্পনিক তৈরি দামী (২০০- ১০০০ টাকা) তাবিজ যাতে অপদেবতা বা শত্র“ তাকে কোন তি করতে না পারে, যেন কোন অবনতি বা অমঙ্গল না হয়। যুগে যুগে কুসংস্কারে বশবর্তী হয়ে তা মানুষের মধ্যে, সমাজের মধ্যে প্রচলিত হয়ে আসছে। এসব কিছু কৌশল অবলম্বন প্রতারণা বা লৌকিকতা ছাড়া আর কিছু নয়। বৌদ্ধধর্মের মধ্যে এমন কোন শাস্ত্র অনুসরণ করার জন্য বলা হয়নি। কিন্তু বৌদ্ধরা তা করে বস্তুত লৌকিকতার আশ্রয়ে যার কোন বাস্তব বা মৌলিক ভিত্তি নেই। বৈদ্যরা সহজ সরল অশিতি ও গ্রাম্য মানুষের কাছে গুরুবাবার আশ্রয় নেওয়ার নামে প্রতারণা করে থাকে। সে কৌশল অবলম্বন করে থাকে একজন তুলারাশি জাতকের লোক ঠিক করে গাছা বসায়। তার আসন তাকে দণি বা পূর্বমুখী যার যেমন ইচ্ছা তেমনি বসায়। বসার আসনে থাকে মঙ্গলঘট, এতে মন্ত্রপূত পানি নেওয়ার নামে গাছার মুখে ও মাথায় ছিটিয়ে দেয়, কাঁসা বাজায়, ধূপ জ্বলায়। বৈদ্যের মাকে অর্থাৎ লোক দেবীকে আবাহন করার জন্য গান গেয়ে থাকে। যেমন-
আইজ রে মা-মঘিনী মইঘ্যা রাজার ঝি
আইয় তুই সোনার নাধং কানত দি
তোয়ার জয়গান গাইতে মাগো আর জনম যায়
মগধেশ্বরী মারে মা শ্রীঘ্র দেখা দেঅ
তোয়ার আসন সজায়ইয়াছি বড় আশা করে
তুমি মাতা দিষ্টি দেঅ এই গাছার উ অরে
তোয়ার জলি দিয়ম মাগো শনি মঙ্গলবারে
তুমি মাতা কিরপা করঅ এই রোগীর উঅরে।১৪
ইত্যাদি বলে থাকে ছলনা বশে।
বৃক্ষ পূজা : বৌদ্ধরা বৃকে অর্থাৎ বৃ দেবতাকে প্রায় সময় পূজা ও বন্দনা করে থাকে। বড়–য়া ও পার্বত্য বৌদ্ধরা অমাবশ্যা ও পূর্ণিমা অষ্টমীর সময় সকালে বৃ পূজা করে থাকে। তাদের ধারণা বুদ্ধ বোধিবৃ তলে বসে ছয় বৎসর কঠোর তপস্যা সাধনা করে বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন, তাই বৃকে পূজা ও বন্দনা করে থাকে। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম মতাদর্শে বৃকে পূজা করা কুসংস্কার। কারণ বুদ্ধ নিজে কখনো এমন উপদেশ কাউকে দেননি যে বৃকে পূজা কর। বরং বুদ্ধ আমৃত পরায়ণ মানুষ যেন নিজেকে শুদ্ধ করে তার জন্য বলেছেন। প্রকৃত অর্থে বৃ বৌদ্ধধর্মে লৌকিক পূজা। কিন্তু দেখা যায় বোধিবৃরে ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনা করে শ্রীলংকাবাসীরা সবসময় অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে বোধিবৃ পূজা করে থাকে।
আট্কী মা পূজা : চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় তাকে আট্টক্কিনি পূজা বলা হয়। এ আট্কী মা পূজা বাঙালি বৌদ্ধদের বহুল প্রচলিত একটি পূজা। আর এই পূজা জনমানসে বহুলভাবে সমাদৃত হয়ে আসছে। বলা যায় সমাজ ব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে কুসংস্কার প্রথা। প্রচলিত আছে যে কেউ যদি বিপদে পড়ে বা ব্যধিগ্রস্ত হয় তাহলে এইসব কিছু থেকে অমঙ্গল রা পাওয়ার জন্য এই পূজা অর্চনা করে থাকে। বাস্তব প্রোপটে এই আট্কী মা পূজার কোন ভিত্তি আছে বলে মনে হয় না।
বৌদ্ধধর্ম সত্যের ধর্ম। লৌকিক বা কুসংস্কারের কোন স্থান নেই বৌদ্ধধর্মে। অথচ তবু মানুষ কুসংস্কার ও লৌকিকভাবে বিশ্বাসী হয়ে এ পূজা করে থাকে। বাঙালি বড়–য়াদের লৌকিকতা ছাড়া আর কিছু নয়। এবার আট্কীমার পূজার উপকরন সর্ম্পকে আলোচনা করা যেতে পারে। যদি পূজা দুটি বসানো হয় তাহলে পূজার উপকরণ লাগে কলা ১৬টি, পিঠা ১৬টি, দূর্বাঘাস (দুলা কের) ১৬টি, কাঁঠাল পাতা ১৬টি, যব ২টি, কলাপাতা ২টি, মোম ও ধূপ ১ প্যাকেট, প্রতিটি ভাগে থাকবে সিন্দুর ইত্যাদি।
এই আট্কী মার পূজার একটি ঐতিহাসিক গল্প আছে। পূজা করার সময় এ গল্প বলতে হয়। গল্প না বলে পূজা ভাঙ্গা যায় না। আর এ পূজার গল্প বাঙালি বৌদ্ধ পুরুষ ও নারীরা কম বেশী জানে। প্রতিটি পূজায় এ গল্প সকলের সামনে বলা হয়। গল্পের নমুনা বা কিছু অংশ প্রদত্ত হলো – এক ছিল রাজা তার ছিল এক মেয়ে। হঠাৎ যখন রাজা তার মেয়ের কথা জানতে পারল তখন যে প্রতিজ্ঞা করল আগামী কাল সকালে যাকে পাবে তার সঙ্গে তার বিবাহ দিয়ে দিবে। আর এ কথা তার মেয়ের খেলার সাথী শুনে তার বাবাকে বলে দিল তখন ঐ মেয়ের বান্ধবীর বাবা সকালে রাজার বাড়ীতে গিয়ে…..।
নদীতে মনসা পূজা : বেহুলার বাসর ঘর একটি ঐতিহ্যবাহী স্মৃতি। হাজার হাজার বৎসর পূর্ব থেকে মানুষের মনে নিয়ে এসেছে এক মহা বিস্ময়, মহাজিজ্ঞাসা। এই স্মৃতি চাঁদ সওদাগরের দৃঢ়তা, পদ্মার কোপ, মনসা মঙ্গল, নিতাই বাবু ও বেহুলার আলৌকিক সতীত্বের করুন কাহিনির সঙ্গে বিজড়িত। প্রাচীন প্রবীণ ব্যক্তিদের মুখ থেকে যা কিছু পাওয়া গেছে তাও এতে সংযুক্ত হয়েছে। কাহিনি স্থল বগুড়া। বেহুলা ও লক্ষ্মিন্দরের কাহিনি সেন যুগের অনেক পূর্বেকার ঘটনা। বেহুলার বাসর ঘর একটি কাল্পনিক মনুমেন্ট। বাসর ঘর বেহুলার দুঃসময় রজনীর একটি অম্লান স্মৃতি চিহ্ন। অভাগিনী বেহুলা তার মৃত স্বামী লক্ষ্মিন্দরকে নিয়ে বাসর ঘরের দরজায় বসে অঝোর নয়নে কাঁদছে। কারণ লন্দিরের লোহার বাসর ঘর। তাতে এ করুণ বিলাপ মনে হয় আজো শোনা যায়। বেহুলা বদ্ধ দরজার পাশে বসে বিনয় কণ্ঠে গাইতে লাগলো-
দাও মা দরজা খুলে
সিথির সিদুঁর মুছিয়াছি নয়নের জলে,
বাসর ঘরে দংশিল মা কাল নাগ আসিয়া,
তোমায় বুঝাব মাগো কোন ধন দিয়া।১৫
বেহুলার ধোপানীর প্রতিউত্তরে বললেন,
বিয়া রাতে পতিমোর খাইল নাগিনী
পতি লয়ে ভেসে যাই আমি অভাগিনী
কি আর কহিব মাসী তোমার নিকট
অভাগিনী নারী আমি পড়েছি সংকটে।
লক্ষ্মিন্দরের পিতা ছিলেন চাঁদ সাওদাগর, মাতা সুনুকা রাণি। বেহুলার পিতার নাম মুত্তেশ্বর ওরফে বাসোবানিয়া আর মাতার নাম কমলাদেবী। বেহুলার করুণ কাহিনী আলোকপাত করতে গেলে পদ্মাদেবীর কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। পদ্মার কূলে জন্ম হয়েছে বলে এই দেবীর নাম পদ্মা। এই দেবী বিষহরী নামেও পরিচিত। পদ্মা অযোনি সম্ভাবা চতুর্ভূজা ও ত্রিনয়ী স্বামীর নাম জরৎকারু মণিরাজ। পদ্মাদেবীর আটটি সর্প সন্তান ছিল।
পদ্মা পুরাণে আছে :
‘কাঁদরে সুনুকা দেবী কাঁদে সদাগর
কাঁদে আজো বেহুলার বিরহ বাসর।’
প্রকাশ থাকে যে এই দেবীর পূজা মন্সা পূজা। শ্রাবণ সংক্রান্তিকে অনুষ্ঠিত হয়। তবে স্থান বিশেষে সময়ের ব্যবধান বিচিত্র নয়। পূজা সকাল ১০-১২ টায় নদীতে ভেসে দিয়ে থাকে। ভেদে দেওয়ার আগে জোয়ার বা উলু দিয়ে থাকে আর সাথে সাথে স্নান করে থাকে। কিন্তু লোক এই মন্সা পূজা ডান হাতে এবং কিছু লোক বাম হাতে দিয়ে থাকে এরও অনেক কারণ আছে। ভেওলা উজান যাওয়ার ছয়মাস পর লন্দির জীবিত হওয়া, যাদু দিয়ে জীবিত মৃত হওয়া ইত্যাদি। হিন্দুধর্মের জাত কাহিনীর এই বেহুলা লèিন্দর তথা পদ্মা দেবীর মন্সা পূজা লৌকিক কুসংস্কার রীতি হিন্দুধর্মে নয়। যুগের সন্ধিণে বাঙালি বৌদ্ধদের রীতি-নীতিতেও পরিণত হয়। বড়–য়া বৌদ্ধদের মাঝে এখনো কিছু লোক এই লৌকিক মন্সা পূজা অপসস্কৃতির পূজা নদীতে বা পুকুরে তার স্মরণে পূজা দিয়ে থাকে। মান্সা পূজার উপকরণ সাধারণত যেসব লাগে তা হল- চাউল, দুধ, কলা, নারিকেল, ফুল, আখ, মোমবাতি, আগরবাতি, দুলাকের কলার বাক্ল, সিদুঁর প্রভৃতি।
নদীতে (গাং) পূজা : বড়ুয়া, চাকমা ও মারমা বৌদ্ধদের মধ্যে আর একটি হল নদীতে পূজা। যখন ঘট তোলার জন্য পুকুরে বা নদীতে গিয়ে ঘট ও ফুল পরিষ্কার করে তৈরি করে। তখন কিছু ফুল ও অন্যান্য পূজার উপকরণ নদীতে বা পুকুরে ভাসিয়ে দিয়ে থাকে। বিজ্ঞজনের মতে এটি হল নদীতে উপগুপ্ত স্থবিরকে পূজা করা। গ্রামে গঞ্জে এ প্রথা বিশেষ ভাবে প্রচলিত কিন্তু বার পূজা দেয় তারা কেন দেয় তা প্রকৃতগত ভাবে জানে না। বৌদ্ধধর্মের কোথাও এ পূজা সম্পর্ক জানা যায় না। তথা বড়–য়া বৌদ্ধরা তা করে থাকে। নদীতে বা পুকুরে এ পূজা দেওয়ার কাল্পনিক প্রথা লৌকিকতা ছাড়া আর অন্য কিছু নয়। সকল সচেতন আধুনিক যুগের মুক্ত মনের অধিকারী মানুষকে এ লৌকিক কুসংস্কার পরিহাস করে সত্যের অনুসন্ধান করতে হবে, তখনই সমাজ কুসংস্কার মুক্ত হবে, সত্য ধর্ম, সত্য ধারণা, সঠিক ইতিহাস জানতে সক্ষম হবে।
বৌদ্ধধর্মে বিভিন্ন দেব দেবীর পূজা : বৌদ্ধ সংস্কৃতি চর্চার উজ্জল নিদর্শন শিলালিপি ও তাম্রশাসনের মধ্যেও স্থানে স্থানে বর্ণিত আছে। বাংলার ইতিহাসের পালযুগ ছিল বৌদ্ধধর্মের সুবর্ণ যুগ। মঙ্গল কাব্যের দেবদেবীর পরিকল্পনা ও পূজা পদ্ধতির মধ্যে বুদ্ধমূর্তি তত্ত্ব এবং লোকাচার, ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রীর বিধি, লোকিক আচার ও ধর্ম বিশ্বাস সমন্বিত হয়েছে। এইজন্য মন্সা, চণ্ডী, ধর্ম ঠাকুর, শিব, দেবদেবী পরিকল্পনার সঙ্গে বিমিশ্রিত হয়ে পৌরাণিক দেবদেবীদের সঙ্গে একাসন অধিষ্ঠিত হয়েছেন।১৬
ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মে মহাশক্তির পূজা বিশেষ স্থান অধিকার করে। অন্যান্য দেব দানবের মূর্তির পাশে স্থান পেল ভীষণ দর্শনা মহাশক্তিরুপিনী নারীমূর্তি। ক্রমে এদের পাশে স্থান পেল ভুত, পিচাস ও পিচাশিনীদের মূর্তি। অলৌকিক শক্তির আধার রূপে এদের পূজা শুরু হয়। সপ্তম শতকের মধ্যভাগে ভারতে অনেক বোধিসত্ত্ব মূর্তির আবির্ভাব ঘটে। এসব মূর্তির পাশে ও স্থান পেয়েছিল নারীমূর্তি। এবং ভূত পিচাশাদির করাল মূর্তি। ওর পর নানাবিধ পূজা, ক্রিয়াকলাপ আচার উপাসনা ইত্যাদি বৌদ্ধধর্মে প্রবেশ করে। বৌদ্ধধর্মের বিকৃত হয় এবং এ বিকৃত বৌদ্ধধর্ম প্রথমে মধ্য এশিয়া দণি এশিয়ার রাষ্ট্রগুলিতে প্রচারিত হয়। পরবর্তী তিন চার শতাব্দী ধরে অন্তসার শূন্য এ বৌদ্ধধর্ম আরও শোচনীয় পর্যায়ে এসে পড়ে।
এবার অতীতে এবং বর্তমানে বৌদ্ধধর্মের অন্তরালে সমাজ সংস্কৃতিতে যে সব লৌকিক বা কাল্পনিক বিকৃত দেবদেবীর পূজা করতো এবং হচ্ছে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-
(ক) মাকাল ঠাকুর : প্রাচীন ভারতবর্ষে যখন বিভিন্ন প্রকার মতবাদ প্রচলিত ছিল, সেখান থেকে বিকৃত হয়ে এ মাকাল ঠাকুরের পূজা করা হতো। সে লৌকিক পূজা বৌদ্ধদের একটি দেবতা হল মাকাল ঠাকুর। বর্তমান ধর্ম বিশ্বাস ও সমাজে এর পূজা দেওয়ার প্রথা মাঝে মাঝে দেখা যায়। এটি বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের মৎস্য জীবিদের উপাস্য এক লৌকিক দেবতা। মৎস্যজীবিরা আবার দেবীর পূজাও করে থাকে তার মধ্যে বিশা লক্ষ্মী, খাল কুমারী প্রভৃতি দেব-দেবীর পূজা। বাঙালি বৌদ্ধদের সচেতনা ও আধুনিক শিায় শিতি হচ্ছে দিন দিন। তাই প্রাচীন কালের এই লৌকিক, কাল্পনিক, অপসংস্কৃতিসমূহ পরিহার করছে। অদূর ভবিষ্যতে এর বিলুপ্তি হবে বলে ধারণা করা যায়।
(খ) পাঁচু ঠাকুর : দেবদেবীর পূজা পাক ভারতে বহুল প্রচলিত ছিল। লোকরীতিতে আজো পল্লী অঞ্চলে অনেক বিচিত্র ও ভয়াবহ আকৃতির লৌকিক দেবতার পূজা পার্বণ দেখা যায়। এ পাঁচু ঠাকুরকে সকলে পেচোঁ ঠাকুর নামে পূজা দিয়ে থাকে।
(গ) ধর্ম ঠাকুর : মহাযানী বৌদ্ধদের উপাস্য ছিল ধর্ম ঠাকুর। বৌদ্ধ পার্বণ বা পূর্ণিমার সময় ধর্ম ঠাকুরের পূজা অনুষ্ঠিত হতো এবং তাদের সকলে ধর্ম ঠাকুরের প্রতি ছিল অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। তৎকালে বৌদ্ধদের ধারণা ছিল একে পূজা দিলে নৈবেদ্য ফল লাভ করা যায়। কিন্তু সে বিকৃত দেবতা পূজা বর্তমানে সমাজে প্রায় বিলুপ্ত।
(ঘ) বৌদ্ধ দেবদেবী : প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্ম বলতে মহাযানীদেরই বুঝায়। এই মহাযানীরা বুদ্ধকে একমাত্র পূজ্য স্বীকার করতেন না, নানা দেবদেবীর উপাসনা করতেন। সকল প্রকার ধর্মমতও স্বীকার করতেন। খ্রিষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে প্রচলিত তান্ত্রিক ধর্মের প্রভাবে মহাযানীদের তিনটি শাখার সৃষ্টি হয়। কালচক্রযান, বজ্রযান, মন্ত্রযান ও সহজযানীরা বিশালাীকে তাদের অন্যতম উপাস্য করে নেয়। এদের সাহিত্য চর্যাপদে বাচদালী নামে যে দেবীর উল্লেখ আছে তা ‘বাসলী’ বলে মনে হয়।১৭ সাধারণ মানুষের ‘বাসলী’ দেবীকে রোগ মুক্তি নজর পড়া অলণ কুলণ ইত্যাদি থেকে রা পাওয়ার জন্য আজও তেমাথা বা চৌরাস্তার মোড়ে পূজা অর্চনা করে থাকে।
ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে বলা হয়েছে যে-
‘মনের হরিয়ে আজি পূজিব বাসলী
নবল বিপ সম্মুখে দিব বলি।’
আবার অনিল পুরাণে উল্লেখ আছে-
‘মন দিয়া শোন সেই বাসুলী ব্যবহার
তাহার উঠিল কলঙ্ক আসুর ভাতার।’
(ঙ) অন্যান্য দেবদেবী : অতীতে অসংখ্য দেব দেবীর পূজা করা হতো তার প্রভাব আজো আছে। যেমন – হাড়িনী বা হারীতি, শীতলা দণিরায় (একজন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য ছিলেন), ত্রেপাল, সত্যপীর, পীরঠাকুর প্রভৃতি। বৌদ্ধরা হিন্দুধর্মের লক্ষ্মী পূজা, শনি পূজা, কার্তিক পূজা, মগদ্বেশ্বরীর পূজাও করতেন।
বর্তমান প্রোপটে সমাজ অঙ্গনের দিকে তাকালে ল্য করা যাবে যে- বাঙালি বৌদ্ধরা সেই প্রথম থেকে বিরোধিতা করছে। এ দেব দেবীর পূজা বড়–য়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে বিশেষ আধিপত্য জুড়ে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। শুধু ভিন্ন মতে কারণে বিকৃত ভাবে কিছু দেবদেবীর পূজা বড়–য়া বৌদ্ধরা করে ছিল এবং সে দেবদেবীর পূজা আজোবধি মাঝে মাঝে দেখা যায়। প্রকৃত পে এ দেব দেবীর পূজা কাল্পনিক, লৌকিক পূজা, চট্টগ্রামে নিভৃত গ্রামের অশিতি অজ্ঞ, দারিদ্র লোকের মধ্যে এ দেবদেবীর পূজা কিছুটা কম হয়ে থাকে। মিথ্যা ধারণায় বশবর্তী হয়ে এ লৌকিক দেবদেবীর পূজা করা হয়।১৮
কালী পূজা : হিন্দুধর্মের ধর্মীয় শাস্ত্র পুরাণের বর্ণনা মতে, হাজার হাজার বছর পূর্বে এক সময়ে রক্তবীজ নামে এক অসুর কোন এক শক্তিশালী দেবতা যা দেবীকে বসে এনে অমর বর লাভ করেছিলেন এবং লাভ করার সাথে সাথে স্বর্গ রাজ্য আক্রমণ করে স্বর্গের রাজা ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবদেবীকে মর্তে এনে দিলেন। ফলে তারা অকল্পনীয় দুঃখ দুর্দশার মধ্যে দিনযাপন করতে লাগলেন। দেবদেবীর চেষ্টায় নিজেদের সম্মিলিত শক্তির রূপকালী রক্তবীজ বধের জন্য যুদ্ধ শুরু করেন। আর এক সময়ে রক্তবীজ পরাজিত হন। এই তাৎপর্যের একটা রূপ/অবস্থা তৈরি করে পূজা করেন। মহাপরী এক শক্তিশালী কালী দেবীর শক্তিও কৌশল লাভের জন্য তার পর থেকেই কালী দেবীর অনুসারীরা পূজা শুরু করেন। কিন্তু বর্তমানে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজেদের তথা নিজ সমাজের অকল্যাণ বা অশুভ লণ দূর করার জন্য কালী পূজা করেন।
হিন্দুরা এক বাক্যে স্বীকার করে থাকেন যে, এ কালি দেবী এক মহান শক্তির দেবী। ১৯ মানুষ যেকোন জাগতিক বিপদ আপদ হতে রা পেতে যেন শক্তিমানের শরণাপন্ন হয় ঠিক তেমনি আধ্যাত্মিক ও জাগতিক সব বিপদ আপদ হতে মুক্তি বা রা পাওয়ার জন্য মানুষ কালী পূজা করে থাকে। প্রথম দিকে কলকাতায় কালী পূজা অনুষ্ঠিত হয় বলে ধারণা করা হয়। হিন্দুদের কালী পূজাকে বাংলাদেশী বড়ুয়ারা বর্তমানে না করলেও এক সময় এ পূজার ব্যাপক প্রচলন ছিল। প্রকৃত অর্থে এটি একটি লৌকিক পূজা বিশেষ। বৌদ্ধধর্মের কোন শাস্ত্র তথা বৌদ্ধ সমাজে এ পূজার কোন স্বীকৃতি নেই।
ভাতরান্না ও কার্তিক পূজা :
আশ্বিনে রান্না, কার্তিকে খায়
যে রব মাগে সে রব পায়।
যে রব মাগে অর্থাৎ প্রার্থনা করে তা পূরণের আশায় মানুষ এ কার্তিক পূজা বা কার্তিকের পান্তা ভাত রান্না করে থাকে। বস্তুত এ কার্তিক পূজা হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান পূজা।২০ এ পূজা বাঙালি বৌদ্ধ সমাজে বহুল ভাবে সমাদৃত। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল বা স্থান বিশেষে বড়ুয়া বৌদ্ধরা এ কার্তিক পূজা বা কার্তিকের ভাত রান্না করে থাকে। বাঙালি বৌদ্ধদের মাঝে প্রচলিত আছে যে কোন লোক যদি তার মনের আশা, বা অভাব অনটন, দুঃখ মুক্তি, যশখ্যাতি অর্জন ইত্যাদি থেকে রা বা উন্নতি লাভ করার জন্য যদি এ কার্তিক পূজা করা হয় তা হলে তার সে আশা পূরণ হয়। লোক সমাজে এ পূজার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। এটি লৌকিক কুসংস্কার ছাড়া আর কিছু নয়। এ ধরনের অনেক অলৌকিক অবাস্তব কাল্পনিক ও কুসংস্কার পরিপন্থী পূজার কথা প্রচলিত আছে এবং মানুষ তা অনুসরণ করছে। আসলে এসব লৌকিক পূজা পার্বণ।
সীবলী পূজা : সুন্দর ও অসুন্দর, বাস্তব আর লৌকিকতার মাঝে মানুষের বসবাস। সুন্দর চিন্তা চেতনা মানুষকে নানাগুণে গুণান্বিত করে। গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক। তাঁর ধর্মের মধ্যে কাল্পনিক, কুসংস্কার, অবাস্তব ও লৌকিক বলতে কিছুই ছিল না। কুসংস্কার ও কাল্পনিকা বর্জিত ধর্ম হল বৌদ্ধধর্ম। বুদ্ধ শুধু শাশ্বত ও চির সুন্দর অমৃত বাণী প্রচার করেছিলেন।
বুদ্ধের সময়ে পূজার কোন বিধান ছিল না এবং বুদ্ধের পরিনির্বাণে শত শত বৎসর পরেও সীবলী পূজা করা হতো না। যতদূর বিশ্বাস বুদ্ধের দেশিত, প্রচারিত ও প্রসারিত রীতি নীতিকে ঘিরেই বৌদ্ধধর্ম ও Buddhist Culture একথা বিশ্বাস করতে দ্বিধা নেই যে বুদ্ধের সময় বুদ্ধের মতাদর্শ ও বাণী লিখিত হয়নি।২১ প্রাজ্ঞ পণ্ডিত ভিক্ষু, দার্শনিক ও বিদগ্ধ ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় বুদ্ধবাণী ত্রিপিটক সংকলিত হয়। এই আলোচনা এতো গভীরে না নিয়ে সংক্ষেপে সীবলী পূজা কথা বলা যাক।
বাংলাদেশে বড়ুয়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে শীতলা পূজা ও তারাদেবীর পূজা করার প্রথা প্রচলিত। মূলত এ শীতলা ও তারাদেবী ছিল হিন্দুদের লৌকিক দেবতা পূজা। বৌদ্ধদের মধ্যে এ শীতলা ও তারা দেবীর পূজা পরিহার করার জন্য সীবলী পূজা প্রথা চালু করা হয়। বাংলাদেশের বৌদ্ধ পণ্ডিত বিশুদ্ধাচার মহাস্থবির এ সীবলী পূজার উদ্ভব করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলার কোথাও এ সীবলী পূজা প্রচলিত ছিল না। বিশুদ্ধাচার তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় লিখেছেন মহালাভী সীবলী স্থবিরের ব্রত কাহিনি। তিনি যে পুস্তক লিখেন তার নামকরণ করেন ‘সীবলী স্থবিরের ব্রতকথা’।২২ উক্ত গ্রন্থে লাভীশ্রেষ্ঠ অর্হত সীবলীর পুর্ণজীবন বৃত্তান্ত, গর্ভে বসবাস, জন্ম, নামকরণ, প্রব্রজ্যা, বুদ্ধের দর্শন, ভিু সংঘের সাক্ষাত, স্রোতাপত্তি ও অর্হত্ব লাভ, পুর্নজন্মের কর্মফল, পঞ্চশত ভিক্ষু ইত্যাদি। সীবলীর পিতা ছিলেন লিচ্ছবি রাজ মহালী কুমার আর মাতা ছিলেন সুপ্রবাসা রাণী। সীবলী কুমার সাত বৎসর সাত মাস গর্ভে মহাদুঃখী ভোগ করে জন্ম নিয়েছিলেন।
প্রচলিত আছে যে, সীবলী পূজা করলে মানুষের দুঃখ দুর্দশা দূর হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি হয়, খাদ্য বস্ত্র অভাব দূর হয়। দারিদ্রের বিত্ত, ধনীর মহাধন লাভ হয়। শত্রুতা থাকলে মিত্রতা লাভ হবে। জলে স্থলে যজ্ঞ দেবতা থেকে রা, সীবলী গুণকথা স্মরণ করলে মুক্ত হওয়া যায়। বৌদ্ধরা আজও বিশ্বাস করেন সীবলী পরিত্রাণ সূত্রপাঠ ও পূজা করলে কেউ অভাবী হন না। তাই বৌদ্ধরা ঘরে ঘরে সীবলী পরিত্রাণ সূত্র পাঠ ও সীবলী পূজা করেন। এ সীবলী ব্রতকথা নামক পুঁথি বা কাহিনী পড়তে হয়। পূজার সময় বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এ সীবলী পূজা এক ধরনের দেবদেবীর পূজার প্রথা রহিত বা দমন বা সাজ থেকে পরিহার করার জন্য এ প্রথা প্রচলন করা হয়। বুদ্ধের মতাদর্শ ও উপদেশবাণী ছাড়া সব কিছুকেই কুসংস্কার ও মিথ্যা বলে ধারণ করা হয়। সে দিক থেকে সীবলী পূজা লৌকিক পূজা। সময়ের প্রোপটে বৌদ্ধধর্মকে রার্থে সীবলী পূজা প্রচলন ধর্ম ও সমাজের জন্য ছিল মঙ্গলপদ। সুখ লাভ, দুঃখ দুর্দশা কিংবা বিপদ হতে মুক্তি লাভে মানুষ মানত স্বরূপ এ পূজা লোকাচারে প্রচলিত আছে।২৩
বৌদ্ধশাস্ত্র ত্রিপিটকে থেরগাথা গ্রন্থে এবং অন্যান্য পুস্তকে সীবলীর জীবন কাহিনি ও সীবলী পরিত্রাণ সূত্র আছে। সীবলী পূজার নানা উপকরণ হল মধু, ঘি, নারিকেল, চিড়া, আপেল, কমলা, মুড়ি, কলা, বিস্কুট, পেপে, আখ, মঙ্গলঘট, ছবি (বুদ্ধ ও সীবলী), ফুল, পান, সুপারি, মোম, ধূপ ও অন্যান্য উপকরণ। সীবলী পূজা করার সময় এক সাথে বুদ্ধ পূজাও করা হয়। পূজার সময় সীবলী ও বুদ্ধের ২টি ছবি সম্মুখ ভাগে রাখতে হয়।
সীবলী স্থবির বন্দনা : বৌদ্ধ শাস্ত্রে সীবলী স্থবিরের পালি ভাষায় বন্দনা হলো- সীবলী যং মহাথেরো লাভী নং সেটা তং গহতো মহন্তং পুঞঞাবতং তং অভিন্দামি সব্বদা।
বিভিন্ন সাহিত্যের উদ্ধৃতি থেকে প্রমাণিত হয় যে, পরিত্রাণ সূত্রের উদ্ভব বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পরবর্তী অন্যূন একশত বৎসর পরবর্তী যেমন রতন সূত্র, খণ্ড পরিত্ত, মেরাপরিত্ত, ধজগপরিত্ত, আটানটিয় পরিত্ত, আঙ্গুলিমাল পরিত্ত ইত্যাদি। বৌদ্ধ গৃহস্থদের বিশ্বাস জালো হাজালো জালং মহালাং জাল্লি, রিত্তি, মিত্তি, বিত্তি, ধনি, ধারণীতি -এ মন্ত্র পাঠক করে ধুল পাড়া দিলে গৃহের আগুন নিবে যায়, মিথ্যা ধারণা বশবর্তী হয়ে পড়ে। ফলে মৌলিক বৌদ্ধধর্ম লুপ্ত হয়ে পরিত্রাণ ও ধারণীর লৌকিকতা বৃদ্ধি পেতে থাকে।
মাংস ভক্ষণ : মাংস খাওয়া সম্পর্কে আলোচনার আগে আলোচনা করা যাক ভগবান বুদ্ধের পঞ্চনীতি নিয়ে। পঞ্চশীল হল- প্রাণী হত্যা থেকে বিরত, অদত্ত বস্তুগ্রহণ/ চুরি হতে বিরত, মিথ্যাকথা হতে বিরত, অবৈধ কামাচার হতে বিরত, সুরা-মদ/নেশা জাতীয় বস্তুগ্রহণ হতে বিরত থাকা। আমরা বুদ্ধের প্রচারিত মতকে দৃঢ়ভাবে ধারণ ও পালন করে থাকি। কিন্তু সকলে বলে থাকি যে প্রাণী হত্যা করা মহাপাপ। আসলে বুদ্ধ এমন করে উপদেশ করেননি; কখনও মহাপাপ বলে ভাষণ করেননি। তিনি বারংবার উপদেশ দিয়েছেন তোমরা প্রাণী বধ বা হত্যা থেকে বিরত থাকিও। অর্থাৎ অকারণে প্রাণী বধ না করা। মানুষকে চিরাচরিত নিয়মে জীবন যাপন করতে হলে কিছু না কিছু অবলম্বন করতে হয়। একটার উপর একটা নির্ভরশীল। বুদ্ধের কার্যকারণনীতি হল কোনটি বাদ দিয়ে মানুষের জীবন চলে না। এর অর্থ এই নয় যে, অহেতুক ভাবে কিছু করা। মানুষের জীবন ধারণ করতে গিয়ে প্রাণী বধ করত হয়। কিন্তু তা আমরা প্রাণী হত্যাকরলেও তার প্রতি অত্যন্ত বিমুখ। সম্যক দৃষ্টিতে প্রাণীবধ অপরাধ। কিন্তু জীবন ধরনের তাগিদে তা ত্রে বিশেষে বধ হয়।
সমাজে প্রথা সিদ্ধরীতি হলো বাঙালি বড়ুয়া বৌদ্ধদের গরু ও মহিষের মাংস খাওয়া যাবে না। আর প্রচলিত আছে যে, বড়ুয়া ও পার্বত্য বৌদ্ধদের অন্যতম প্রিয় খাদ্য শুকর, ছাগল, মুরগি মাংস। কি করে তা হতে পারে সবইতো প্রাণী। খেতে হলে বধ করে খেতে হবে। বৌদ্ধদের প্রচলিত রীতি নীতি মতে, প্রমার্জন অর্থে প্রাণী হত্যা না করে ক্রয় করে মাংস খাওয়া যাবে। অর্থাৎ পরোভাবে বলা। সুক্ষ্মদৃষ্টিতে এ নিয়ে একটু ভাবলে অনুধাবন করা যায় এটা এক ধরনের সামাজিক লোকাচার।
বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ এর পূর্বে প্রধান সেবক আনন্দকে বলেছিলেন যে, আনন্দ দশ প্রকার প্রাণীর মাংস ভণ করা নিষেধ। সেই দশ প্রকার প্রাণী কি কি ? যথা: মানুষের মাংস, বাঘ্রে মাংস, দীপিকার মাংস (বিড়াল), সিংহের মাংস, কুকুরের মাংস, অশ্বের মাংস, হস্তির মাংস, নেকড়ে বাঘ্রের মাংস, ভল্লুকের মাংস এবং সর্পের মাংস। বুদ্ধের মতে এসব অখাদ্য। আবার বুদ্ধ পরিনির্বাণ কালে আনন্দকে দুই প্রকার পিণ্ডপাত সমান ও সমফলপ্রদ দায়ক, সমান বিপাক দায়ক বিশিষ্ট অর্থাৎ অতীব ফলপ্রদ ও মহাপুণ্যপ্রদ বলে ভাষণ করেন- ১. সুজাতার পায়সান্ন ও ২. স্বর্ণকার চুন্দের শুকর মদ্দব (মাংস)।২৪
প্রকৃত পে বৌদ্ধরা মিথ্যা ধারণা ও লৌকিকতার আশ্রয়ে আদৃত হয়ে মাংস ভণ করে না। বড়ুয়া বৌদ্ধরা বিভিন্ন মাছ মাংস, তথা মুরগী, শুকুর ও অন্যন্যা প্রাণীর মাংস অনায়সে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। আর গরু, মহিষ, ছাগলের মাংস না খাওয়ার ফতোয়া লৌকিকতা ও কুসংস্কার ছাড়া আর কিছু নয়। প্রকৃত পে বড় প্রাণী কারণে বধ না করা এবং নিরামিষযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করার প্রতি বুদ্ধ সব সময় উপদেশ দিয়েছেন। বুদ্ধ পাঁচ প্রকার বাণিজ্যকে নিষেধ করেছেন- প্রাণী, মাংস, অস্ত্র, মদ, বিষ বাণিজ্য। বৌদ্ধধর্মে হিন্দুধর্মের প্রভাব ছিল একথা সত্য। কিন্তু আজও হিন্দুদের আচার, কৃষ্টির লৌকিক প্রথাগুলো আমাদের বৌদ্ধ ধর্মীয় কৃষ্টি সভ্যতা ও পূজা-পার্বণ থেকে বৌদ্ধরা আজো মুক্ত হতে পারছে না।
আল্পলানি : বৌদ্ধরা প্রধানত কৃষিজীবি। বর্তমানে ত্রে বিশেষে ব্যবসা ও চাকরি পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। বাঙালি বৌদ্ধরা কৃষি চাষ করার পূর্বে একটি বিশেষ উৎসব বা পূজা অনুষ্ঠান করে থাকে। এই উৎসবকে বলা হয় আল্পলানি বা অম্বুবাচী। একে হালপলানী পুজাও বলা হয়।২৫ বৌদ্ধদের সামাাজিক এ লৌকিক ক্রিয়াকলাপকে অনেক ভাবে বলে থাকে। হিন্দুরা বলেন আম্বুবাচীর দিন বড়–য়া চাকমারা বলে আল্পলানি। প্রচলিত আছে যে, চাষাবাদ করার আগে আল্পলানি নামক উৎসব বা পূজা করতে হয়। যদি এ আল্পলানি না করে তাহলে জমিতে ফসল ভাল হবে না। বড়ুয়াদের যেহেতু কৃষি প্রধান পেশা সেহেতু তারা এ আল্পলানিতে প্রচণ্ড ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে পূজা ও ক্রিয়াকলাপ করে থাকে। যাতে ফসল অধিক হারে জন্মায়। প্রকৃত পক্ষে বড়ুয়া বৌদ্ধদের মধ্যে এটা লৌকিক প্রথা। তারা মিথ্যার বশবর্তী হয়ে এ পূজা করে থাকে। কারণ তাদের বিশ্বাস ঐ দিন ধরিত্রী রাজস্বল হন।
আল্পলানির দিন বিশেষ খাদ্য তৈরী করা হয়। এ খাদ্য দ্রব্য গুলো লোকজনকে বিতরণ করে থাকে। তৈরীকৃত সামগ্রীর কিছু অংশ (কাঁঠাল, আম, সুজি, ভাত ও পিটা) চাষের জমিতে গিয়ে সকলকে প্রদান করে থাকে। আর সকলে এসব খাদ্য খেতে খেতে হৈ, হৈল্লা ও আনন্দ প্রকাশ করে থাকে। প্রকৃতপে এর দ্বারা কৃষকরা দেবতাকে পূজা করে থাকে। এটা আসলে এক ধরনের কুসংস্কার।২৫
কুসংস্কারের (Superstiotion) বেড়াজালে বৌদ্ধরা আষ্টে পৃষ্টে বাঁধা। এই কুসংস্কার প্রথা আমাদের সমাজ ও ধর্ম সত্য রীতিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কবি সুইফট বলেছেন, ধর্মীয় ও সামাজিক গোঁড়ামী দারিদ্রকে আরো দারিদ্র করে তোলে। এতদ্সত্ত্বেও ধর্ম মানুষ যা ভালো মনে করেছে তাকে দিয়েছে প্রচণ্ড সমর্থন, বলবৎ করেছে অবশ্য পালনীয় বিষয়। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের জন্য যা কল্যাণকর, উপকারী ধর্ম তাকে অনুমোদন দিয়েছেন দ্বিধাহীন ভাবে। আর ধর্ম মানুষকে সন্দেহ মুক্ত করেছে সাহস যোগিয়েছে। মেলিনোতস্কির মতে, ধর্ম সমাজে সংহতির স্তম্ভ স্বরূপ। তিনি তাঁর Magic, Secince and Religon (নিউইর্য়ক, ১৯৫৪) নামক গ্রন্থে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন, কিভাবে ধর্মীয় ক্রিয়া অনুষ্ঠান মানুষকে হতাশা, ভয় ও চরম নৈতিক অধঃপতন থেকে রা করেছে।২৪ ব্যাডফিক ব্রাউন তাঁর Structure and Function in Primitive Society (লণ্ডন, ১৯৫২) নামক গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন, কিভাবে ক্রিয়া ও অনুষ্ঠান সামাজিক ও ধর্মীয় সংহতিকে রা করে, মানুষের অস্তিত্বকে ধরে রেখেছে। ধর্ম যদি ব্যক্তি চরিত্র, বিশ্বাস, বিশুদ্ধ সংহতি, সামাজিক সমঝোতা রা না করতো, তাহলে মানব সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তো। মানব সমাজের ধর্মীয় পূজা পার্বণ, সমাজ সংস্কৃতি, আদি ঐতিহ্য জীবনের সঙ্গে তা গভীর ভাবে সম্পৃক্ত। জীবনের সকল পর্যায়ে তা আজ মজ্জা প্রোথিত, জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি পরিব্যাপ্ত।
একথা সত্য যে, শত কুসংস্কার, অপসংস্কৃতি ও বিভিন্নতা সত্ত্বেও ধর্মীয় বিশ্বাস, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, পূজা, পার্বণ ও সামাজিক রীতিনীতি মানুষকে অনিশ্চয়তার হাত থেকে রা করেছে। তাই বর্তমান এ প্রোপটে এর গুরুত্ব ও অপসংস্কৃতির শেকড় যতই গভীরে হোক না কেন, সকলের ঐকান্তিক স্বত:স্ফুর্ত সচেতনার মাধ্যমে এ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। বর্তমানে মানবতা ভুলুণ্ঠিত হচ্ছে। দ্বন্দ্ব, সংঘাত, হানাহানি, হিংসায় উন্মুক্ত পৃথিবীর সমস্ত অশুভ সংস্কৃতি ও মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতা পরিহার করে মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করতে হবে। এর মাধ্যমে সৃজনশীল মুক্তবুদ্ধির প্রগতিশীল আধুনিক সমাজ, দেশ ও জাতি বিনির্মাণ করা সম্ভব।
সামাজিক ক্রিয়াকলাপ:
বাংলাদেশের বৌদ্ধদের মধ্যে প্রাচীন কাল থেকে জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ ইত্যাদিতে বহ পুরানো নিয়ম-নীতি বা লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান করার প্রথা প্রচলিত আছে। নিম্নে সে বিভিন্ন সামাজিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-
সাধভক্ষুণ : সাধভণ হচ্ছে খাওয়ার স্বাধীনতা। গর্ভবতী রমনীকে সাতমাসে বা নবম মাসের সময় উৎকৃষ্ট খাদ্য ভোজ্যের মাধ্যমে সাধ ভণ করতে দেওয়া হয়। এসময় গর্ভবতীর পঞ্চম মাসে পঞ্চামৃত পান (দুগ্ধ, চিনি, ঘৃত, দধি ও মধু) করতে হয়। এছাড়াও গর্ভবতী রমনীকে বস্ত্র প্রদান এবং গুড়াপিটা, বাশুটি পিটা রান্না করে খাওয়ানো হয়। এ সময় সে যা খাওয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে তাকে সেই খাদ্য গুলো ভণ করতে দেওয়া হয়। কিছু দিন পর তাকে আবার বার মাসের নানান ফলও খেতে দেওয়া হয়। বড়ুয়া জনগোষ্ঠির মধ্যে ইহা ‘হাদি’ নামে পরিচিত। বৌদ্ধ দৃষ্টিতে সাধভণ একটি লৌকিক আচার অনুষ্ঠান।
সন্তানের জন্ম : বড়ুয়া বৌদ্ধদের রীতি অনুসারে সন্তান প্রসব হলে মহিলারা উলুধ্বনি দিয়ে থাকে। পুত্র সন্তান হলে পাঁচবার আর কন্যা সন্তান হলে তিনবার উলুধ্বনি দেওয়া হয়। বৌদ্ধ সমাজে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে ঘরে কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে রাখা হয়। প্রসূতি এবং নবজাতককে গরম পানি দিয়ে স্নান করে পাক পবিত্র করা হয়। তারপর নবজাতকের সারা গায়ে তৈল মেখে দেওয়া হয় এবং মধু খাওয়ানো হয়। শিশু জন্মের তিনদিন, পাঁচদিন বা সাতদিন পর মাথার চুল কামানো হয়। এ অনুষ্ঠানকে বলা হয় ‘হুদ’। প্রসবের প্রায় পনের দিন পর্যন্ত প্রসূতি অশুচি থাকে। সংসারের কোন কাজে তাকে অংশ নিতে দেওয়া হয় না। নবজাতকের নাভি ছেদন না হওয়া পর্যন্ত প্রসূতিকে বিহার কিংবা পূজার ঘরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না।
নামকরণ : বৌদ্ধদের মাঝে ছেলে মেয়েদের নামকরণ ও দোলনায় তোলা একটি বিশেষ আঞ্চলিক অনুষ্ঠান। শিশু জন্মের সপ্তাহ পর দোলনায় তোলা এবং আসল নামে নামকরণ করা হয়। জন্মের পরেই আদর করে অনেকে পছন্দ মত নাম রাখে। এটি ডাক নাম। আনুষ্ঠানিকভাবে দাদা-দাদী, আত্মীয়-স্বজনরা বই, খাতা, পেন্সিল, কলম (শিা ও জ্ঞানের প্রতীক), বোধিবৃরে পাতা (বীর্য ও প্রজ্ঞার প্রতীক), লজ্জাবতী পাতা (লজ্জার প্রতীক), নিদ্রালী পাতা (অধিক নিদ্রার প্রতীক), পাথর (গাম্ভীর্যের প্রতীক), মনকাঁটা (স্মরণ শক্তির প্রতীক), একখণ্ড লৌহা (শক্তি ও সাহসের প্রতীক) ইত্যাদি বিছানার পাশে রেখে শিশুকে দোলনায় শুইয়ে দেয়। মোমবাতি জ্বালানোর মধ্য দিয়ে পছন্দের নামটিসহ শিশুর আসল নাম রাখা হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে গণক ব্রাহ্মণ বা ভিুদের দিয়ে চিকুজী কুষ্ঠি করে তদানুসারে আসল নাম ঠিক করা হয়। আজকাল বড়–য়া সমাজে বৌদ্ধ হিন্দুরীতি মিশ্রিত আধুনিক নামই রাখা হয়ে থাকে। যেমন বেনীমাধব, সমরেন্দ্র, শশাংক, সুধাংশু, সারনাথ, মেঘনাথ, রাজপতি, সুবল চন্দ্র, শান্তিবালা, সুধাসিনী, দীপক, সুজাতা, নির্মল, তৃপ্তি, দীপা ইত্যাদি উপাধি হিসেবে চট্টগ্রামে বৌদ্ধরা লিখেন বড়–য়া আর পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধরা লেখেন চাকমা, মারমা, রাখাইন, তনচঙ্গ্যা, চাক, ম্রো, খুমি, খিয়াং, নেয়াখালি ত্রিপুরা অঞ্চলের বৌদ্ধরা লেখেন সিংহ, মাঝে মাঝে পেশাভিত্তিক উপাধি কিংবা প্রাপ্ত খেতাবও লিখতে দেখা যায়। যেমন- মুৎসুদ্দি, তালুকদার, চৌধুরী, সিকদার, মহাজন, রায় বাহাদুর, নাজির ইত্যাদি।
অন্নপ্রাসন : বৌদ্ধরা গৃহে পুত্র-কন্যার আগমনকে সুখের বলে মনে করে থাকে। সেই সাথে পুত্র-কন্যার মুখে প্রথম আহার দেওয়াকে অন্নপ্রাসন বলে। অন্নপ্রাসনকে আঞ্চলিক ভাষায় ‘ভাত ছোঁয়ানী’ বলা হয়। শিশুর মুখে অন্ন দেওয়া একটি আনন্দঘন অনুষ্ঠান। কোন পূর্ণিমাকে কেন্দ্র করে পঞ্জিকা তারিখ দেখে দিন ঠিক করা হয়। ঐদিন শিশুর মস্তক মুণ্ডিত করে স্নানের পর শিশুকে নববস্ত্র পরিধান করে মাথায় টোপড় পরানো হয়। তারপর বৌদ্ধ বিহার বা বোধিবৃরে মূলে শিশুকে নিয়ে যাওয়া হয়। উপাসনা শেষ করে বৌদ্ধ বিহারের প্রধান ভিুকে দিয়ে প্রথমে শিশুর মুখে অন্ন তুলে দেওয়া হয়। সাধারণত ছেলে হলে ৬ থেকে ৮ মাস এবং মেয়ে হলে ৫ থেকে ৭ মাস বয়সে অন্নপ্রাসন করতে হয়। সেদিন থেকে শিশুকে অল্প অল্প অন্ন খেতে দেওয়া হয়। এর আগে শিশুকে মায়ের দুধ বা বিকল্প দুধ খেতে দেওয়া হয়। এ উপলে ভিুদের পিণ্ডদান কিংবা সংঘদান এবং আত্মীয় স্বজনকে খাওয়ানো হয়। এ সময় অভিভাবকগণ নতুন থালা (অন্নের প্রতীক), গামছা (দীর্ঘায়ুর প্রতীক) এবং কাপড় (লজ্জা নিবারণের প্রতীক) উপহার স্বরূপ দেওয়া হয়।২৬
বিদ্যারম্ভ : বিদ্যারম্ভ বড়ুয়া বৌদ্ধদের আর একটি সামাজিক অনুষ্ঠান। আধুনিক বৌদ্ধ সমাজে এর বিধান আছে। প্রত্যেক পিতা-মাতারা বিদ্যারম্ভ মাঙ্গলিক কর্মাদির মাধ্যমে সম্পন্ন করে থাকেন। এদিনে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে পঞ্জিকা অনুসারে শিশুর বিদ্যারম্ভ করা হয়। শিশুর বয়স যখন তিন-চার বছর তখন এ অনুষ্ঠান হয়। এটি একান্ত ঘরের অনুষ্ঠান বলে অভিভাবকের আর্থিক সংহতি এবং সদিচ্ছার উপর এ অনুষ্ঠান নির্ভর করে।
প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা : বৌদ্ধ ধর্মীয় সামাজিক অনুষ্ঠানাদির মধ্যে দীক্ষা/প্রব্রজ্যা প্রদান একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় প্রথা। পারিবারিক জীবন ত্যাগ করে বৌদ্ধরীতিতে সন্ন্যাস অবলম্বনের নাম প্রব্রজ্যা। প্রব্রজ্যা বৌদ্ধ সন্ন্যাস জীবনের প্রথম পর্যায় বা শ্রমণ হওয়া। ‘পাপকানং মলং পব্বজেতী’তি।’ অর্থাৎ নিজের পাপমল বর্জনে সংকল্পবদ্ধ হন বলেই তাঁকে প্রব্রজিত বলা হয়। পরম প্রাপ্তি নির্বাণ প্রত্যাশাই প্রব্রজ্যা গ্রহণের অন্যতম উদ্দেশ্য। শ্রমণকে দশশীল প্রতিপালন করতে হয়। ন্যূনতম সাত বছর বয়স্ক শিশুকে দীা দেওয়ার রীতি আছে। প্রব্রজ্যার জন্য প্রয়োজন আট প্রকার দ্রব্য যাকে অট্ঠ পরিক্খার বলা হয়। তাহলো- ত্রি-চীবর (উত্তরাসঙ্গ, সংঘাটি, অন্তবাস), ভিাপাত্র, জলছাকনী গামছা, ক্ষুর ও কটিবন্ধনী, সূই-সূতার পিণ্ড। প্রব্রজ্যার পূর্বে তাকে প্রথমে স্নানাদি সেরে নতুন বস্ত্র পরিধান করা হয়। তার পর মাথার উপর প্রব্রজ্যার উপকরণসহ শোভাযাত্রা সহকারে বাড়ি হতে বিহারে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রব্রজ্যা প্রার্থীকে পিতা-মাতা ও অভিভাবকের অনুমতি নিতে হয়। এভাবে নানা পুণ্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে সাড়ম্বর ভাবে সংঘদান ও অষ্টপরিষ্কার দান দিয়ে প্রব্রজ্যা/দীা দান করা হয়। আগেকার দিনে নারীদের দীক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও বর্তমানে বৌদ্ধ সমাজে নারী জাতির দীক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে নারীরা সাধুমা হয়ে আলাদা ঘরে থাকে পারে।২৭ বিনয় বিধান মতে, ৭ বছরের ছোট শিশুকে প্রব্রজ্যা প্রদান করা হয়। কিন্তু তার Psychologe text বুদ্ধি পরীক্ষা করে দেয়া হয়। পালিতে একে ‘কাকাতুয়া’ প্রব্রজ্যা বলা হয়। একজন কুলপুত্র গাহস্থ্য বা সংসার দুঃখ, চিত্তের মল বা ধিকার বা পাপ মল পক্কালনের জন্য ভব দুঃখ হতে মুক্তি লাভের আশায় সকল বিষয়ে লোভ, দ্বেষ, মোহ, ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে।
প্রব্রজ্যা প্রার্থী পালিতে বলেন, ‘সব্বদুক্খ নিস্সরণ নিব্বানং সচ্ছিকরণত্থায ইমং কাসাবং গহেত্বা পব্বাজেত্থ মং ভন্তে, অনুকম্পং উপাদায’ (তিনবার)। এর পর ধর্মীয় বিধান মতে, ভিু তাকে সদ্ধর্মে দীক্ষা প্রদান করে থাকেন।
শ্রামণ থেকে ভিু হওয়ার যে অনুষ্ঠান তাকে উপসম্পদা বলে। প্রথমে কেউ উপসম্পদা গ্রহণ করতে পারে না। আগে প্রব্রজিত হয়ে শ্রামণ্যধর্মে দীক্ষা এবং বয়স বিশ হলে উপসম্পদা নিতে পারেন। প্রবীন প্রাজ্ঞ ভিুর নিকট অষ্টপরিষ্কার নিয়ে শরণাপন্ন হয়ে উপসম্পদা গ্রহণ করেন। উদক সীমায় উপসম্পদা গ্রহণ করার রীতি প্রচলিত আছে। উপসম্পদার জন্য সংঘ তথা কমপক্ষে পাঁচজন ভিুর প্রয়োজন হয়। উপসম্পদা প্রার্থী প্রার্থনা করেন – ‘সঙ্ঘং ভন্তে উপসম্পদং যাচামি, উল্লম্পতু মং ভন্তে সংঘো অনুকম্পং উপাদায।’ তখন ভিক্ষুসংঘ কর্মবাচা পাঠ করে উপসম্পদা প্রদান করেন। ভিুকে বিনয় পাতিমোক্খ বিধান মতে, ২২৭ টি শীল প্রতিপালন করতে হয়।
কর্ণছেদন ও নাসিকা ছেদন : বাঙালি বৌদ্ধ সমাজে মেয়েদের কর্ণছেদন ও নাসিকা ছেদনকে আঞ্চলিক ভাষায় কান ফুড়ানী ও নাক ফুড়ানী অনুষ্ঠান বলে। বিবাহের আগে বৌদ্ধ কুলপুত্রকে যেমন প্রব্রজ্যা দীক্ষা নিতে হয়, তেমনি মেয়েদের বিবাহের আগে কর্ণ ও নাসিকা ছেদন করা অনিবার্য বলে মনে করেন। কারণ বিয়ের আগে মেয়েদের কান ও নাক ফুড়ানো হয় তারা যেন বিবাহের সময় স্বর্ণালংকারগুলো নাকে ও কানে পরিধান করতে পারে।
বড়ুয়া বৌদ্ধরা এ অনুষ্ঠান আড়ম্বর পূর্ণভাবে করে থাকে। এ আনন্দঘন জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান আত্মীয় স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশী সকলকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করা হয়। আর সে উপলে সাধ্যমত অতিথি আপ্যায়নের খাওয়া ও মেলা দিয়ে থাকেন। এ অনুষ্ঠান সাধারণত দুপুর বেলায় করার হয়। ইহাতে কর্ণ ছেদনের পূর্বে বোনের জামাই ও দাদা-দাদীরা সকলে মিলে মেয়ের আত্মীয় স্বজন থেকে বায়না ধরে এবং সকলে আনন্দ উল্লাস করে থাকেন। কান ফুড়ানী ও নাক ফুড়ানী অনুষ্ঠানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বা আকর্ষণীয় দিক হল শিয়ালি প্রদান অর্থাৎ কান ফুড়ানোর পর এদিন মেয়ের সকল আত্মীয় স্বজন কানের বালি, স্বর্ণ, জামা, প্যাণ্ট, স্কাট, সেলোয়ার কামিজ, টাকা, বিভিন্ন উপকরণ ইত্যাদি দিয়ে থাকেন। এগুলো শিয়লি করে লিখে রাখা হয় এবং পরবর্তীতে তার ঐ ধরনের কোন অনুষ্ঠানে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। ত্রে বিশেষে বড়ুয়া মেয়েদের কর্ণ ছেদন করলেনও নাক ফুড়ানো হয় না।
বিবাহ ও যৌতুক প্রথা : বিবাহ বা পরিণয় প্রথা একটি বৃহৎ সামাজিক অনুষ্ঠান বর্তমান প্রোপটে বিবাহ প্রথার গুরুত্ব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বৌদ্ধ মতে, বিবাহের পূর্বে বর কনেকে বিবিধ গৃহকর্ম সম্পাদন ও ভিুদের নিকট ‘মঙ্গলসূত্র’ শ্রবণ করতে হয়। তবে বর্তমানে এ অনুষ্ঠানের কোন সর্ব সম্মত বিধি বা নিয়ম করা চলে না। তথাগত বুদ্ধ বিবাহ প্রথা সম্পর্কে কোন উপদেশ প্রদান করেননি। উল্লেখ থাকে যে বৌদ্ধ আচরণে বিবাহ বা পরিণয় প্রথা সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া যায় না। তাই বুদ্ধ পরিণয় প্রথা সম্পর্কে কোন মতামত প্রদান করেননি। কিন্তু তিনি তৎকালিন পরিণয় প্রথা সম্পর্কে কোন বিরোধিতাও করেননি বলে ধারণা করা হয়। তবে বুদ্ধ শুধু বারংবার বিবাহ প্রথা সম্পর্কে অনীহা ও অনুৎসাহ প্রদান করেছেন। এছাড়াও বুদ্ধ সব সময় মানুষকে প্রব্রজ্যা ধর্ম গ্রহণ করে সংসার ত্যাগী হওয়ার জন্য উৎসাহ দান করেছেন। বুদ্ধকালীন সমাজে সংস্কার সাধন করার মত অনেক অপসংস্কৃতি বা কুপ্রথা সমাজে বিদ্যমান ছিল। বুদ্ধ সব সময় তৃষ্ণামুক্ত, অবজ্ঞাহীন সৎজীবন ও মুক্ত বিহার করার কথা বলেছেন।২৮ বুদ্ধের বিবাহ প্রথার অনীহা ল্য করে প্লেটো বলেছেন- ‘এ জগৎ বা ভব পৃথিবীতে যদি পরিণয় প্রথা না থাকতো তাহলে এ জগৎ ক্রমে নিঃস্ব, জনশূন্য হয়ে যেতো।’
বিশ্বের সকল সভ্য মানব সম্প্রদায় বিবাহ প্রথাকে স্বীকার করে নিয়েছে। বৌদ্ধধর্মের চিরাচরিত নিয়মে ও বিধান অনুসারে বিবাহ প্রথা যুক্তি সঙ্গত নয়। বিয়ে শাদী সাধারণত লৌকিক আচার অনুষ্ঠান। প্রাচীন কাল থেকে প্রতিটি মানুষের মধ্যে এ বিবাহ প্রথার লৌকিক আচার অনুষ্ঠান হিসেবে প্রচলিত ছিল। আদিম জনগোষ্ঠির উদ্ভব কালে স্ব-স্ব গোত্রের আচার অনুষ্ঠানের সমন্বয়ে দ্বিতীয় শতকের দিকে বৃত্তের চট্টগ্রামের সংস্কৃতির লৌকিক আচার অনুষ্ঠানের প্রাথমিক রূপ লাভ করে। বিংশ শতাব্দীতে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার লাভ ও চর্চার ফলে এর কিছুটা শিথিল হলেও এখানকার লোকজীবন থেকে একে বারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। ধর্মীয় ইতিহাসে দেখা যায়, বিশাখার বিবাহের সময় তাঁর পিতা ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী প্রদত্ত দশটি উপদেশ বা বর: ১. ঘরের আগুন বাইরে নিও না ২. বাইরের আগুন ঘরে এনো না ৩. যে দেয় তাকে দেবে ৪. যে দেয় না তাকেও দেবে ৫. যে দেয় বা দেয় না তাকেও দেবে ৬. সুখে বসবে ৭. সুখে আহার করবে ৮. সুখে শয়ন করবে ৯. অত্রির বা সাধু সজ্জনের সেবা ১০. গৃহাগত দেবতার পূজা করবে।
তৎকালে প্রদেয় এসব উপদেশ কল্যাণময়। তবে বৌদ্ধ দৃষ্টিকোণ থেকে এ লৌকিক বিবাহ আচার অনুষ্ঠানের পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বৌদ্ধধর্ম বিবাহ প্রথার ঘোর বিবোধি ছিল। আর বিবাহ প্রথার সাথে যে যৌতুক প্রথা প্রচলিত আছে তা মূলত বৌদ্ধধর্মের অনুসারীদের নব বিধান থেকে সৃষ্টি হয়েছে। কেননা অন্যান্য ধর্মের বিধান মতে, নারীরা পিতা-মাতা বা আত্মীয়-স্বজনের ভূ-সম্পত্তির বা টাকা পয়সার কিছু অংশের অংশীদার হয়ে থাকে। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের বিধান ও নিয়ম অনুসারে নারীরা সমঅধিকার প্রাপ্ত হলেও বিবাহ প্রথায় নারীরা যেমন অবহেলিত তেমনি পিতামাতার সম্পত্তি ভোগের অংশীদার থেকেও বঞ্চিত। এর কারণে বৌদ্ধধর্মের অনুসারী মেয়েদের বিয়ে শাদিতে প্রচুর পরিমাণে যৌতুক প্রদান করতে হয় (সমাজে স্বীকৃত নয়)। কারণ তারা বিবাহিত হওয়ার পর পিতা-মাতার কোন অর্থ সম্পত্তির অংশীদার বা দাবিদার হতে পারে না। তাই দেখা যায় যৌতুক প্রথা বৌদ্ধধর্মেরই সৃষ্ট। বৌদ্ধধর্ম মতে, এ লৌকিক আচার অনুষ্ঠানের কোন বিধি-বিধান না থাকলেও যুগ যুগ ধরে এ বিবাহ ও যৌতুক প্রাথার লৌকিক আচার অনুষ্ঠান বৌদ্ধ সমাজে প্রচলিত হয়ে আসছে।
আবাহ-বিবাহ পরিণয় পদ্ধতি : ত্রিপিটক শাস্ত্রে পুত্রের বিবাহ পরিণয় প্রথাকে আবাহ আর কন্যার বিবাহ পরিণয় প্রথাকে বিবাহ বলে। বিবাহ সামাজিক জীবনের বৃহত্তর এবং জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান। বিবাহের আগে ছেলেকে একবার প্রব্রজ্যা ধর্মে দীা নিতে হয়। সচরাচর প্রথমেই বরের পে কন্যা নির্বাচন করে। পাত্রের যোগ্যতা অনুযায়ী পাত্রী নির্র্ধারণ গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বৌদ্ধরা সমরক্তের সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ বন্ধন থেকে বিরত থাকে। স্বগোত্র এবং স্ববংশের মধ্যে বিবাহ না হওয়া প্রতিষ্ঠিত সামাজিক রীতি। তবে মামাতো বোনকে অনেকে সিদ্ধার্থ গৌতমকে অনুসরণ করে এ প্রথায় বিয়ে করে থাকে। তাছাড়া পিসী, মাসী, পিসতুত ও মাসুতত বোনের সঙ্গে বিয়ে হয় মাঝে মাঝে। উভয় প ঠিকজী বা কোষ্ঠি বিচার করে ফোটক (প্রতিবন্ধকতা) আছে কিনা পরীা করে। এছাড়াও শারীরিক, মানসিক, চারিত্রিক, ধনী দরিদ্র বিচার করা হয়। জন্ম মাসে, জোড় মাসে, বর্ষাব্রত অধিষ্ঠানের সময়, পৌষ মাসে, চৈত্র মাসে, জ্যৈষ্ঠ মাসে, কার্তিক মাসে এবং মাতা পিতার মৃত্যুর এক বছরের মধ্যে বিয়ে হয় না। বিয়ে শাদী অনুষ্ঠান মাসের শুভাশুভ ধারণা। প্রবাদে প্রচলিত আছে-
ফাগুণের বিয়ে আগুন
চৈত্রের বিয়ে হারুগা
জেঠের বিয়ে হেট
কার্তিকের বিয়ে হাতি
পউষের বিয়ে পুষ্করা।২৯
বৈশাখ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ ও মাঘ এই সাতমাসে বিয়ে শাদী অনুষ্ঠিত হলে সে বউ স্বামী ও শ্বাশুর পরিবারের পে শুভ ও মঙ্গলজনক হয়। বিবাহ সাধারণত তিন রকমের (ক) বর গিয়ে কনের বাড়িতে বিয়ে করে আসাকে চলন্ত বিয়ে। (খ) কনেকে তার নিজ বাড়ী থেকে নিয়ে এসে বরের বাড়ীতে বিবাহ করা কে বলা হয় নামন্ত বিয়ে (গ) বর বিয়ে করে অপুত্রক শ্বাশুর বাড়ীতে চলে যাওয়াকে ঘরজামাই বিয়ে বলে। অনুষ্ঠান প্রস্তুতির সাথে সাথে চলে উৎসবের ঐতিহাসিক অহলা কেসেট বাজান, বিবাহের মন মাতানো সানাই, ঢোল বাদ্য, গান বাজনা ইত্যাদি। বিয়ে সম্পর্কীয় বাঙালি বড়–য়া বৌদ্ধরা যেসকল সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ও লোককর্মগুলো অনুসরণ করে থাকে তা সংপ্তি ভাবে তোলে ধরা হলো-
১) পাত্র-পাত্রী নির্বাচন ২) বউ জোড়লী বা অলংকার চড়ানী (৩) গদ গলানো (৪) লগ্ন আনা (৫) পানসল্লা (৬) বরের তেলোয়াইদেয়া বা তেল চড়ানী (৭) বর কনের সোহাগ ধরা (৮) বউ নামানী (৯) হাইচধরা (১০) কনের শ্বশুর বাড়ী যাত্রা (১১) গৃহদেবতা পূজা (১২) সিধা দেওয়া ১৩) ঢোলবিদ্যা ও অনুসরণসহ বিহারে গিয়ে বুদ্ধপূজা, প্রদীপ পূজা ও ত্রিরতœ বন্দনা ১৪) মঙ্গল সূত্র পাঠ (১৫) বিয়ে অনুষ্ঠান (১৬) বিয়ের মন্ত্র (১৭) সহমেলা (১৮) নব দম্পতি গোসল (১৯) নব দম্পতিকে গুরুজনের আশীর্বাদ গ্রহণ (২০) বেয়াই ভাতা (২১) মাটি হোঁড়ানী (২২) ভিুদের পিণ্ডদান (২৩) ছোয়াইং তোলা (২৪) বৌভাত খাওয়া (২৫) মাড়ি হোরানী (২৬) ন দিন্যা যাওয়া (২৭) ফিরাইন্যা ভাত (২৮) বারমাসে তের ফল বেয়ার (২৯) বেয়াই ভাতা (৩০) মঙ্গলঘট (৩১) কলসির জল ভরান (৩২) বরকলা (৩৩) বরকনের গায়ে হলুদ স্নান (৩৪) ঘাটা ঘরা (৩৫) পানমিটা (৩৬) বরসজ্জা, কনে সজ্জা (৩৭) ডুলিধরা (৩৮) নতুন বধুকে ভাত তরকারী ও ধান দেখানো (৩৯) বর বধুর ফুল শয্যা (৪০) নতুন জামাইর সালামী (৪১) বউ দেখা (৪২) রং ও ফুট খেলা (৪৩) ঢোলবাদ্য, মাইক, সানাই বাজনা (৪৪) বর কনের পিতা মাতার অনুমতি (৪৫) স্ত্রী পুরুষ স্বগ্রামী ও ভিন্ন গ্রামীদেরকের সান্ধ্য ভোজ (৪৬) যৌতুক প্রথা ৩০ (৪৭) বিবাহ আসরে মন্ত্রপাঠ ইত্যাদি ইত্যাদি।
এবার বিবাহের দুটি ঐতিহাসিক বিশেষ উপকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হলো-
মঙ্গলঘট : বাংলাদেশে বৌদ্ধ সমাজে মঙ্গলঘাট প্রথা প্রচলিত আছে। বাড়ির প্রবেশ পথে শুভ লণের প্রতীক মঙ্গলঘট স্থাপন করা হয়। বাড়ীর প্রবেশ পথে দু পাশে দুটি কলাগাছ পুতে তার উপর বা গোড়ায় জলপূর্ণ কলসী স্থাপন করত মুখে দুটি আম্রপল্লব, অশ্বথ, বাঁশ মুরাজী, বৈইল, মধুবাঁশের পাতা এবং কলা গাছের ডিক দিলে মঙ্গলঘট হয়। কোন কোন েেত্র দুটি ডাবও দেওয়া হয়। সপ্তদশ শতকের কবি মোহাম্মদ রফিক উদ্দীন বিরচিত জবল মুল্লক মনোরস কাব্যে তার উল্লেখ পাওয়া যায়-
‘কুম্ভ দুই জল ভরি পন্থ দুইপাশে
আম্রজল দিয়া তাতে রাখিছে হরিষে।’
বরণকুলা : বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিয়ে বা শুভ কাজে মাঙ্গলিক প্রতীক রূপে বরণ কুলা বা ডালা দেওয়া বহুল প্রচলিত আছে।৩১ এ প্রথা হিন্দু-মুসলিম সমাজেও প্রচলিত আছে। বৌদ্ধদের বরণ কুলার উপাদানের তালিকা নিন্মে প্রদত্ত হলো-
ক্র.ম উপকরণ বা দ্রব্য নাম পরিমাণ উপাদানের প্রতীক ধারণা
১. নতুন কুলা: ১ টি কল্যাণ ও শান্তির প্রতীক।
২. সাইল ধান:৫ পোয়া খাদ্য মানুষের জীবন ধারণ ও ধন সম্পদ লাভের প্রতীক।
৩. দূর্বাঘাস:১ গুচ্ছ বংশধারা বৃদ্ধির প্রতীক।
৪. কাঁচা কলা : ৫ টি সবুজ ফল, সুস্বাস্থ্য ও নিরাময় জীবনধারার প্রতীক।
৫. কাঁচা হলুদ: ২/৩ টুকরা,সৌন্দর্যের প্রতীক।
৬. শিলা: (ছোট পাথর) ১ টুকরা,শৌর্য-বীর্যের প্রতীক।
৭. ঘিলা:১ টি দৃঢ়তা ও গাম্ভীর্যের প্রতীক।
৮. সরিয়া তেলের মাটি সেজ দীপ: ১ টি আলো অন্ধকার দূরীভূত করে। জ্ঞানের বা আশার প্রতীক।
৯. পরিপূর্ণ মাটির কত্তি: ১ টি পানির অপর নাম জীবন।
১০. অশ্বথ পাতা:১ টি,সবুজ পাতা মানুষের জীবনের চির তারুণ্য ও দীর্ঘায়ুর প্রতীক।
১১. আম্রপল্লব:১ গুচ্ছ
১২. বাঁশ পাতা:১ গুচ্ছ
১৩. মুরাজী পাতা:১ থোকা
১৪. বৈইল পাতা:১ থোকা
১৫. কলা গাছের কচি ডিক:১ টি
সমাজ প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি বৌদ্ধদের বিবাহ পদ্ধতিরও অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। সমাজে ছেলে মেয়েরা আধুনিক শিায় শিতি হচ্ছে। বৌদ্ধদের মধ্যে বিবাহে যৌতুক প্রথা প্রচলিত থাকলেও তবে সামাজিক দায়বদ্ধতা নেই। তবে বর্তমান বৌদ্ধ সমাজে ছেলে মেয়েদের ধর্মান্তর বিষয়টি অতীব প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়ে। স্বধর্মে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিসর্জন দিয়ে পরধর্ম সংস্কৃতি গ্রহণ করছে। এ অশুভ প্রভাব ও সংস্কৃতিকে রোধ করতে হবে। বাঙালি বড়ুয়া বৌদ্ধ সমাজে বিধবা-বিবাহ, বিবাহ বন্ধনছিন্ন, সধবার পুনর্বিবাহ এবং স্থল বিশেষে বিবাহ বিচ্ছেদ প্রচলিত আছে। পুনর্বিবাহ ইচ্ছুক বিধবাকে প্রথমত: একটি কলাগাছের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার পর যথারীতি বরের হাতে সম্প্রদান করা হয়। এ প্রথা অনেক জাতিতেই আছে।
পরিত্রাণ দেশনা : বাঙালি বৌদ্ধরা পরিত্রাণ সূত্রপাঠ একটি পবিত্র অনুষ্ঠান বলে সম্পাদন করে থাকে। থেরবাদী বৌদ্ধদের কাছে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় কার্য। বৌদ্ধরা রতন সূত্র, মৈত্রী সূত্র, মঙ্গল সূত্র, করণীয় মৈত্রী সূত্র, পরাভব সূত্র, বোধ্যঙ্গ সূত্র, আটানটিয় পরিত্ত, মোর পরিত্ত, খন্ধ পরিত্ত প্রভৃতি সূত্রপাঠ করেন। এ পরিত্ত সূত্র সম্পর্কে ড. বেণীমাধব বড়ুয়া বলেন, ‘যখন কালক্রমে বৌদ্ধ গৃহস্থ সমাজ গঠিত হয় সেই সময় হতে প্রচলিত হিন্দু বা আর্য গুহ্যমন্ত্রের অনুকরণে পালি ও মিশ্রিত ভাষায় বৌদ্ধ পরিত্রাণ সূত্রের রচনা আরম্ভ হয়। বৌদ্ধ সাহিত্যে পরিত্রাণ সূত্রের উদ্ভব ও লৌকিক বৌদ্ধধর্মের অঙ্গ। এ সূত্রের দুটি দিক আছে- লৌকিক বা জাগতিক এবং লোকোত্তর বা পারমার্থিক। লৌকিক হলেও কালে কালে এ সূত্র পাঠের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ সাধিত হয় বলে এ ব্যাপক পরিচিতি লোকমুখে আছে। পালি পরিত্ত শব্দের অর্থ পরিত্রাণ, সংরণ বা নিরাপত্তা। বৌদ্ধ ভিুরা পরিত্ত সূত্রপাঠ করে থাকে।
শব সৎকার ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া : জন্মিলে মরিতে হবে। মৃত্যু ধ্রুব সত্য। মৃত্যু সকলকে আলিঙ্গন করতে হয়। বৌদ্ধদের সামাজিক কর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ চিরাচরিত প্রথা হলো শব সৎকার ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। সমাজে কোন মানুষের মৃত্যু হলে শবদেহ হলুদ ও সাবান দিয়ে উত্তম রূপে ম্লান করে নেওয়া হয়। তার পর নববস্ত্র পরিধান করে সুগন্ধ, পুষ্প ও গন্ধ দ্রব্যাদি দিয়ে শবকে শুচি পবিত্র করে উন্মুক্ত খাটে কিংবা উন্নত শয্যায় সজ্জিত করা হয়।
শবদেহ শ্মশানে নেওয়ার সময় ভিক্ষুসংঘের নিকট সকরে বসে ত্রিশরণ ও পঞ্চশীলাদি গ্রহণ করে অনিত্যতা বিষয়ক পালি সূত্র শ্রবণ করেন। মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ভিক্ষু সংঘ বলেন, ‘ইমং মতকাবত্তং ভিক্খুসঙ্ঘস্স দেথা।’ এ মন্ত্র তিনবার পাঠ করে সংঘদান করা হয়। ভিক্ষুগণ নিন্মোক্ত অনিত্য গাথা দেশনা করে থাকেন- ‘অনিচ্চা বত সংখারা উপ্পদাবযধম্মিনো, উপ্পজিত্বা নিরুজ্ঝন্তি তেসং বুপসমো সুখো। সব্বে সত্তা মরিন্তী চ মরিংসু চ মরিস্সরে, তাতে ওযহাং মরিস্সামি নত্থি মে সংসযো।’৩২ মৃতদেহকে বাঁশ বা কাঠ দিয়ে আলং বা শবাধার দিয়ে কীর্তন মাইক বাজনা, বাজি পোড়ান এবং আনন্দ উল্লাস করে শ্মশান খোলায় নিয়ে যাওয়া হয়। বৌদ্ধরা বয়স্ক ব্যক্তি নারীর শবকে দাহ (আগুনে পুড়ানো) করা এবং শিশুদের কবর দিয়ে থাকে। দাহ করার সময় চিতাতে সাতবার প্রদণি করে সাতবার অগ্নি সংযোগ করার পর অন্যান্যরা তাতে অংশ নেয়। বৌদ্ধদের শ্মশানে (দ্বিতীয়) নারীরা যেতে পারে না। মৃত ব্যক্তির জন্য শোক বা কান্না করার রীতি বৌদ্ধ বিধানে নেই। অন্ত্যেষ্টির সপ্তাহের দিন শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হয়। বৌদ্ধরা পুদ্গলিক দান কিংবা সংঘদান কিংবা অষ্টপরিষ্কার দান করে থাকে। ভিু-শ্রামনকে দান দিয়ে যথা সাধ্য লোকজনকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হয়। ঐ দিন হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক দিন সূর্যাস্তের পর ভিক্ষু বা ভিক্ষুসংঘ মৃতের বাড়িতে এসে মঙ্গলসূত্র পাঠ করেন। এই অনুষ্ঠানের নাম ‘ফারিক শ্রবণ’ বাড়ীর চারিদিকে ফারিক সূতা দেওয়া হয়।৩৩
সাপ্তাহিক শ্রাদ্ধের পর হতে প্রথম বছর প্রতিমাসেই ভিু বা সংঘকে খাদ্য ভোজ্য ও দান দণিাসহ অনুরূপ দান দেওয়া হয়। সাধারণত অশুভ তিথি নত্রের দিনে পরলোক গত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ষম্মাসিক ও বার্ষিক শ্রাদ্ধার ছোয়াই দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে।
পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের পূজা পার্বণ ও লোকবিশ্বাস এবং লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান
প্রাচীন বঙ্গে বসবাসকারী পাহাড়ী উপজাতিদের মধ্যে ধর্ম পূজার বিধান আছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অভিমত, ধর্মপূজা বৌদ্ধধর্মের শেষ পরিণতি। অনার্য জাতি বিশেষের মধ্যে প্রচলিত ধর্মপূজার প্রাচীন অনুষ্ঠান হতে ধর্মপূজার উদ্ভব হয়েছে। কারো কারো মতে উন্নত আর্য সংস্কৃতি হতে এর উৎপত্তি। এই অনুষ্ঠানকে চাকমা ভাষায় ধর্মকাম বলে। এর অন্য নাম সিদ্ধিপূজা, জাদি পূজা। উপজাতি সম্প্রদায়ের আনুষ্ঠানিক সকল পূজার মধ্যে এটি অন্যতম পূজা। মহাসমারোহে এ পূজা সম্পন্ন করেন। ইহার অনুষ্ঠান ঐহিত্য ও পারত্রিক মঙ্গলের কারন বলে লোকের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। অনেকে বিপদে পতিত হলে ইহা মানত করত। বর্তমানে আদিবাসী সমাজে আধুনিক শিার বিস্তারে ধর্মপূজার বিশ্বাস শিথিল হয়েছে। শ্রদ্ধাবান গৃহী সমস্ত গৃহদ্বার পরিষ্কার করে সস্ত্রীক স্রাতশুচি হয়ে পূর্বাহ্নে আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করেন এবং বৌদ্ধ ভিুগণকে আহবান করেন। বুদ্ধমূর্তির সামনে পূজা অর্পণ করে, বৈকালে ধুপ, দীপ, পুষ্প প্রভৃতি দ্বারা ঘন্টাধ্বনি সহকারে বুদ্ধের বন্দনা/অর্চনা করেন। এ সময় বিকৃত পালি ভাষার লিখিত চাকমা বৌদ্ধ শাস্ত্র ‘সাহস পুলুতারা’ এবং ‘মালেমতারা’ পাঠ করা হয়। (মৎ প্রণীত ‘চাকমা জাতির ইতিহাস’ (পৃ-৫৪) এবং সতীশ চন্দ্র ঘোষ প্রণীত ‘চাকমা জাতি’ (পৃ. ২০০)। প্রাচীন কুসংস্কার থাকলে ধর্মকাম, ধর্মঠাকুরের পূজা নয়, এতে বুদ্ধপূজা, দশ পারমিতা প্রার্থনা, ধর্মপদের বাণী এবং সাইত্রিশ প্রকার পায়ি ধর্মলোচনার প্রতীক।”৩৪
বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের নানামাত্রিক ভৌগোলিক, নৈসর্গিক ও নৃতাত্ত্বিক স্বজাত বৈশিষ্ট্যগুলো অন্যতম হলো এ অঞ্চলের ভাষাগত বৈচিত্র্য। পার্বত্য চট্টগ্রামেও বেসরকারি পর্যায়ে নানা ভাষা কেন্দ্রিক উদ্যোগ আয়োজন চলছে। বান্দরবানের উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনসটিটিউট সেখানকার বৈচিত্র্যমণ্ডিত ভাষা ঐতিহ্যের অধিকারী ক্ষুদ্র জাতিগুলো মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন প্রকাশ করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসি জনগোষ্ঠিগুলোর বর্ণমালাগত সমস্যা এখন খুব একটা নেই। প্রায় সব’কটি জনগোষ্ঠির হরফ বা বর্ণমালা সম্প্রতি কম্পিউটারের আওতায় এসেছে। যেমন: চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যাদের Aujhaapaat, মারমা ও চাকদের Myanmar বম, খুমি ও লুসাইদের Roman ম্রোদের Mruchow,, ত্রিপুরাদের Bijoy-sutonny প্রভৃতি ফ্রন্টে মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজও ইদানিং এগিয়ে চলেছে। এখন সেই লিপিগুলোর ব্যাপকচর্চা ও উন্নয়ন দরকার।
চীনা তিব্বতি (Sino –Tibetan) ভাষা গোষ্ঠিকে কেউ কেউ ভোট চীনীয় গোষ্ঠি বলেন। চাকমারা মঙ্গোলীয় গোষ্ঠির লোক হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য মঙ্গোলীয় গোষ্ঠিভূক্ত উপজাতিদের ভাষার মত তাদের ভাষা টিবটো বার্মান (Tibeto-Burman) বা সিনে টিবেটান (Sono-Tibetan) নয়। চাকমা ভাষা ইন্দো ইউরোপীয়ান ভাষাগোষ্ঠির অন্তর্গত একটি ভাষা। ইন্দো (ইউরোপীয়) এবং এরিয়ান (ভারতীয় ও ইরানীয় ভাষার ভিত্তিতে); এটি বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষার নিকটবর্তী একটি ভাষা।৩৫ চাকমা হরফে লিখিত পাণ্ডুলিপি গুলোর মধ্যে, তাহলিক শাস্ত্র, শাঙ্চে ফুলু তারা, আঘরতারা, রাধামন, বৌদ্ধ রঞ্জিকা, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।
১৮৫৬ সালের পূর্বে চাকমা এবং বড়–য়া সম্প্রদায় তান্ত্রিক মহাযানী বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী ছিল। উল্লেখ্য মহাযানী তান্ত্রিক বৌদ্ধরা যেমন ভগবান বুদ্ধকে আরাধনা করতেন, তেমনি তারা হিন্দুদের দেব দেবীকেও পূজা করত। সেজন্য তখন চাকমা এবং বড়ুয়ারা হিন্দুদের অনেক দেব দেবী, যেমন : স্বরস্বতী, লক্ষ্মী, কালী দেবীর পূজা করত। ১৮৫৬ সালে আরাকান হতে থেরবাদী বৌদ্ধ সারমেধ মহাথেরো চট্টগ্রামে আসেন এবং রাঙ্গুনিয়া রাজানগরে রাজ দরবারে আসেন। কালিন্দী রাণি তাঁর ধর্মোপদেশ শ্রবণ করে অভিভূত হন এবং থেরবাদী মতবাদে দীতি হন। এরপর রাণির প্রজা অনেক বড়–য়া এবং চাকমা থেরবাদী মতবাদে দীতি হন। তখন মহাযানী ভিুদের বলা হত রুলি বা রাউলি এবং টাউর বা ঠাকুর। তারা সংসারী ছিলেন। ১৮৬৪ সাল ৭ জন মহাযানী রউলী সারমেধ মহাথেরের নিকট সর্বপ্রথম থেরবাদ সম্মত উপস্পদা গ্রহণ করেন। কিভাবে চট্টগ্রামে থেরবাদ মতবাদ প্রচার শুরু হয় এবং ক্রমে ক্রমে বিস্তার লাভ করে। এখন চাকমা বড়–য়া এবং সারা বাংলাদেশে বৌদ্ধ সমাজ থেরবাদ মতবাদে বিশ্বাসী। তবে এখনও নাকি পার্বত্য চট্টগ্রামের অত্যন্ত প্রত্যন্ত অঞ্চলে মহাযানী বা রুলি ভিু দেখা যায়। কালিন্দী রানী তাঁর রাজধানী রাজানগরে (বর্তমান রাঙ্গুনীয়া থানার কিছু দূরে) একটি বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা করে তার নাম রাখেন শাক্যমুনি বিহার। তিনি বার্মা থেকে মহামুনি নামের একটি বুদ্ধমূর্তি এনে মন্দিরে স্থাপন করেন। একই ভাবে মং চীফ বর্তমান রাউজান থানার একটি বৃহৎ এবং সমৃদ্ধ প্রাচীন বড়ুয়া গ্রাম পাহাড়তলীতে একটি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করান এবং সেই বিহারে বার্মা থেকে এনে মহামুনি নামের বুদ্ধমূর্তি স্থাপন করেন। এখন গ্রামটির নামই পরিবর্তিত হয়ে মহামুনী পাহাড়তলী নামে পরিচিতি লাভ করে।৩৬
ব্রিটিশ আমলে উভয় বিহার প্রাঙ্গণে চৈত্র সংক্রান্তি অর্থাৎ চাকমাদের বিজু/বিঝু উৎসবের সময় একমাস ব্যাপী বৌদ্ধ মেলা বসত তবে উভয় স্থানে প্রথম ৩ দিন মেলাটি কেবল মাত্র উপজাতি বৌদ্ধদের জন্য নির্ধারিত ছিল। মেলায় আইন শৃঙ্খলা রা করত পার্বত্য চট্টগ্রামের পুলিশ। ৩ দিন পরে পার্বত্য চট্টগ্রামের পুলিশ চলে গেলে মেলা সবার জন্য উন্মক্ত থাকত। তখন চট্টগ্রাম জেলার পুলিশ আইন শৃঙ্খলার দায়িত্বে নিয়োজিত পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ উপজাতি নারী পুুরুষ যুবক যুবতী অংশগ্রহণ করতেন। পাকিস্তান হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম পুলিশ বাহিনীকে অবলুপ্ত করে দেয়া হয় এবং মেলায় আইনশৃঙ্খলা রায় দায়িত্ব দেয় চট্টগ্রাম জেলার পুলিশ বাহিনীকে। এরপর পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি বৌদ্ধরা মেলায় আগের মত নিরাপদ বোধ করত না। ক্রমে ক্রমে আইন শৃঙ্খলাও শিথিল হতে থাকে। উপজাতিরা বিশেষ করে মেয়েরা নানাভাবে হয়রানি হতে থাকে এবং মেলায় বাঙালি-উপজাতির মধ্যে দাঙ্গা বিবাদ হয় এবং শেষ পর্যন্ত ষাটের দশকে বন্ধ হয়ে যায়।
ব্রিটিশ আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে সব স্থানে বড় বড় বৌদ্ধ বিহার ছিল, সে সব স্থানে মাঘী পূর্ণিমা, ফাল্গুনী পূর্ণিমা, বৈশাখী পূর্ণিমা এবং চৈত্র সংক্রান্তি অর্থাৎ বিজুর সময় কমপে ৩ দিন হতে একমাস ব্যাপী বৌদ্ধ মেলা বসত। তখন ধর্মকর্ম করতে, যাত্রা অনুষ্ঠান দেখতে হাজার হাজার মানুষ মেলায় যেত। চট্টগ্রাম হতে বহু ব্যবসায়ী পণ্য সামগ্রী নিয়ে মেলায় দোকান খুলত। ১৯৭২ সাল ফাল্গুনি পূর্ণিমার সময় খাগড়াছড়ি বাজারে প্রায় শত বছরের প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরে শেষ বার বৌদ্ধ মেলার আয়োজন করা হয়। ঐ এক বছরের চৈত্র সংক্রান্তি উপলে রামগড় মহামুনি বৌদ্ধ বিহারে শেষ বার মেলার আয়োজন করা হয়। ষাটের দশকের প্রথম দিকে কর্ণফুলী প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শেষ হলে কাপ্তাই হ্রদে কয়েকটি বৌদ্ধ বিহার ডুবে যায়। তখন ঐ সব বিহারে মেলা বন্ধ হয়ে যায়।
আগেই বলা হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামে ৩ জন সার্কেল চীফ বা রাজা আছেন। তিন রাজাই তাদের জুম খাজনা আদায় উপলে প্রতিবছর আগস্টের পৌষ মাসে পূর্ণিমার সময় তাদের রাজবাড়ী প্রাঙ্গণে পুণ্যাহর আয়োজন করতেন। তখন প্রত্যেক সার্কেলের হেডম্যানগণ তাদের আদায়কৃত জুমের খাজনা একটি বাৎসরিক অনুষ্ঠানে রাজার কাছে জমা দিতেন। সেই অনুষ্ঠানকেই পুন্যাহ বলা হয়। সেই উপলে নাচ, গান, যাত্রা, ঘোড়দৌড় এবং অন্যান্য বিনোদনের আয়োজন করা হত। ৩ দিন বা সপ্তাহ খানেকের জন্য মেলা বসত। সেই উপলে চট্টগ্রাম হতে অনেক ব্যবসায়ী দোকানদার তাদের বিভিন্ন মালামাল নিয়ে ছোট ছোট অস্থায়ী দোকান খুলে বসত। পুন্যাহ শেষে মেলা হতে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় মালামাল ক্রয় করে বাড়ীতে চলে যেতেন। বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলায় এখনও কম বেশি জুম চাষ রয়েছে। তাই মাঝে মধ্যে অনিয়মিত হলেও ঐতিহ্যবাহী রাজাপুণ্যাহ অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। বৌদ্ধ মেলা বা রাজাপুন্যাহ না থাকলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধরা এখন চীবর দান অনুষ্ঠান করে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বৌদ্ধ ভিুদের চীবর দানানুষ্ঠান করা হয়। সেটা সাধারণ ভাবে কঠিন চীবর দান হিসাবে পরিচিত। প্রত্যেক বৌদ্ধ বিহারে যেখানে ভিক্ষুরা বর্ষাবাস করেন, কেবল সেই মন্দিরে চীবর দান অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।
ইতিহাসে দেখা যায়, এয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত বৌদ্ধ ধর্মীবলম্বীগণ নামে মাত্র বৌদ্ধ ছিলেন। ধর্মীয় কুসংস্কার, নানা মিথ্যাদৃষ্টি, লৌকিক ক্রিয়াকর্ম, প্রকৃতি পূজা, লোকবিশ্বাস এবং অবৌদ্ধোচিত ধর্মীয় কার্যক্রম ছিল অত্যন্ত প্রবল, ভিুদের মত মুণ্ডিত মস্তক পুরোহিত নামে এক শ্রেণির ধর্মীয় গুরু ছিলেন তারা সংসার জীবন যাপন, চাষাবাদ করতেন আবার ধর্মীয় কার্যাদিও পরিচালনা করতেন। কেউ কেউ একে লুরি বা লাউরী বলতেন। এরা ধর্ম বিনয় নীতিতে ছিলেন অজ্ঞ। রাউলীরা ধর্ম বিনয় প্রশিণ ও শিার অভাবে পার্বত্য বৌদ্ধ সমাজে নেমে এসেছে অবিদ্যা অন্ধকার। তারা ধর্মীয় কাজে ‘আগরতারা’ নামক গ্রন্থ থেকে তন্ত্র-মন্ত্র পাঠ করতেন।
অধ্যাপক দিলীপ কুমার বড়ুয়া লিখেছেন, মিথ্যাদৃষ্টিতে আচ্ছন্ন হয়ে আদিবাসীরা বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা অচর্না, থানমান, দানপাং পূজা, ধুবলাপূজা, গাংপূজা, গ্রাম রাপূজা, বৃপূজা, কালীপূজা, লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতী পূজা, দুর্গা-শিবপূজা, হোইয়া পূজা এমন কি প্রকৃতির পূজাও করতো। আর কখনো কখনো মগধেশ্বরী ও চট্টেশ্বরীর পূজা ছিল তাদের নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম। এসব পূজা পার্বণে ভুত-দেবতা সন্তোষ সাধনে পশুবলির প্রচলনও ছিল। রাউলীদের পাশাপাশি ওঝা-বৈদ্যের প্রভাবও পরিলতি হয়। আদিবাসী উপজাতিদের চিকিৎসা শাস্ত্র লৌকিক পন্থা হলেও বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা ও লোকাচারে বহুল প্রচলিত আছে।৩৭
পার্বত্য চট্টগ্রাম এমনকি বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার প্রসার, পুনরুত্থান, সংরণ ও সংস্কারে চাকমা রাজবংশের আবদান অপরিসীম। এতে বিশেষ করে চাকমা রাজা ধরমবক্স খাঁর প্রধানা মহিষী বিদে্যুৎসাহী, পুণ্যশীলা মহিয়সী কালিন্দীরাণীর (১৮৪৪-৭৩) নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। বাংলায় বৌদ্ধধর্ম পুনর্জাগরণে মহান সাংঘিক ও প্রথম সংঘরাজ চকরিয়া হারবাং এর সারমেধ মহাস্থবির ও বৌদ্ধ সমিতির প্রতিষ্ঠা সভাপতি গুণমেজো মহাস্থবিরের সাথে কালিন্দী রাণির সাক্ষাৎ হয়। তখন সারমেধ মহাস্থবিরের কাছে বুদ্ধের জীবন ও দর্শনের-উপর তাৎপর্যপূর্ণ দেশনা শুনে উদ্বুদ্ধ হন। তখন তিনি তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম থেকে পরিবর্তত হয়ে থেরবাদ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৮৫৭ সালে রাজ পুন্যাহ উপলে সারমেধ মহাথেরকে স্মারক ও সম্মাননা প্রদান করেন।৩৮ সদ্ধর্ম হিতৈষীণী রাণি কালিন্দী ১৮৬৬ সালে রাজধানী রাজানগরে শাক্যমুনি বৌদ্ধ বিহার, ১৮৭০ সালে ভিক্ষুসীমা (চিং বা গেং), ১৮৫৭ সালে বুদ্ধের জীবনী সমন্বিত ফুলচন্দ্র বড়ুয়ার ‘বৌদ্ধ রঞ্জিকা’ পুস্তক প্রকাশ করে প্রচার করেন।
পরবর্তীতে চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়ের আহবানে রেঙ্গুন হতে অগ্রবংশ মহাথের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে পার্বত্য চট্টগ্রামে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম থেকে প্রকৃত ধর্ম বিনয় শিাদর্শ প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথের পার্বত্যবাসীকে ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রব্রজ্যা প্রদান করেন আদিবাসী যুবকদের। প্রতিষ্ঠা করেন পার্বত্য বৌদ্ধ ভিু সমিতি ও গ্রামে গ্রামে বৌদ্ধ বিহার, প্রতিটি বৌদ্ধ বিহারে ভিুসংঘের মাধ্যমে প্রচলন করেন ত্রিরত্ন বন্দনা, শীলগ্রহণ, বুদ্ধপূজা, সংঘপূজা, সীবলীপূজা, সংঘদান, অষ্টপরিস্কার দান, চীবর দান ইত্যাদি। এছাড়াও বুদ্ধপূর্ণিমা, আষাঢ়ী পূর্ণিমা, মধূপূর্ণিমা, প্রবারণা পূর্ণিমায় পঞ্চশীল ও অষ্টশীল ব্রতপালন ইত্যাদি। এভাবে পার্বত্যবাসী বৌদ্ধদের মধ্যে ধর্মের জাগরণ এবং সমাজ সংস্কার সূচিত হয়েছিল।
নবকুমার তনচঙ্গ্যা উল্লেখ করেছেন, ‘সে সময় চাকমা ও তনচঙ্গ্যা সম্প্রদায়ের কোন ভিু নাই বললেও চলে। মারমা ও বড়ুয়া সম্প্রদায়ের ভিুরা পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহারে ধর্মীয় গুরু হিসেবে অবস্থান করতেন। …. পর্যায় ক্রমে মারমা, চাকমা ও তনচঙ্গ্যা সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে শ্রামণ্য ও ভিুধর্মে দীতি হয়ে ধর্মবাণী প্রচারে ভূমিকা রাখেন।৩৯
বর্তমান সময়ে পার্বত্য বৌদ্ধদের শিক্ষা-দীক্ষা ও অগ্রগতিতে শ্রীমৎ মোঙ্কর মহাস্থবির, শ্রীমৎ আর্যনন্দ মহাস্থবির, শ্রীমৎ শান্তজ্যোতি মহাস্থবির, শ্রীমৎ ধর্মপ্রিয় মহাস্থবির, রাজগুরু অগ্রবংশ মহাস্থবির, জ্ঞানশ্রী মহাস্থবির, আর্যশ্রাবক সাধনানন্দ মহাথের, সুমনালঙ্কার মহাস্থবির, প্রজ্ঞানন্দ মহাথের, উপঞ্ঞা জোত থের, গিরিমানন্দ ভিক্ষু, স্মৃতিমিত্র থের, শীলানন্দ থের প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫৭ সালে পালি ভাষা-সাহিত্য ও ধর্মীয় শিার জন্য চাকমা রাজ বিহারে পালি টোল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। পার্বত্যবাসী বৌদ্ধদের মধ্যে ধর্মীয় কুসংস্কার ও অজ্ঞতা দূর করার জন্য পাহাড়ের নির্জন অরণ্যে বহু বিহার, চৈত্য, ধ্যানকুটির, ধর্মীয় পুস্তক, ত্রিপিটক গ্রন্থ প্রকাশ, পালি কলেজ ও মেডিকেল প্রতিষ্ঠা করেন।
ধর্মবিশ্বাস : চাকমারা প্রধানত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তবে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে কিছু সংখ্যক চাকমা খৃষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত হন। জানা যায় যে, অনেক দরিদ্র চাকমা রোববার দিন পাদ্রিদের কাছ হতে বিবিধ দ্রব্যাদি পাবার জন্য চার্চে সমবেত হত। আবার বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে রাজনৈতিক সহিংসহতায় কেহ কেহ বাধ্য হয়ে ইসলাম ধর্মে দীতি হন। তবে উভয়ের সংখ্যা খুবই নগণ্য। অতীতে চাকমাদের বৌদ্ধধর্ম চেতনাবোধ লুরিরা রা করেছিলেন। অতীতে চাকমারা বৌদ্ধধর্মের অনুসারী হলেও তাদের মধ্যে হিন্দু ধর্মের প্রভাব ল্যণীয়। চাকমাদের বিভিন্ন রাজা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। স্বয়ং রাণী কালিন্দিও প্রথম দিকে হিন্দু ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন বলে জানা যায়। ফলে রাজার ধর্মই চাকমা জাতির ধর্ম বলে বিবেচিত হয়ে এসেছে।
ব্রহ্মদেশে অবস্থানকালে চাকমারা বাংলায় সংস্পর্শে এসে পুরোপুরি বৌদ্ধধর্ম অনুসরণ করতো না বলে জানা যায়। পার্বত্য আদিবাসীরা বাহ্যিক যে আচার-অনুষ্ঠানগুলি পালন করতেন আসলে সেগুলো তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম প্রভাবে। চাকমা রাণি কালিন্দি আরাকান হতে সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবির ও চকরিয়া হারবাং এর গুণমেজো মহাস্থবিরসহ প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ভিুগণকে আমন্ত্রণ করে রাজধানী রাজানগরে মহামুনি বৌদ্ধ বিহার স্থাপন করেন। তিনি সে সময়ে থাধুথং নামক বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ পঞ্জিকা নামে অনুবাদ করে প্রচারের ব্যবস্থা করেন। অন্যদিকে বড়–য়া বৌদ্ধগণও চাকমাদের বৌদ্ধধর্ম লালনে উৎসাহ যুগিয়ে চলেন। পাকিস্তান আমলে ইসলাম ধর্মের আগ্রাসন বেড়ে গেলে চাকমা সমাজ প্রতিটি গ্রামে বৌদ্ধ বিহার নির্মাণে উদ্যোগী হয়। কিন্তু প্রয়োজনীয় নীতিবান ভিু তখন খুঁজে পাওয়া মুশকিল হয়ে পড়ে। মারমা ও বড়–য়া ভিুরা এসব বিহার বা ক্যাংএ বিহারাধ্য রূপে বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসার ঘটান চাকমা রাজ পরিবারের এেেত্র বিশেষ অবদান রয়েছে। চাকমা রাজা নিজেই রাজ বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। রাঙ্গামাটিতে গড়ে উঠে রাজবন বিহার। চাকমা রাজা ভূমি দান করে রাজবাড়ির উত্তর পার্শ্বের সমতল পাহাড়ে এই বিহার স্থাপন করেন। এই রাজ বন বিহারের অধ্য হলেন বনভন্তে। মুখ্যত চাকমাদের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণ ঘটে বনভন্তের (শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাথেরো) মাধ্যমে। বনভন্তের গৃহস্থ জীবনের নাম ছিল রথীন্দ্র। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম সহ গোটা বিশ্বের বৌদ্ধ ধর্মালম্বীদের কাছে অতিশয় পূজনীয় একজন ভিু। অনুত্তর ভিু সংঘ ত্রে ও স্বধর্মপ্রাণ দায়ক দায়িকাগণ মনে করেন যে তিনি অর্হৎ লাভ করেছেন। তাই তিনি শ্রাবক বুদ্ধরূপে সকলের কাছে পূজনীয়।
পূজা অর্চনা : চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও তারা নিজস্ব কতকগুলি পূজা-অর্চনা করে থাকে। এসব পূজার মধ্যে ভাতদ্যা অন্যতম। যা পূর্ব পুরুষের উদ্দেশ্যে অন্নদান করা বুঝায়। মাথা ধোয়া হলো আরেকটি পূজা যার মাধ্যমে কোন পরিবার পবিত্র হয়ে উঠে। অনেক সময় কোন গোজার লোক বাঘের কামড়ে মারা পড়লে তখন সে গোজার লোকেরা মিলে মাথা ধোয়া পূজা করে। মা লক্ষ্মীমা পূজা করা হয় নতুন ধান খাওয়ার আগে। ভাত ঝরা পূজা দেওয়া হয় সন্তানের অসুখ হতে আরোগ্য লাভ কামনা করার উদ্দেশ্যে। জুমের দোষ নিরসনের জন্য পূজা দেওয়া হয়। এটাকে ধুজ মারা পূজা বা জুম মারানো বলে।
গ্রামবাসীর মঙ্গলের জন্য সবাই মিলে থানমানা করা হয়। থানমানার সময়ে মা গঙ্গা বা গাঙ পূজা করা হয়। এ পূজা দেয়ার সময় একজন ওঝা পৌরহিত্য করেন। সাধারণত অগ্রহায়ণ মাসে থানমানা করা হয়। থানমানার সময়ে গ্রামবাসীরা সামর্থ্য অনুসারে চাল, শুকর, অন্যান্য দ্রব্যাদি ও নগদ টাকা দেয়। এ সকল আয়োজন করে সবাই মিলে আহার করেন। তখন বিভিন্ন ধরণের আলাপ আলোচনাও চলে। বিশেষ করে কে কত আড়ি জুম কাটবে, কোথায় কোন জায়গায় কে জুম কাটবে এসব নির্ধারিত হয় থানমানার আলোচনায়। যাদের বাড়তি বীজ ধান থাকে এবং যাদের বীজধানের ঘাটতি থাকে তখন সেখানে তার ভাগাভাগি বা সমাধা করা হয়। চাকমাদের আরেকটি পূজা হলো আদাম বন। বন মানে ‘নিষেধ’, কোন গ্রামে বা পার্শ্ববর্তী গ্রামে সংক্রামক ব্যাধি যেমন কলেরা ও বসন্ত দেখা দিলে আদাম বন করা হয়। একজন বৈদ্য গ্রামের প্রবেশ ও বাহির পথে বাঁশের চিহ্ন টাঙিয়ে দিয়ে আদাম বা গ্রাম বন করে। আদাম বন করার প্রধান কারণ হলো সতর্কতা অবলম্বন। যেন সে গ্রামে সংক্রামক রোগ থাকলে অন্যরা গ্রামটি এড়িয়ে চলেন বা সংক্রামক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি যেন ঐ গ্রামটি এড়িয়ে চলেন। আদাম বন করলে গ্রামবাসীদের কিছু সতর্কতা বা নীতি পালন করতে হয়। যেমন কোন কিছু মাটিতে হেছঁতে নেয়া যাবে না, দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা করা যাবে না, সন্ধ্যার সময়ে বড়ো ধরণের শব্দ করা যাবে না ইত্যাদি। অনেক সময় ভিন্ন কারণে আদাম বন করা হয়ে থাকে।
চাকমাদের আরেকটি পূজা হলো এদা দাগা। নিম্নে এদা দাগা সম্পর্কে বলা হয়েছে, ‘বাংলায় একটা কথা ভয়ে ‘আত্মরাম খাঁচা ছাড়া’ চাকমাদের মধ্যে এই কথাটার একটা অদ্ভুত বাস্তব নজির আছে। ক্ষেত্রে কিন্তু আত্মরামকে আবার বিশেষ প্রক্রিয়ায় খাঁচায় আনা যায়। এটাকে ভাতদ্যার মতো একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সংস্করণ বলা চলে। হাঁটি হাঁসি পা পা এই বয়সের ছোট ছেলেমেয়ে হঠাৎ যদি খুব ভয় পায়, অনেক ক্ষেত্রে সে ভয়ে একেবারে নেতিয়ে পড়ে। ছেলেটার বাবা, মা, যাদের খুব ন্যাওটা অনেক সময় তাদেরই কেউ রাগের বশে ছেলের উপর তর্জন গর্জন করে এরূপ বিপত্তি ঘটিয়ে থুাকে। তখন সন্তানটি ঘাড় সোজা করতে পারে না, চোখ বোঁজা অবস্থায় ভাতদ্যায় আবিষ্ট হয়ে পড়া লোকের মতো একঘেঁয়েভাবে কাঁদতে থাকে আর শিউরে উঠে। এসময় হয়ত গা সামান্য গরমও হয়ে থাকতে পারে। সহসা এর উপশম ঘটাতে না পারলে ছেলের প্রাণহানির আশংকা থাকে। এ অবস্থাকে বলে এদা জুরানা অর্থাৎ কিনা আত্মরাম খাঁচা ছাড়া হওয়া।৪০
যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় এরূপ ছেলেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায় তাকে বলে এদা দাগা। এই অনুষ্ঠানে কোন দেবতার পূজা হয়না এবং বিশেষ কোন মন্ত্রোচ্ছারণেরও কোন বালাই নেই। অঝা বা যে কোন অভিজ্ঞ লোক এ ব্যাপারে পৌরহিত্য করতে পারে। এ অনুষ্ঠানেও ভাতদ্যার মতো মেজাং এর উপরর আগ কলা পাতা পেতে আদারাহ সাজাতে হয়। তবে সেখানে ভাত তরকারী ইত্যাদি কিছু দিতে হয় না। উপকরণের মধ্যে লাগে মুরগীর বাচ্চা, কলা, আখ, আখের গুড় দুয়েকখানা বেঙ পিঠা আর একটি টাকা। আগের দিনে রুপোর টাকা দেওয়া হত। একাধিক দিলেও তি নাই। অনুষ্ঠান শেষে এগুলোতে সূতা জড়িয়ে কিংবা গেট লাগিয়ে ছেলে কিংবা মেয়ে তাকেই পড়তে দেয়া হয়। যার প্রস্তুত প্রণালী নিন্মরূপ:
মুরগীর বাচ্ছাটাকে জবাই করে সেটার পালক ছাড়িয়ে নাগিয়ে ফেলে মাথাটাকে ঘুরিয়ে এনে বুকের ছিদ্র দিয়ে পেটের ভিতর ঢুকিয়ে দিতে হবে। অনুষ্ঠানের সময় ছেলের মা সন্তানকে কোলে বাড়ীর সদর দরোজায় বসে থাকে আর নিজে মাটিতে অঝা আদারাহ বসায়। আদারাহ বসানো মেজাং এর সঙ্গে সাতগছি সুতো বেঁধে তার অপর প্রান্তে ছেলের মা হাতে ধরে থাকে। আদারাহ যার জন্যে সে যদি ছেলে হয় তবে একখানা গামছা দিয়ে আর মেয়ে হলে একখানা খবং কিংবা খাদি দিয়ে আদারাহ ঢেকে দিতে হয়। সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে গেলে অঝা আদারার ঢাকনা ঈষৎ ফাঁক করে এদা ডাকে। পাত্তুরু-তরু, ত বাবে কেচকেজেয্য, তম্মা কেচকেজেয়্যে ইত্যাদি ইত্যাদি। যার ভাবার্থ হলো তোকে বাপ শাসিয়েছে মা খেদিয়েছে এখন তারা তোকে কলা দিয়েছে, আখ দিয়েছে, আয় আয় তুই বুঝে নে। অঝা একখানা গামচা দিয়ে ডাকার মতো করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে থাকে এভাবে যতণ না একটা মাছি বসলে। তখন আদারাহ তুলে ছেলেকে গচানো হয়। অর্থাৎ তার সামনে ধরা হয়ে থাকে। সে সেখান থেকে যা খুশী একটা কিছু তুলে নেয়। তারপর ভালো হয়ে যায়।’ -বঙ্কিম কৃষ্ণ দেওয়ান
পার্বত্য বৌদ্ধদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে এ লৌকিক পূজা-অচনা ও অনুষ্ঠানাদি হয়ে আসছে। বর্তমান পার্বত্য বৌদ্ধরা অনেক সচেতন ও আধনিক শিায় শিতি হচ্ছে এবং ক্রমান্বয়ে এ সব কুসংস্কার ও লৌকিক ক্রিয়াকর্ম ও পূজা-অর্চনা পরিত্যাগ করে সম্যক ও যুক্তিনির্ভর ধর্মের আচরণে সচেষ্ট।
খাদ্যাভ্যাস : চাকমাদের খাদ্যাভ্যাস বাঙালি থেকে ভিন্ন ধরণের। খাদ্যাভাসের বিষয়ে চাকমাদের কোন সংস্কার নেই। চাকমাদের প্রধান খাদ্য ভাত। তারা সচরাচর শুকুর, মুরগি, ছাগল এবং বিভিন্ন বন্য প্রাণী ও পশুপাখির মাংস খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে থাকে। মাছ, শুটকি, কাঁকড়া, চিংড়ি, হাঙ্গর, ছিদোল (নাপ্পি) এবং বাঁশের অংকুর, বেতের ডগা, ওল, জুম চাষের বিভিন্ন সবুজ শাক সবজি খাদ্য তালিকায় প্রধান। তাদের খাদ্য রন্ধন প্রক্রিয়া ও স্বাদ বাঙালি খাদ্যের স্বাদ থেকে একটু ভিন্ন রকম। চাকমা সমাজে বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠানে এবং কর্মব্যস্ততা শেষে নিত্য কিংবা মাঝে মাঝে মদ পানের রীতি আছে। চাকমারা নিজেরাই ঘরে মদ তৈরী করে। এটা সমাজে স্বীকৃত এবং ইহা একটি অপরিহার্য পানীয়।৪১
মদ চাকমাদের অতি প্রয়োজনীয় একটি পানীয়। চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও সামাজিক প্রথায় মধের ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে দেখা যায়। সাধারণত মদের তিনটি রূপ দেখা যায়। যেমন- ১. মদ যা এক চুয়ানি ও দুচুয়ানিতে গুণগতমান দ্বারা ভাগ করা, ২. জগরা, আর ৩. কানজি। জগরা বিনি চাউল দ্বারা তৈয়ার করা হয়। কানজি এবং মদ সাধারণ চাউল দ্বারা প্রস্তুত করা হয়। চাকমাদের চুঙলাঙ পূজায় মদ লাগে। অতীতে বিবাহের ভোজের আগে উপস্থিত অতিথিদের এক চুমুক মদ দিয়ে আপ্যায়ন করা হতো। গ্রামাঞ্চলে এখনো এর সীমিত ব্যবহার রয়েছে। মৃতদেহ পোড়ানোর সময়েও ওঝারা মদ ব্যবহার করেন।
চিকিৎসা শাস্ত্র : চাকমারা নিজস্ব চিকিৎসা শাস্ত্র দ্বারা সমৃদ্ধ। চাকমা ভাষায় এটাকে তালিক শাস্ত্র বলা হয়। তালিক শাস্ত্র নিয়ে যারা চিকিৎসা কাজ করে তাদের বৈদ্য বলা হয়। সচরাচর বনজ ননান গুল্ম, লতাপাতা থেকে চিকিৎসার কাঁচামাল বা তালিক বানানো হয়। এছাড়া বিভিন্ন প্রাণী থেকেও চিকিৎসার কাঁচামাল সংগ্রহ করা হয়।৪২ অনেক সময় শুধু মন্ত্র দিয়েও চিকিৎসা করা হয়। চিকিৎসা ব্যতীত নানান কাজে চাকমা বৈদ্যরা মন্ত্র ব্যবহার করেন। যেমন- শিকার মন্তর, ফি বলা বা আপদ তাড়ানোর মন্ত্র, দুধ পিড়া মন্ত্র, হলুদ পড়া মন্ত্র, নুনপড়া মন্ত্র, চিগোনগুড়ার বমি প্রভৃতি।
ম্রোদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও কয়েকটি উৎসব : ম্রোদের জীবনচর্যা এবং কর্ম প্রক্রিয়ার অধিক বিচারে তাদেরকে প্রকৃতি ও সর্বপ্রাণবাদী বলা হলেও বর্তমানে তারা বেশির ভাগ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, অনেকে খ্রিষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হচ্ছে। তবে আবার অনেক তাদের নতুন ধর্মক্রামায় অনুরক্ত। প্রকৃতি পূজা, ম্রোরা প্রাচীনকাল থেকে বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী হলেও জীবনচর্চা ও কর্ম প্রক্রিয়ায় প্রকৃতি পূজার অনুসারী। তারা বৃপূজা, পাথর পূজা, মানত করা, গো হত্যা, জীবজন্তু বলি ইত্যাদি করে থাকে। অনেক সময় নানা কুসংস্কারে রীতি প্রতিপালন করেন। তারা আচার আচরণে আদিকালের।
ম্রোরা প্রধানত পাহাড়ে জুমচাষ করে জীবন নির্বাহ করে। খাদ্য হিসাবে ভাত প্রধান মাংস হিসেবে বন্য পশু পাখি, মুরগী, শুকর তাদের প্রিয় খাদ্য। এছাড়াও বিভিন্ন জীবজন্তু, গরু, কুকুর, সাপ, হরিণ, গিরাগিটি প্রভৃতি খায়। রোগব্যাধি হলে বিভিন্ন জীবজন্তু বলি দিয়ে বৃপূজা, পাথর পূজা, দেবতা পূজা ও মানত করে থাকে এবং মুক্তি কামনা করে। মুরুংদের দেবতার নাম ওরেং এবং উৎসবের নাম মুৎসলোং। ম্রোরা নিজেদের বৌদ্ধধর্ম বিশ্বাসী বলে দাবি করলেও অন্যান্য ধর্মের মতাদর্শেও বিশ্বাসী, ম্রোদের গ্রাম, বৌদ্ধ বিহারে (ক্যাং) নেই বললেই চলে। তারা সাংগ্রাইং হলে অবশ্যই বৌদ্ধ বিহারে যায়।
ম্রোদের বিভিন্ন উৎসব রয়েছে। যেমন- সুরাইলা পই, নিংসার কিয়োরী পই (নববর্ষ উৎসব), রামোলা পই/ত-থোয়াক পই (বনবাস উৎসব), লুদলা পই/নিংমানাই খাং পই (বাৎসরিক বিশ্রাম উৎসব), প্রাতলা পই/নিংচুর পই (বৎসর বিদায় উৎসব), তাংফুং (ধর্মীয় কৃত্য)। ফ্রান্সিস বুখানন বলেন, ম্রোরা ঈশ্বর, ঠাকুর রাম খোদার উপাসনা করে না, শুধু মহামুনির (বুদ্ধের) পূজো করে।৪১ ম্রোদের প্রধান উৎসবের নাম চিয়াসদ পই। ‘চিয়া’ শব্দের অর্থ হচ্ছে গুরু। ‘সদ’ শব্দের অর্থ ‘বল্লম’ এবং ‘পই’ বলতে নৃত্যানুষ্ঠান বোঝায়। জুম চাষের ফসল ঘরে তোলার পর মুরং পল্লীতে চিয়াসদ পই অর্থাৎ গো হত্যা নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। সদ্য বিবাহিত তরুণী ছাড়া এ নৃত্যানুষ্ঠানে সব বয়সের মুরং নারী পুরুষ অংশ নিয়ে থাকে। মুরংদের দেবতার নাম ‘থুরাই’। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মোফাজ্জলুল হক কর্তৃক ম্রো জনগোষ্ঠির কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ‘ম্রোচেট’।
ক্রামাধর্ম : ক্রামাধর্ম ম্রোদের স্বীয় ধর্ম, এ ধর্মের মূলকথা হলো একতা, সততা ও নিষ্ঠা। এ তিনটি নীতি প্রতিটি ম্রো শুনুক, বিশ্বাস ও নিঃশ্বাসের দ্বারা পালন করার জন্য ক্রামাধর্ম প্রবক্তা মেনলে ম্রো আহবান জানান। ১৯৮৪-৮৫ সালে বান্দরবানে লামার পোড়াপাড়ায় এ ম্রো কৃতি সন্তান ক্রমাধর্ম প্রবর্তন করেন। ম্রোদের ধর্ম বিশ্বাস ও আদর্শিক জীবন গঠনে তিনি এ ধর্মমত প্রচার করেন। তিনি ম্রো জাতির জন্য বর্ণমালাও আবিষ্কার করেন। ধর্মীয় উৎসবের সময় বা ধর্ম পালন ও ছুটির দিবসে তারা প্রাণী হত্যা করেন না। প্রয়োজন ছাড়া প্রাণী হত্যা নিষেধ। সারা বছরে ৩ বার ধর্মীয় উৎসব পালন করে থাকে। ম্রোদের মধ্যে সারা বৌদ্ধধর্ম ও খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারী তার স্ব স্ব ধর্মের বিধি বিধান পালন করে থাকেন। ম্রোদের পরিবারে কোন শিশু জন্মগ্রহণ করলে সাতদিন পর শিশুর নাম রাখা হয়। তখন ধাত্রী ও গ্রামের গণমান্য ব্যক্তিদের নিয়ন্ত্রণ করে আশির্বাদ কামনা করা হয়। শিশুটির বয়স ১২ বছর পূর্ণ হলে ‘তাং ফুং’ (ধর্মীয় কৃত্য) করা হয়।৪২ মেনলে ম্রো প্রবতিৃত ম্রো বর্ণমালাতে ব্যঞ্জনবর্ণ ২৩টি ও স্বরবর্ণ ৮টি অর্থাৎ সর্বমোট ৩১টি বর্ণমালা রয়েছে। ম্রো শব্দের নমুনা বাবা-পা, মা-উ, হাত-বাং, চুল-সাম, গরু-চিয়া,মাথা-লু প্রভৃতি।
ম্রোদের গরু হত্যার অনুষ্ঠান : গরু হত্যা ম্রো উপজাতিদের এক প্রকার বিশেষ ধর্মীয় পূজা, পূজাটি বৈচিত্র্যময়ভাবে পালন করে থাকে। গো হত্যা ম্রো উপজাতিদের একটি ধর্মীয় তান্ত্রিক পূজা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ম্রোদের ভাষায় সৃষ্টি কর্তার সন্তুষ্টির জন্য তারা এ গো হত্যা অনুষ্ঠান করে থাকে। তারা একটা বিশেষ নিয়ম নীতি মাধ্যমে গো হত্যা অনুষ্ঠান করে থাকে। ম্রোদের মাতৃমোচন পদ্ধতি, ম্রো সমাজের আদি বিবাহ প্রথা, ম্রো সমাজে সৎকার প্রথা প্রভৃতির নিজস্ব নিয়মনীতি মাধ্যমে সম্পাদন করে থাকেন।
মুরংরা তাদের উৎসবে ‘পুং’ নামে এক প্রকার বাঁশি বাজিয়ে থাকে। এ বাঁশি পাহাড়ে উৎপন্ন এক প্রকার জংলি লাউয়ের খোল এবং সুরু বাঁশের নল দিয়ে নিজস্ব কারিগরি কলা কৌশলে নিজেরাই তৈরি করে। চৈত্র সংক্রান্তি উৎসবকে মুরংরা ‘কবং পই’ উৎসব বলে। এছাড়াও ‘কংনাত’ নামে শীত ও বর্ষাকালে শহরে দুটি উৎসব উদ্যাপন করে থাকে।৪৫ ম্রোদের প্রাত্যহিক জীবনে জুম চাষের ক্ষেত বা পাহাড়ে শিকার একটি উল্লেখযোগ্য দিক। মুরাংরা সাদারণত জুম েেতর ফসল রা এবং খাদ্য সংগ্রহ করার জন্য ফাঁদ তৈরি করে থাকে। এ ফাঁদে নানা রকম বন্য জীবজন্তু ও পশুপাখি আটকা পড়ে থাকে। এত জুমচাষের ফসলও রা হয় এবং প্রাত্যহিক খাদ্যও সংগ্রহ হয়। শিকারের জন্য তারা বাঁশের বর্শা, তীল, ধনুক প্রভৃতি ব্যবহার করে থাকে। ম্রো জাতিসত্তার এ গো হত্যা অনুষ্ঠান বৌদ্ধধর্মীয়ভাবে গ্রহণীয় কর্ম নয়। এ অনুষ্ঠান তারা সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে করে থাকে।
খুমিদের সামাজিক ও ধর্মীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান-উৎসব
জুমচাষ অনুষ্ঠান : জুমচাষের উপর ভিত্তি করে খুমি সমাজে দুটি অনুষ্ঠান করা হয়। এর একটি ‘লবনা’ এবং অপরটি ‘চৌপলনা’।
লবনা : জুমে বীজবপনের পর যখন চারাগুলো ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করে জুমে তখনও বিভিন্ন, প্রকার আগাছা থাকে। এসব আগাছা মোট তিনবার পরিষ্কার করতে হয়। প্রথমবার পরিষ্কার করার পর অদৃশ্য ধান দেবতা ‘টিটো’ এর উদ্দেশ্যে পূজায় একটি মুরগি ও একজোড়া মুরগির ডিম উৎসর্গ করা হয়। এর ফলে ফসল ভালো ও উৎকৃষ্ট হয়। এ উৎসবই লবনা।
চৌপলনা : বছরের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে জুম থেকে ধান তোলার পর খুমিরা নবান্ন উৎসব করে থাকে। খুমি ভাষায় এ উৎসবের নাম ‘চৌপলনা উৎসব’। এ উৎসব পরিবার ভিত্তিক। কে কবে ধান তোলা উৎসব বা চৌপলনা করবে তা পরিবারের সদস্যদের উপর নির্ভর করে। এটি খুমি সমাজে অন্যতম প্রদান উৎসব।
আরাং চ্যাং : আরাং চ্যাং এর বাংলা অর্থ ‘রাজ উৎসব’ বা রাজমেলা। খুমি আদিবাসী যারা প্রাচীন ধর্মাবলম্বী এ উৎসবটি তাদের কাছে সবচেয়ে বড় উৎসব। যে কেই এ উৎসবটি ইচ্ছে করলেই করতে পারে না। এ উৎসবটি তাদের সমাজে সবচেয়ে ব্যয়বহুল এবং কঠিন নিয়ম-রীতি দ্বারা পালন করতে হয়। উৎসবটি পরিবার ভিত্তিতে করা হলেও এর সামাজিক সার্বজনীনতা ব্যাপক এবং বিশাল। এর আয়োজনও বিশাল। উৎসবটি সাতদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়। যে কোন ব্যক্তি এই উৎসবটি একবার আয়োজন করে থাকলে তার জীবদ্দশায় না হলেও তার সন্তানদেরকে অবশ্যই দ্বিতীয় বারের মতো উৎসবটির আয়োজন করতে হবে। যে পরিবারটি একবার এ উৎসবটি আয়োজনে সমর্থ হয় তার ঘরের প্যাটার্ন, বিভিন্ন কারুকাজ অন্যান্য ঘরের তুলনায় কিছুটা ভিন্ন। সে কারণে ঘরের প্যার্টান, বিভিন্ন কারুকাজ দেখেই তাদের সমাজের যে কেউ সেই পবিারটি শনাক্ত করতে পারে। এ কারণে ঐ পরিবারটি এবং তার বংশধরকে সমাজে উচ্চ মর্যাদার চোখে দেখা হয় এবং সে বংশধরদের তাদের ভাষায় ‘রাজগোষ্ঠি’ বলা হয়।
আ-ওয়া-আনা : খুমিদের বহুলভাবে অনুষ্ঠেয় বা পালিত লোকজ অনুষ্ঠান হচ্ছে ‘আ-ওয়া-আনা’ যাকে বাংলায় বলা যায় পাড়াবন্ধ। এ অনুষ্ঠান মূলত জুন-জুলাই মাসের মধ্যেই সম্পন্ন হয়। জুমের ফসল যখন একটু মাথা উঁচু করে দণিা হাওয়ায় দুলতে শুরু করে তখন এ পূজা করা হয়ে থাকে। মূলত এ পূজার উদ্দেশ্য হলো যাতে ঐ জুমের ফসল খুমিদের সাংবাৎসরিক খোরাক যোগাতে পারে। অনুষ্ঠানটি দু’দিন ধরে চলতে থাকে।
আঁ-তাঁইপাঁ : নতুন ভাত খাওয়ার অনুষ্ঠানে যে চিবিদ (যা খুমি ভাষায় ‘আহমু’ বলে) রাখা হয়, দুপুরে খাবার পর এ চিবিদ বা আহমু খাওয়ার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতার সময় যে হাঁড়িতে আহমু থাকে ঠিক তার বরাবার উপর থেকে একটি রশির সাহায্যে বাঁধা একটা লম্বা বাঁশের চোঙা টাঙানো হয়।
রেইনা, আরেচেইনা বা গোহত্যা উৎসব : এ উৎসবটি সাধারণত নভেম্বর হতে জানুয়ারি মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। জুমে যেন অধিক পরিমাণ ফসল ফলে সে লক্ষে এ উৎসব পালিত হয়। এ উৎসব খুমি সমাজে দু’ভাবে পালিত হয়। যারা মধ্যবিত্ত বা নিন্ম-মধ্যবিত্ত তারা যে গোহত্যা উৎসব উদযাপন করে তাকে ‘রেইনা’ বলা হয় আর সমাজের বিত্তবান বা ধনাঢ্য পরিবারের আয়োজনকে ‘আরেচেইনা’ উৎসব। বর্তমান খুমি সমাজের খ্রিস্টান ও ক্রামা অনুসারীরা এ উৎসব করে না।
ক্রামা ধর্মীয় উৎসব: আগস্ট, ডিসেম্বর, জুন ও মার্চ মাসে বছরে চারবার এই উৎসব হয়ে থাকে। নববর্ষ উদ্যাপন, ক্রামদি বনবাসের উপলক্ষে, বর্ষ বিদায় ও বাৎসরিক বিশ্রাম উৎসব হিসেবে ক্রামা ধর্মানুসারী খুমিরাও এ উৎসবসমূহ পালন করে থাকে। অন্যান্য এলাকায় ক্রামাধর্মানুসারী খুমি ছাড়া অন্য খুমিরা সাধারণত এই উৎসব পালন করে না।
সাংগ্রাইং : বৌদ্ধ ধর্মানুসারী খুমিরা এ উৎসব পালন করে থাকে। তবে মাত্র একদিন নববর্ষ উৎসব উদ্যাপন করে থাকে। এ উপলে ঘরে ঘরে পিঠা তৈরি হয় এবং পাড়ার লোকজনকে খাওয়া দাওয়া করানো হয়।৪৬
পার্বত্য চট্টগ্রামের ুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠির ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার এবং লৌকিকতা থেকে উত্তরণের উপায়
বাংলাদেশের বৌদ্ধ ইতিহাস ও পার্বত্য ক্ষুদ্র জাতিসত্তার উন্নয়ন, সমৃদ্ধি ও অগ্রযাত্রার প্রশংসনীয় পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে হিতকর। কিন্তু বৌদ্ধ জাতির সামগ্রিক প্রোপটের অন্তরালে রয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং তা হলো ইসলাম ধর্ম ও খ্রিস্টানধর্মের বিপুল প্রভাবের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের ভবিষ্যৎ কি? ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জীবন-জীবিকা ও অস্তিত্ব রায় কি হবে? বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধধর্মের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রশ্ন এসে যায়। এর কারণ প্রধানত, প্রথমত: বাংলাদেশের সমগ্র বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রায় অর্ধেকের বেশির বসবাস পার্বত্য চট্টগ্রামে। দ্বিতীয়ত: বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সাল থেকে পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জেলা থেকে যে বিরাট বাঙালি জনগোষ্ঠি পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করে তাতে উপজাতীয়দের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে বিরূপ প্রভাব পরিলতি হচ্ছে।৪৭ তৃতীয়ত: ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জীবন-জীবিকা, শিা, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বলয় বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। চতুর্থত: জম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং ভূমি বিরোধসহ নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে ঋদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিলুপ্তির পখে।
তথ্য পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ক্রমাগত অ-উপজাতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতির অধিকাংশই হলো সম্বলহীন ও ভূমিহীন কৃষক। সরকারের বিশেষ তত্ত্বাবধানে বাঙালিদের চাষপোযোগী সমভূমি ও পাহাড়ী এলাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, আর্থিক অনুদান ও ঋণসহ সব ধরণের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। সে কারণে উপজাতি বৌদ্ধরা ভূমি ও পাহাড়ী জমি ব্যবহার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, হচ্ছে দরিদ্র ও নি:স্ব। পার্বত্য শান্তি চুক্তির পর পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলেও বিভিন্ন পদপে ও কর্মকাণ্ডের কারণে আবার অশান্ত হয়ে উঠছে। বিশেষ করে চুক্তি বাস্তবায়ন্, ভূমি সমস্যা, উপজাতি-আদিবাসী স্বীকৃতি প্রসঙ্গ, উপজাতি বাঙালি দ্বন্দ্ব-সংঘাত, জাতিগত বৈষম্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি ও আচার-আচরণের ভিন্নতা বিষয় প্রকট হয়ে উঠচ্ছে।
পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠিকে নানাভাবে ভয় প্রলোভন দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করছে। অনেকেই নামমাত্র মূল্যে তাদের জমি বিক্রি করে দেয়। অনেকে ছলচাতুরি ও প্রতারণার মাধ্যমে জমি ও পাহাড়ী এলাকা দখল করে নিয়েছে। উপজাতি নারীপুরুষ নির্যাতনের স্বীকার হচ্ছে। ফলে সাম্প্রদায়িক ও সামাজিক অপরাধ ও অবিচার বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁরা শিা-দীা ও অর্থনৈতিক কারণে দরিদ্র, নিঃস্ব ও অসহায়। অর্থনৈতিক দৈন্যতা নানাবিধ কারণে তারা আজ নিজেদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও অস্তিত্বকে হারাতে বসেছে। তাদের অনেকেই আর্থিক সুযোগ-সুবিধা ও প্রলোভনের কারণে ইসলাম ধর্ম ও খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করেছে। বিশেষ করে দাতা সংস্থা ও খ্রিস্টানরা পার্বত্য চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন এলাকায় অনগ্রসর ুদ্র জাতিগোষ্ঠিকে সাহায্য সহযোগিতার নামে খ্রিষ্টধর্মে দীতি করছে। ফলে একদিন এমন অবস্থা হবে বাঙালি ও খ্রিস্টান প্রভাবিত হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব থাকবে না। তাই উপজাতিদের রার বিষয়ে সুশীল সমাজ তথা আদিবাসী পার্বত্য বৌদ্ধদের সচেতন ও আরো ঐতিহ্যবান হওয়া প্রয়োজন।
পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী বৌদ্ধদের আলোকপ্রদীপ পরম শ্রদ্ধেয় সাধনানন্দ মহাথের (বনভন্তে)। তিনি ১৯৭৬ সালে রাঙাগামাটিতে স্থায়ীভাবে অবস্থান করতে থাবেন। মহান পুণ্যপুরুষ, পরমপূজ্য বনভন্তে পার্বত্য অঞ্চলে আবির্ভাবের পর হতে বহু সংখ্যক মানুষকে ধর্ম পথে চালিত করেছেন, ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং অগণিত নারী-পুরুষের করুণ আর্তনাদ, শোক, বিলাপ, মুহ্যমানতা বিদূরিত করেছেন। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের বহু সংখ্যক শিষ্য গড়ে উঠে। অন্যদিকে ধর্ম জাগরণের ফলে সদ্ধর্ম দেশনা শ্রবণ ও ধর্ম-পুণ্য কর্ম সম্পাদনের জন্য মানুষের মাঝে ধর্মীয় চেতনা বৃদ্ধি হেতু রাজবন বিহারের শাখা বিহার নির্মাণের প্রয়োজন পড়ে। গত শতকের নব্বই দশকের মাঝামাঝি হতে এ পর্যন্ত রাজবন বিহারের অনুমোদিত ও অননুমোদিত শতাধিক শাখা বিহার, ভাবনা কেন্দ্র ও অরণ্য কুটির গড়ে উঠেছে। পরম পূজ্য বনভন্তের প্রধান শিষ্য শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির, শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ ভৃগু মহাস্থবির, শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ বুদ্ধশ্রী মহাস্থবির প্রমুখ মহান ত্যাগী ভিুগণ বিভিন্ন শাখা বিহারের সাথে সংশিষ্ট থেকে সাধারণ লোকদের সদ্ধর্ম আচরণ ও অনুশীলনে সবিশেষ অবদান রেখে চলেছেন। তাই যারা দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করতে চান তারা দুঃখ প্রদানকারী অকুশল ও পাপ কর্ম সম্পাদনে সতর্কতা অবলম্বন করে স্বীয় স্বীয় এলাকার বিহারের সাথে যুক্ত থেকে ও বাদ-বিবাদ রহিত হয়ে দান-শীল-ভাবনা র্চচা করতে সচেষ্ট থাকা উচিত। দুর্লভ মানব জীবন লাভ করেও যদি জেনে অকুশল কর্ম হতে বিরত থাকতে পারা না যায়, তবে তা অভ্যন্ত পরিতাপের বিষয় হবে। অকুশল বা পাপ কর্ম সম্পাদন করে কেউ বা সুখী হয় না। রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান- তিন পার্বত্য জেলা এবং ভারতে রাজবন বিহারের শাখা বিহার, ভাবনা কেন্দ্র ও কুটির নির্মিত হয়।
রাখাইন বৌদ্ধদের মধ্যেও অনেক কুসংস্কার, ধর্মীয় ও সামাজিক ক্রিয়াকর্ম, লৌকিক পূজা-পার্বণ ও আচার অনুষ্ঠান রয়েছে। বর্তমান সময়ে কক্সবাজার, পটুয়াখালী, বরগুণা অঞ্চলে রাখাইন বৌদ্ধদের বসতি হীন থেকে হীনতর হচ্ছে। এমন সময় আসবে এসব অঞ্চলে কোন রাখাইন বৌদ্ধ পরিবারের বসতি থাকবে না, থাকবে না কোন বৌদ্ধ বিহার ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি। এদের রায় ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি পুনরুদ্ধারে যথাযথ পদপে গ্রহণ করা প্রয়োজন।
সার্বিক পর্যালোচনা মতে, ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার এবং লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান লোকজীবনের এক অত্যাবশ্যকীয় অন্বয়। মানুষের ধীকল্প (idea), চিন্তা, আভ্যাস, রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান ও চর্যাবোধ পুনশ্চভাবে সপর্যাগত সংস্কৃতিতেই পর্যায়ক্রমিক প্রভাবিত। বিধিবদ্ধ নিয়মনীতি ও শাস্ত্রীয় বিধান থাকলেও বিভিন্ন কুসংস্কার ও লৌকিকতা মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এমনকি চর্যার ভিত্তিমূল হিসিবে অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। সকলে আষ্টে পৃষ্টে এই প্রায়োগিক লৌকিক কৃষ্টি সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত। এর মাধ্যমেই একটি জাতিগোষ্ঠির বিকাশ ও আত্মপরিচয়। জনজীবনে এসব কীভাবে বহুমাত্রিকভাবে প্রভাবিত করে এবং চর্যায় নিবিষ্ট হয় তার সম্যক পর্যেষণা। সমতলে বসবাসকারী বাঙালি বড়ুয়া বৌদ্ধ ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী বৌদ্ধ, পটুয়াখালী, বরগুণা, কক্সবাজারের রাখানই বৌদ্ধ এবং উত্তরবঙ্গের ওঁরাও বৌদ্ধদেরও একই অবস্থা। নৃতাত্ত্বিক ক্ষুদ্র জাতিসত্তা হিসেবে সমঅধিকার ও আত্মমর্যাদায় বসবাস করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। দিন দিন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বৌদ্ধরা শিল্প সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক, ভূমি, অস্তিত্ব রা, আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সামাজিক ও ধর্মীয় নানা সমস্যায় জর্জরিত। বর্তমানে ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার এবং লৌকিক আচার অনুষ্ঠান ছাড়াও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকেরা বিশেষত খ্রিষ্টান ও ইসলাম ধর্মে দীতি হয়ে যাচ্ছে। এর জন্য যথাযথ ব্যবস্থা ও সঠিক পদক্ষেপ অত্যন্ত প্রয়োজন।
তথ্যনির্দেশ :
১. আবদুল হক চৌধুরী, কক্সবাজার ইতিহাস সমাজ সংস্কৃতি, (চট্টগ্রাম, ১৯৮৪), পৃ. ৮৩
২. শ্রী শরৎ কুমার রায়, বৌদ্ধ ভারত, (কলকাতা, ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৬৫
৩. আহমদ শরীফ, প্রচ্ছ্ন্ন বৌদ্ধ সাহিত্য, সাহিত্য পত্রিকা, দ্বিতীয় সংখ্যা, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৩৫
৪. অলৌকিক নয় তবুও অলৌকিক (প্রবন্ধ), অধ্যাপক রতি মহাথের, স্মরণিকা, বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশন, (ঢাকা, ১৯৯৫), পৃ. ৪৫
৫. মুরারি ঘোষ, পাক্ আধুনিক বঙ্গ সংস্কৃতি, (কলকাতা, ১৯৮৩), পৃ. ২৩৬
৬. ড. তৃপ্তি ব্রহ্মা, বাংলার ইসলামী সংস্কৃতি, (কলকাতা, ১৯৮৭), পৃ.।
৭. ভিক্ষু সুনীথানন্দ, বাংলাদেশে বৌদ্ধ ভাস্কর্য, (এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৯), পৃ. ১৮-১৯
৮. ড. সুকোমল চৌধুরী, বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, (সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৭৬
৯. বিপ্রদাশ বড়ুয়া, শ্রামণ গৌতম, (জানুয়ারি, ঢাকা, ১৯৯৬), পৃ. ৪৬
১০. 10. Sir Charles Eliiot, Hinduism and Buddhism, (London, 1987)
১১. ভিক্ষু সুনীথানন্দ, বাংলাদেশে বৌদ্ধ বিহার ও ভিক্ষু জীবন, (বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫), পৃ. ২৩৪
১২. বৌদ্ধ মহাসংগীতি (প্রবন্ধ), শান্তি প্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, অর্ঘ্য, (চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহার, ২৩ অক্টোবর, ১৯৯২)
১৩. বঙ্কিম কৃষ্ণ দেওয়ান, চাকমা পূঁজা পার্বণ, (রাঙ্গামাটি, ১৯৮৯), পৃ. ১৮/পূর্বোক্ত, বৌদ্ধ ভারত, পৃ. ৪৮
১৪. পূর্বোক্ত, ড. সুকোমল চৌধুরী, বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, পৃ. ১৯
১৫. এম. তবিবুর রহমান, বেহুলার বাসার ঘরের ইতিহাস, (রাজশাহী, ১৯৮৯) পৃ. ২৫
১৬. ড. আশা দাশ, বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য, (ক্যালকাটা বুক হাউজ, কলকাতা, ১৯৬৯), পৃ. ৯২/৯৩
১৭. পূর্বোক্ত, বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য, পৃ. ৯৪
১৮. বৌদ্ধধর্মের তান্ত্রিকতা (প্রবন্ধ), জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, কৃষ্টি- – Kristi (মে, ঢাকা, ১৯৯৫/ ২৫৩৯ বুদ্ধাব্দ)
১৯. গোপেন্দ কৃষ্ণ বসু, বাংলার লৌকিক দেবতা, (নভেম্বর, কলকাতা, ১৯৯৩), পৃ. ১১২
২০. পুরাণ (হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থ)।
২১. আব্দুল হক চৌধুরী, চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা, (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮), পৃ. ১৮৭
২২. বিশুদ্ধাচার মহাস্থবির, সীবলী ব্রতকথা, (চট্টগ্রাম, ১৯৩৭), পৃ. ১৪
২৩. 23. Dr. Dilip Kumar Barua & Dr. Mitsaru Ando, Syncretism in Bangladeshi Buddhism, (Nagoya, Japan, 2002), pp. 121,150
২৪. সাক্ষাৎকার : সুবল চন্দ্র বড়ুয়া, গ্রাম- বিনামারা, ডাক- চিরিঙ্গা, থানা-চকরিয়া, জেলা-কক্সবাজার
২৫. সাক্ষাৎকার : বেন্জু বড়ুয়া, গ্রাম- শীলকূপ, ডাক- মনকিচর, থানা-বাশঁখালী, জেলা-চট্টগ্রাম
২৬. ধর্মরত্ন মহাথের, মহাপরিনির্বাণ সূত্র (অনু.), (চট্টগ্রাম, ১৯৪৯), পৃ. ১৮৫
২৭. 27. Ibid, Syncretism in Bangladeshi Buddhism, p. 143
২৮. পূর্বোক্ত, বাংলাদেশে বৌদ্ধ বিহার ও ভিু জীবন, পৃ. ২৪৩
২৯. ড. বেণীমাধব জন্মশত বার্ষিক স্মারক গ্রন্থ, জগজ্জ্যোতি, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা, (কলকাতা, ১৯৯২), পৃ. ১৭
৩০. আবদুল হক চৌধুরী, চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা, চট্টগ্রাম, পৃ. ১৮৭
৩১. পূর্বোক্ত, চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা, পৃ. ১৮৮
৩২. 32. Ibid, Syncretism in Bangladeshi Buddhism, p. 172
৩৩. ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া, বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মালম্বী বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর লোক সংস্কৃতির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, পি-এইচ. ডি অভিসন্দর্ভ, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭), পৃ. ২০২
৩৪. ড. দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া, বাঙ্গালী বৌদ্ধদের ইতিহাস, ধর্ম ও সংস্কৃতি, (চট্টগ্রাম, ২০০৭), পৃ. ২৩২
৩৫. দীনেশ চন্দ্র সেন, সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ, (কলিকাতা, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৩৯
৩৬. সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃতি ও সংস্কৃতি, উসাই, (রাঙ্গামাটি, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৪), পৃ. ৪১
৩৭. 37. Ibid, Syncretism in Bangladeshi Buddhism, p. 143-150
৩৮. শরদিন্দু শেখর চাকমা, চাকমা বৌদ্ধ সম্প্রদায় : উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও বর্তমান আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা (প্রবন্ধ), অনোমা, রজত জয়ন্তি সংখ্যা, (চট্টগ্রাম, ২০০৯), পৃ. ২১৩
৩৯. নবকুমার তনচঙ্গ্যা, পার্বত্য চট্টগ্রামের ধর্মের জাগরণে শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাস্থবির ও বর্তমান প্রেতি (প্রবন্ধ), দীপ্তি, (রাঙ্গামাটি, ২০০৮), পৃ. ১২৭
৪০. তনয় দেওয়ান, চাঙমাটারা, প্রত্যয়ন, (খাগড়াছাড়ি পার্বত্য জেলা, ২০০৭), পৃ. ৩০
৪১. বিপ্রদাস বড়ুয়া, পার্বত্য চট্টগ্রামের সাহিত্য ও সংস্কৃতি (সম্পা.), (দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩), পৃ. ১২৪-১২৫
৪২. পূর্বোক্ত, তনয় দেওয়ান, চাঙমাটারা, (রাঙ্গামাটি, ২০০৭), পৃ. ৩৯
৪৩. ভেলাম ভান সেন্দেল (সম্পা.), দক্ষিণপূর্ব বাংলায় ফ্রান্সিস বুখানন, (আইসিবিএস, ঢাকা, ১৯৯৪), পৃ. ৯০
৪৪. ইয়ং রিং ম্রো, ম্রোদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও কয়েকটি উৎসব (প্রবন্ধ), সমুজ্জ্বল সুবাতাস, (বান্দরবান, ২০০৫), পৃ. ৪৭
৪৫. সালাম আজাদ, শান্তি চুক্তি উত্তর চট্টগ্রাম ও আদিবাসী প্রসঙ্গ, (হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০১), পৃ. ১১৩
৪৬. চেীধুরী বাবুল বড়ুয়া, খুমিদের সামাজিক ও ধর্মীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান-উৎসব (প্রবন্ধ), সমুজ্জ্বল সুবাতাস, (বান্দরবান, ২০০৮), পৃ. ১০৭
৪৭. ড. নীরু কুমার চাকমা, বুদ্ধ তাঁর ধর্ম ও দর্শন, (মিনার্ভা পাবলিকেশন, ঢাকা, ১৯৯৬), পৃ. ১৬২
ভূমিকা:
বাংলাদেশ তথা বৃহত্তর চট্টগ্রামের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন পূজা অর্চনা, লোক সংস্কৃতি ও আচার অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। এ সকল ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার, পূজা-পার্বণ ও লোকাচারসমূহ সাধারণত পুরনো আস্তর নামে খ্যাত হয়ে থাকে। এটি শাস্ত্র শব্দের বিকৃত রূপ (হাস্তর>শাস্তর>শাস্ত্র)। প্রাচীন কালে এখানকার বৌদ্ধ অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত লৌকিক সংস্কৃতির আচার অনুষ্ঠানসমূহ শাস্ত্র বাক্য জ্ঞানে একান্ত ভাবে বিশ্বাস ও আচরণ করা হত বলে শাস্ত্র শব্দটি আঞ্চলিক উচ্চারণে ‘হাস্তর’ রূপ প্রাপ্ত হয়েছিল এবং তা প্রাচীন কাল থেকে পুরানো শব্দটি যুক্ত হয়ে ‘পুরানো হাস্তর’ নামে খ্যাত হয়ে এসেছে। খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগ হতে বড়ুয়া বৌদ্ধদের আর্যধর্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতি, ভাষা ও লিপি প্রচারিত হয়। বাঙালি বড়ুয়া ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের মতে, প্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন কুসংস্কার, লোকবিশ্বাস, লোক সংস্কৃতি ও আচার অনুষ্ঠানসমূহের প্রথম গোড়াপত্তন হয়েছিল।১
সহজ সত্য চিরকালই এক, কিন্তু সেই সহজ সত্যই মানুষ বারংবার ভুলে যায়। তথাগত বুদ্ধ সেই বিস্মৃত সত্য সরল ও হৃদয়স্পর্শী কথায় বলেছেন, সুবিজ্ঞভুত ক্রিয়াকর্মের আবর্জনা উড়িয়ে দিয়ে মানুষকে সত্যের উজ্জ্বল মুক্তি দেখিয়েছিলেন।২ ধর্মের প্রাণ হচ্ছে ‘বিশুদ্ধ বিশ্বাস’ (belief) । এই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই আসে সামাজিক জীবনাচরণ ও সংঘবদ্ধতা। ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনকে ধর্মীয় দিক থেকে সংহিত করার জন্য প্রতিটি সমাজেই ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানের প্রয়োজন। প্রত্যেক ধর্মেরই ধর্মীয় গ্রন্থ আছে (কখনো মৌখিক), আছে তার পবিত্র ভাষা, আছে মন্ত্র স্তোত্র ইত্যাদি। বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি যেহেতু প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে তাই তখনকার যুগ আর এখনকার যুগ এবং জ্ঞান মেধা ও প্রজ্ঞায় পার্থক্য দেখা যায়। এ সময় মানুষ আদিম (Primitive) কুসংস্র (Superstition) ও লৌকিক (Earthly) সংস্কৃতির বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল কিন্তু সেই কুসংস্কার অনিয়ম অপসংস্কৃতিগুলো আজো ধর্ম ও সমাজে বিদ্যমান। এগুলো সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে। বৌদ্ধ সমাজে বিশেষত Religious Rituals and Falk Belief ব্যাপক ভাবে প্রচলিত রয়েছে।
একবিংশ শতাব্দীতে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার লাভ ও চর্চার ফলে তার আড়ষ্টতা কিছুটা শিথিল হলেও এখনকার লোকজীবন থেকে তা একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। তাই সমগ্র বৌদ্ধধর্মে তথা বাঙালি বড়ুয়া বৌদ্ধদের মধ্যে লোক সংস্কৃতি ও আচার অনুষ্ঠানের প্রভাব ল্য করা যায়। একটু সচেতন ভাবে দেখলে বুঝতে পারা যায় যে, বাঙালি বড়ুয়া ও পার্বত্য বৌদ্ধদের আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মীয় ও সামাজিক লোক সংস্কৃতির প্রতিটি বিষয়ে লৌকিকতা বিদ্যমান। বাংলাদেশের বৌদ্ধেরা সেকালের যুগে ধ্যান-জ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষা ও শিল্পকলায় অগ্রসর ছিল ঠিক কিন্তু তারা লৌকিকতা (Worldlienss) বর্জিত ছিলেন না। সেকালের প্রাপ্ত লোক সংস্কৃতি ও আচার অনুষ্ঠানগুলো থেকে আমরা মুক্ত হতে পারছি না, পারছি না ছাড়তে, পারছি না পরিহার করতে। খ্রিষ্ঠপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতের চিন্তারাজ্যে এক তুমুল বিপ্লব ঘটেছিল। বহু শতাব্দী ধরে এদেশের হিন্দু আর্যগণ যে ধর্মীয় প্রভাব গড়ে তুলে ছিল তার আমূল পরিবর্তন সাধন করেন গৌতম বুদ্ধ। মূলত আধুনিক কালে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের প্রভাব এবং সামাজিক লোকাচার ও সংস্কৃতির ধারা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান ও রীতি-নীতি সরব হয়ে উঠে।
বর্তমান বাঙালি হিন্দু সমাজের অধিকাংশ লৌকিক দেবদেবী ও আচার অনুষ্ঠান আজ বৌদ্ধদের ঘরোয়া আচারে ও প্রাচীন ধর্মীয় সংস্কারে রয়ে গেছে। প্রচলিত অনেকগুলি আবার হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি রেওয়াজ।৩ বর্তমান বিশ্বায়ন হল যুক্তি তত্ত্ব ও কম্পিউটার বিজ্ঞান প্রযুক্তির যুগ। এ যুগের মানুষ বস্তুবাদে বিশ্বাসী, বাস্তবতায় বিশ্বাসী। বৌদ্ধধর্ম শাস্ত্রে লৌকিকতা ও অলৌকিকত্বকে সহজে মেনে নিতে পারে না। বাংলাদেশের বৌদ্ধরা থেররাদ আদর্শের অনুসারী। থেরবাদে প্রতিষ্ঠিত হলেও বৌদ্ধদের প্রকৃত আচরণে, বিনয় বিধানের অন্তরালে থাকে বিভিন্ন কুসংস্কার, লোক বিশ্বাস, আচার-আচরণ, পূজা-পার্বণ ও লৌকিক সংস্কৃতি। এমন কি ধর্মের তত্ত্বাশ্রিত আবেদন লৌকিক ধারায় নেমে এসে ধর্মের অলৌকিকত্বের বেড়া ভেঙ্গে জীবনাশ্রিত সংস্কৃতি হিসেবে রূপ লাভ করেছে। এর অসংখ্য উদাহরণ সমতলি বাঙালি বড়–য়া ও পার্বত্য নৃতাত্ত্বিক ক্ষুদ্র আদিবাসী বৌদ্ধদের মধ্যে সচরাচর বিদ্যমান।৪
ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে বাংলাদেশের বৌদ্ধরা বুদ্ধের প্রকৃত ধর্মদর্শন ও বিনয়নীতি সম্বন্ধে মোটেই অবহিত ছিলেন না। পাল ও গুপ্ত যুগের পরে বৌদ্ধধর্ম ক্রমশ নিজ বৈশিষ্ট্য হারিয়ে নানা কুসংস্কার ও লৌকিকতায় বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিল – এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বৌদ্ধধর্মের তাদৃশ বিপর্যয় বৌদ্ধদের ধর্ম ও সমাজ জীবনে দারুণভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। উল্লেখ যে বেন্ডেল সাহেবের মতে, ১৪৪৬ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশে প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম পুঁথি লিখিত হয়েছিল।৫ বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রধান দুটি ধারা থেরবাদ ও মহাযান প্রভাবান্বিত ছিল। বিশেষত লৌকিকতা ও বিভিন্ন মতাদর্শের কারণে পাল ও চন্দ্র বংশের রাজাদের রাজত্ব কালে বাংলাদেশে মহাযান ধর্মের প্রসার ঘটে। এই সময় তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের চারটি বিশেষ শাখা – বজ্রযান, কালচক্রযান, মন্ত্রযান, তন্ত্রযান ও সহজযান বাংলাদেশে নিজ নিজ প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করে। বর্তমান বিশ্বে মূলত হীনযান ও মহাযান এ দুটি ধারা বিদ্যমান। বাংলাদেশে মূলত থেরবাদ আদর্শের সংঘরাজ নিকায় ও মহাস্থবির নিকায় এ দু’সংঘ ধারা প্রচলিত আছে। এ শুধু বৌদ্ধধর্মে নয় প্রত্যেক ধর্ম এ রকম শ্রেণিভেদ ল্য করা যায়। যেমন- হিন্দুধর্মে শাক্ত ও বৈষ্ণব, মুসলিম ধর্মের শিয়া ও সুন্নি এবং খ্রিষ্টান ধর্মে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্ট।৬ এ সমস্ত শাখা প্রশাখা ও মতভেদের জন্য এ সমস্ত লৌকিক ক্রিয়াকলাপ, আচার ও সংস্কৃতি সৃষ্টি হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।
এবার বুদ্ধপূজা, বুদ্ধমূর্তি পূজা সম্পর্কে আলোচনা করা যায়, খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের প্রথম দিকেই বুদ্ধের মূর্তি তৈরি প্রথা আরম্ভ হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে তাঁর পূজার প্রচলনও আরম্ভ হয়েছিলো। পার্শ্ববর্তী ব্রাহ্মণদের ধর্মায়তন প্রভাবের ফলেই অলে কখন ভক্তদের মধ্যে বুদ্ধ পূজার প্রচলন আরম্ভ হয়েছিল তা বলা অত্যন্ত শক্ত ব্যাপার।৭
বুদ্ধপূজা : ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, ব্যাপক ভাবে বুদ্ধপূজার প্রচলন হয় কুষাণ যুগে, প্রথম খ্রিষ্টীয় শতাব্দীতে মহারাজ কনিষ্কের রাজত্ব কালে। উপাসকগণের মধ্যে এক শ্রেণির লোক যখন বুদ্ধের মূর্তি তৈরি করে বুদ্ধের পূজা করতে আরম্ভ করেছিল তখনই তাকে স্বগোত্রে অপর শ্রেণীর উপাসকগণ বুদ্ধ নিদ্দিষ্ট পার্থক্যেই দৃঢ় ভাবে অবলম্বন করে থাকলেন। প্রাচীন বৌদ্ধধর্মে বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ ত্রিশরণ মন্ত্র রূপে গৃহীত হয়েছিল। পরবর্তী যুগে বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ জ্ঞান-কল্যাণ-শক্তির প্রতীক রূপে ত্রিমূর্তি ধারণা করে বুদ্ধ বৌদ্ধদের পূজার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। কালক্রমে বৌদ্ধগণ কেবল বুদ্ধ ধর্ম সংঘের প্রতীক পূর্ণ করে সন্তুষ্ট হলেন না। ত্রিরতœ কে মানবীর মূর্তিতে রূপায়িত করে দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত করে নিলেন। পণ্ডিত সিদ্ধ হর্ষের সংগৃহিত ধাতব মূর্তি ক্রয়ের একটি ধর্মদেবতার প্রতিমা। এখানে ধর্ম বুদ্ধ দেবতার দেিণ পদ্মাসনে চতুর্ভূজা নারী মূর্তি উপবিষ্টা।৮
পুরাতত্ত্ববিদ Sir Cunningham এর মহাবোধি চিত্রে দেখা যায়- বুদ্ধদেবের বামে সংঘ ত্রিভূজা নারী মূর্তিতে এবং ধর্ম পুরুষ রূপে বুদ্ধের দক্ষিণ পার্শ্বে আসন গ্রহণ করেছে।৯ তার ধর্ম মতে যাগ, যজ্ঞ, ফেস প্রভৃতি পূজার কোন নির্দ্দেশ নেই। তাকে দেবতার আসনে বসিয়ে পূজার ব্যবস্থাও তিনি নিষেধ করে দিয়েছিলেন। বুদ্ধ নিজে কখনো তান্ত্রিক ভাবধারাকে স্বীকার করেননি। এ মতের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন বিখ্যাত বৌদ্ধ যোগচারী সন্ন্যাসী অসঙ্গ। প্রকৃত পে বৌদ্ধ অর্চনা হীনযানে ছিলই না। বুদ্ধের পরিনির্বাণের ৪/৫ শত বৎসর পরে বুদ্ধমূর্তি বিহারে প্রতিষ্ঠিত হয়। কারো কারো মতে, খ্রিষ্টীয় শতাব্দীর প্রথম শতকে মূর্তি নির্মিত হয়। ক্রমে আসতে লাগলো এক একটি ধ্যানী বুদ্ধ। প্রথম অভিতাভ, তার পর আেভ্য, বৈরোচন, রতœসম্ভব, তার পর অমো সিদ্ধি। বৌদ্ধধর্মে তখন ব্রাহ্মণ্য মতের তান্ত্রিক ভাবধারা প্রবল ভাবে প্রবেশ করেছিল। কারণ শেষে তারাদেবী, ডাক, ডাকিনী, পেত, যোগধ্যানী, হারতি, বৌদ্ধ শ্যামা দেবী প্রভৃতির উপাসনা করা হতো। ইহা নিঃসন্দেহে এই সকল পাপাচার চরিত্রহীন দেবদেবী। বৌদ্ধগণের ক্রিয়াকাণ্ডে লোক সাধারণের মনে বৌদ্ধ সমাজের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে ছিল এবং বৌদ্ধ সমাজ ধর্মহীন ভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এই প্রসঙ্গে ঝরৎ ঈযধৎষবং ঊষরড়ঃ তাঁর প্রণীত ঐরহফঁরংস ধহফ ইঁফফযরংস গ্রন্থে বলেছেন,Sir Charles Eliot Zuvi cÖYxZ Hinduism and Buddhism MÖ‡š’ e‡j‡Qb, The aberration of Indian religion is not due to its inherent depravity but to its Universality. In Europe those who follow dis-reputable occupation rarely suppose that they have anything to do with church. In India robbers murderer’s gamblers, prostitutes and maniwes all have their appropriate gods.10
বৌদ্ধরা ধর্ম বিশ্বাসে বৌদ্ধ ছিল কিন্তু ধর্মীয়, সামাজিক ও বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠনে তাদের বৌদ্ধ বলা অযৌক্তিক হবে। কারণ তারা বৌদ্ধধর্মের, বৌদ্ধ সংঘের বাহিরে তাদের সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য রার বিরোধী হয়। স্যার চার্লস ইলিয়াড লিখেছেন, It aimed not at founding a seat but at including all the world as lay believers of easy farms. This ascendant but its effect was disastrous when decline began. The line dividing Buddhist lay man from ordinary thirds became less and less marked.
ত্রিপিটকের সুত্ত নিপাত গ্রন্থে বুদ্ধ একস্থানে উপ শিব-এর প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, যিনি নির্বাণ প্রাপ্ত হন কোন ভাবেই তাকে পরিমাপ করা যায় না। তার আকৃতি নির্দেশ করা যায় না। যখন সমস্ত উপকরণ সরে যায় তখন তিনি অস্তিত্বে লীন হন। অস্তিত্বের এই উপকরণ হচ্ছে ধর্ম। চূড়ান্ত নির্বাণের পর এগুলো থাকে না। তখন নির্বাণ প্রাপ্ত ব্যক্তি আকিঞ্জন হয়ে যান। বুদ্ধ আরো বলেছেন যে, নির্বাণ প্রাপ্তকে পূজা দিতে হয় না। কারণ নির্বাণ প্রাপ্তগণ পূজা পান না। সুতরাং বুদ্ধের কোন ছবি বা মূর্তি তৈরি করে খাদ্য ভোজ্য আহার, বাতি, ধূপ, ফুল ও সুগন্ধী দ্রব্যাদি দ্বারা পূজা করা প্রকৃত অর্থে লোকাচার। উল্লেখ্য যে সাঁচীর বৌদ্ধ স্তূপ পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপো পরিচিত। সাঁচী ভারতবর্ষের মধ্য প্রদেশে অবস্থিত। বুদ্ধমূর্তি নির্মাণের উপকরণ হিসেবে কখনও কাঠ ব্যবহার হয়েছে, কখনও পাথর, কখনও ব্রোঞ্জ, কখনও স্বর্ণ বা অন্য কোন ধাতু। আবার দেয়াল গাত্রের ফ্রেসকো হিসেবে বুদ্ধমূর্তি তৈরি হয়েছে।
মহাপরিনির্বাণ সূত্রে বুদ্ধ এসব কিছুর পূজা করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেও বৌদ্ধদের অনাড়ম্ভরপূর্ণ উৎসব ও পূজা পার্বণ। যেমন বুদ্ধমূর্তি, স্তূপ, বোধিবৃ, বুদ্ধাস্থি, কৃত্রিম বুদ্ধ পদচিহ্ন ইত্যাদি প্রচলিত আছে। আর এ সব বুদ্ধ জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন পবিত্র বিষয় বলে বিহারে থাকে। বৌদ্ধরা এগুলোর পূজা করে থাকে।১১ এসব প্রচার অনুষ্ঠান নির্বাণকামী ব্যক্তিদের অপ্রয়োজনীয় হলেও ধর্মীয় আবেগ পূর্ণ করার ল্েয এগুলোর গুরুত্ব ও মূল্য অপরিসীম।
পদ্মসূত্রের কথা : বুদ্ধ নিজেকে সর্বদাই মানুষ হিসেবে ঘোষণা করেছেন এবং কখনও ঈশ্বর বা দিব্য পুরুষ বলে ঘোষণা করেননি। তিনি (বুদ্ধ) শিষ্যদের সম্যক উপদেশ প্রদান করেছেন। কিন্তু কালজয়ী মহাযানী পদ্মসূত্রে বুদ্ধের মতের বিরোধী বক্তব্য রয়েছে। এতে বলা হয়েছে, এই ত্রিজগৎ আমারই কর্মত্রে। এর সমস্ত প্রাণী আমারই সন্তান। কিন্তু এই পৃথিবী দুঃখময় এবং কেবল মাত্র আমিই তোমাদের বাঁচাতে এবং রা করতে পারি। বুদ্ধের কর্মবাদী ধর্মে, কখনও এসব কথা নেই, কিন্তু মূল নিক্কোও নিওয়ানো অনুবাদ করতে গিয়ে জ্ঞান বিকাশ বড়–য়া ‘শান্তির জন্য নিবেদিত’ গ্রন্থে ৩৯ পৃষ্ঠায় এমন লৌকিক অবাস্তব স্ববিরোধী কথার অবতারণা করেছেন। এ বক্তব্য যদি ঠিক হয় তাহলে বুদ্ধের ধর্মদর্শন ঈশ্বরবাদী বা একেশ্বরবাদী ধর্মের মাপকাটিতে পড়ে। ইহা আসলে লোকাচার দৃষ্টিভঙ্গি।
মাজার পূজা বা জেয়রত : ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায় যে, বৌদ্ধধর্মের সমাজ সংস্কৃতিতে বর্তমান সময়ে ইসলাম ধর্মের লৌকিক ক্রিয়াকর্মের মাজার জেয়ারত প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু সেই মাজার জেয়ারত বড়ুয়া ও পার্বত্য বৌদ্ধরা মাঝে মধ্যে করে থাকে। সময়ের বিবর্তনে ইসলাম ভাবাদর্শী মাজার জেয়ারত বৌদ্ধধর্মের এক বিশেষ করণীয় পূজা হয়। বৌদ্ধ ধর্মীয় ত্রিপিটক সাহিত্যের কোথায়ও মাজার পূজা সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায় না। তা সত্ত্বেও কিন্তু বড়ুয়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কাছে জনমনে মাজার পূজা আছে। কালের বিবর্তনে বৌদ্ধধর্মের পতন ও বিলুপ্ত প্রায় হয়েছিল একথা নিঃসন্দেহ। কিন্তু তারই সুবাধে বৌদ্ধধর্মের মধ্যে নয়; বরং বড়ুয়া বৌদ্ধ সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে সর্বোপরি মানুষের অন্তরে এই মাজার পূজা বা মাজার জেয়ারত কালক্রমে বড়ুয়া বৌদ্ধদের একটি প্রথায় পরিণত হয়।১২
সেই ছিন্ন লোকরীতি মাজার পূজা বাঙালি বড়ুয়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুল ভাবে প্রচলিত। লোকচার ও কুসংস্কার আদৃত কাল্পনিক এই মাজার পূজা বা জেয়ারত। একটু সচেতন ভাবে ল্য করলে দেখা যাবে যে, এই মাজার বা দরগাগুলো বিশেষ করে গড়ে উঠেছে প্রায় নির্জন বনে জঙ্গলে কিংবা অজ্ঞ অশিতি দারিদ্র নিরান্ন এলাকায় বা কোন যাতায়াত ব্যবস্থার মাঝে মাঝে এলাকা জুড়ে। মহাকারুণিক গৌতম বুদ্ধ প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম শাস্ত্র ত্রিপিটকে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, এসো, দেখ, পর্যালোচনা কর, নিজে জানো, সমালোচনা কর এবং নিজেকে প্রশ্ন কর। যদি গ্রহণীয় হয় তাহলে গ্রহণ কর আর যদি বর্জনীয় হয় তাহলে বর্জন কর। এছাড়া মহাপরিনির্বাণ সূত্রে তিনি বলেছেন যে, বৌদ্ধধর্মের মধ্যে যা কিছু গ্রহণীয় তা রা কর আর কোন কিছু যদি তোমরা সম্যক ভাবে পরিবর্তন চাও তাহলে তা সম্যকভাবে বিচার বিবেচনা করে সংস্কারযোগ্য হলে সংস্কার কর। গ্রহণযোগ্য হলে গ্রহণ কর। তাই বৌদ্ধধর্মের সার্বিক মতাদর্শ সকলের নিকট গ্রহণীয়। এতে কুসংস্কারের কোন স্থান নেই। তাই বড়ুয়া বৌদ্ধরা যে মাজার পূজা করে তা লৌকিক পূজা বা লোকধর্ম।
মাজারে যিনি খাদেম থাকেন, তিনি মানুষকে নানাভাবে কুসংস্কারের পন্থায় উৎসাহিত করে থাকেন। যে সব বিভিন্ন পন্থার কথা মাজারের পীর সম্পর্কে বলে থাকেন আর যে উদ্দেশ্যে মানুষ যায় তাহলো- ক) সকলে পীরের মাজারে বা দরগায় আসে মানত করে ও মানসিক পরিশুদ্ধতা লাভের আশায়। খ) গাছ গাছড়া জাতীয় ঔষধ ও মাদলী কবচ প্রভৃতি দিয়ে থাকেন। গ) জল পড়া, তেল পড়া, ডাব পড়া প্রভৃতিও দেওয়া হয় আগত লোক সাধারণকে। ঘ) পীরের দরগায় ফুল, ধূপ, দীপ, বাতিসহ শিরনী দেওয়া হয়। ঙ) সন্তান কামনায়, ব্যবসায় সফলতার জন্য, রোগ নিরাময় কমনায় দরগায় ইট বাধা হয়, ফুল প্রদত্ত হয় ও তাবিজ নেয়া হয়। চ) গরু, ছাগল, মুরগী প্রভৃতি পীরের স্মরণে উদ্যাপন করে তা পরে হাজত মুক্ত করে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়ে থাকে। ছ) গরু, ছাগল, মুরগী প্রভৃতি পীরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে পরে রান্না করে সকলে খেয়ে থাকেন।
মানত করা : মানুষের মধ্যে মানত করার প্রবণতা প্রতিনিয়ত ল্য করা যায়। মানত সকলের চেনা-জানা শব্দ ও বিষয়। কি হিন্দু, কি মুসলিম, কি খ্রিষ্টান দেখা যায় বৌদ্ধদের মাঝেও মানত করার প্রথা প্রচলিত আছে। তাদের সকলের বিশ্বাস যে তার দ্বারা মানুষের মঙ্গল হয়; সফলতা লাভ হয়। উল্লেখ্য যে, তাদের কোন কিছু কাজ কর্ম, লেখা পড়া, ব্যবসা বাণিজ্য, মনের ইচ্ছায় যদি সফলকাম হয় তাহলে তারা কোন দরগা, মসজিদ, মন্দির সেবাখোলা বা চার রাস্তার মাথায় গিয়ে গরু, ছাগল, মুরগি, কবুতর ইত্যাদি মানতের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেবেন। তাদের মনের ইচ্ছা পূর্ণ হলে মানত করা জিনিস সেখানে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে থাকেন। এটাও আসলে হিন্দু, মুসলিম সমাজের তথা বড়ুয়া বৌদ্ধদেরও এক ধরনের কুসংস্কার। এটা আসলে কাল্পনিক লৌকিকতা, কারণ এসব মানত করার পেছনে বাস্তবভিত্তিক চিন্তা ধারার কিছুই প্রতীয়মান হয় না। আমরা জানি বৌদ্ধরা যে সকল ক্রিয়াকর্ম করে আর পূজা পার্বণ করে তা শুধু বৌদ্ধধর্ম ভিত্তিক যুক্তিনির্ভর ও স্বয়ং বুদ্ধ নির্দেশিত। আর এ মানত করার প্রথা বা কর্মবাদী বৌদ্ধধর্মের শাস্ত্রে কোথাও উল্লেখ নেই। তাই এ মানত করার প্রবণতা বাস্তবে লোকধর্ম ছাড়া আর কিছু নয়।
সত্যপীরের সিন্নি : বড়ুয়া বৌদ্ধদের ধর্মীয় বা সমাজ সংস্কৃতিতে মুসলিম সমাজে সত্যপীরের সিন্নি নামে একটি বিশেষ প্রথা প্রচলিত। এছাড়াও মানিকপীর, বদরপীর সাহেব ও মর্জ্জির সিন্নি দিয়ে থাকেন। সত্যপীর মুসলমানদের অবতার কিনা তানিয়ে অনেক মতানৈক্য আছে। এ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন, মুসলিম সমাজের অবতার বিশেষ সম্প্রদায়েরও সত্যপীর বহুদিন হতে ‘সত্য নারায়ণ’ আখ্যায় হিন্দু সম্প্রদায়েরও পূজা লাভ করে আসছেন। উভয় সমাজেই এই শ্রেণির মিশ্র পূজা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন কবি ফকির দাস উদার প্রাণে লিখেছেন-
‘দেখো থাকে পুরাণে, কোরান থাকে দেখো
জোই রাম রহিম দোনাহি হোয়ে একো।’
ক্রমে ক্রমে তা বৌদ্ধ বড়ুয়া সমাজে প্রবেশ করে। বৌদ্ধদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। লোক মুখে প্রচলিত আছে যে, যদি কারো অভাব বা দুঃখ বা কোন কাজে অমঙ্গল দেখা দেয় তাহলে সে যদি এই সত্যপীরকে স্মরণ করে বা মানত করে সিন্নি দেয়। তাহলে তার অভাব, অনটন, দুঃখ, দুর্দশা আর থাকে না। এই সিন্নি জাতীয় লৌকিক অপসংস্কৃতিক পূজা অর্চনাদি বড়–য়া বৌদ্ধদের মধ্যে দেখা যায়। বড়ুয়া ও পার্বত্য বৌদ্ধদের মধ্যে লৌকিক অপসংস্কৃতির প্রবণতা প্রায় বেশী ল্য করা যায়। প্রকৃত পে অশিতি, অজ্ঞ লোকের মধ্যে এ ধরনের লৌকিক কুসংস্কার প্রচলিত আছে। মূর্খ মানুষের মধ্যে লৌকিক কুসংস্কারসমূহ বাসা বেধে থাকে। বুদ্ধের প্রদত্ত উপদেশ ও বাণীসমূহের মধ্যে এবং বৌদ্ধধর্মের কোন শাস্ত্রে এ সত্যপীরের সিন্নির উপমা নেই। তদ্সত্ত্বেও বৌদ্ধরা লৌকিকভাবে এ সত্যপীরের সিন্নি বা পূজা করে থাকে। অধ্যাপক দিলীপ কুমার বড়ুয়া তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ‘সোয়া সের দুগ্ধ লাগে সোয়া সের আটা,
সুপক্ক কদলি লাগে সোয়া সের মিটা।’১৩
সত্যপীরের সিন্নির উপকরণ সমূহ- চাউল ১ পোয়া, কলা ৯টি (বিজোড়), দুটি পাত্র, দই, গুড়, নারিকেল, মোমবাতি, ধূপ, ফুল ইত্যাদি।
জীনভূত বা পরীতে পাওয়া : লোক সমাজের মধ্যে জিনভূত বা পরীতে পাওয়ার কুসংস্কার দেখা যায়। তারা মনে করে থাকে যে, রাতে বা ভর দুপুরে গাছ তলায় বা পুকুর পাড়ে গেলে মানুষের বা গর্ভবতী নারীকে পরীতে পাবে, ভূতে পাবে, জিনে পাবে। প্রত্যেক ধর্মে তার প্রথা প্রচলিত আছে। এই প্রোপটে হঠাৎ যদি কেউ অসুস্থ বা অন্য কোন কারণে দ্বায়ী কোন কিছু হয় তাহলে তাকে বলা হয়ে থাকে জিনে পেয়েছে, ভূতে পেয়েছে, পরীতে পেয়েছে ইত্যাদি। আর তাকে ভাল বা সুস্থ করা জন্য প্রয়োজন হয় বৈদ্য, গাছা, ফকির, ভিক্ষু, মৌলভি ইত্যাদি।
বাণ টোনা ও বৈদ্য: বাংলাদেশে প্রাচীন কাল থেকে প্রতিটি ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বহুলভাবে প্রচলিত হয়ে আসছে বাণটোনা, বৈদ্য ইত্যাদি কুসংস্কার ও লৌকিক কাজ কর্ম। লোক সমাজ বিশেষ করে বৌদ্ধ সমাজে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নিকট তা ওতপ্রতোভাবে জড়িত এবং বহুল জন সমাজে পরিচিত। বিশেষ করে মগ, মারমা, রাখাইন ও চাকমা বৌদ্ধরা সব সময় করে এবং করে আসছে। এ বাণটোনা ও বৈদ্য এর সম্পর্কে মানুষের লৌকিক ধারণা ও দুর্বলতা আছে। যেমন :
কোন লোকের সাথে যদি কারো শত্রুতা থাকে তার বিনষ্ট বা তি সাধন কিংবা অমঙ্গল অবনতি ইত্যাদি করার জন্য মিথ্যা কুসংস্কারের আশ্রয় নিয়ে করা হয় বান টোনা। বাণটোনা যে ফল দেয় তা লোক মনে প্রচলিত আছে। তারা মনে করে-বাণটোনা দ্বারা শত্রুদের তি হয়। এ বাণটোনা করার অজ্ঞাত ধারণা প্রবল বিশ্বাস বিশেষ করে গ্রামের অশিতি সমাজে বিদ্যমান। এর আবার আর একটি ব্যাপার হল বৈদ্য দ্বারা অশুভ বাণটোনা থেকে রা পাওয়া। বাঙালি বৌদ্ধ সমাজে এ ধরনের বৈদ্যের আনাগোনা দেখা যায়। তারা বলে বাণটোনা থেকে রা করতে পারবে, রোগের উন্নতি করে দিতে পারবে। এ ছাড়া বৈদ্যেরা কোন লোকের রোগ হলে, হারানো গেলে, মানুষের অমঙ্গল দেখা দিলে নানা বিষয় সম্পর্কে হুবহু বলে দিতে পারে। এরা আবার ভালো করার জন্য নানান কথা বলে থাকে।১৩ বৈদ্যরা বাণটোনা কেটে রোগ ভালো করার জন্য প্রথমে কি হয়েছে দেখার জন্য নিবে কিছু টাকা, তার পরিমাণ এ ধরনের – ১.২৫, ৩.২৫, ৫.৫০ ইত্যাদি হারে। রোগ নির্ণয় করে পরে যা উপকরণ প্রয়োজন হয় কলার মোয়া, কচি ডাব, মোমবাতি, ধূপকাটি, কলা, মরিচ, পেঁয়াজ, রসুন, আদা .৫০ অথবা ১ কেজি, ১ ছটাক ভালো সরিষার তৈল, কদু বা লাউ, গৃহের কোণের শন ইত্যাদি ইত্যাদি।
নানা রোগের জন্য বৈদ্য নানা উপকরণ দিয়ে থাকেন। আর শরীরের সাথে দেওয়া হবে তার কাল্পনিক তৈরি দামী (২০০- ১০০০ টাকা) তাবিজ যাতে অপদেবতা বা শত্র“ তাকে কোন তি করতে না পারে, যেন কোন অবনতি বা অমঙ্গল না হয়। যুগে যুগে কুসংস্কারে বশবর্তী হয়ে তা মানুষের মধ্যে, সমাজের মধ্যে প্রচলিত হয়ে আসছে। এসব কিছু কৌশল অবলম্বন প্রতারণা বা লৌকিকতা ছাড়া আর কিছু নয়। বৌদ্ধধর্মের মধ্যে এমন কোন শাস্ত্র অনুসরণ করার জন্য বলা হয়নি। কিন্তু বৌদ্ধরা তা করে বস্তুত লৌকিকতার আশ্রয়ে যার কোন বাস্তব বা মৌলিক ভিত্তি নেই। বৈদ্যরা সহজ সরল অশিতি ও গ্রাম্য মানুষের কাছে গুরুবাবার আশ্রয় নেওয়ার নামে প্রতারণা করে থাকে। সে কৌশল অবলম্বন করে থাকে একজন তুলারাশি জাতকের লোক ঠিক করে গাছা বসায়। তার আসন তাকে দণি বা পূর্বমুখী যার যেমন ইচ্ছা তেমনি বসায়। বসার আসনে থাকে মঙ্গলঘট, এতে মন্ত্রপূত পানি নেওয়ার নামে গাছার মুখে ও মাথায় ছিটিয়ে দেয়, কাঁসা বাজায়, ধূপ জ্বলায়। বৈদ্যের মাকে অর্থাৎ লোক দেবীকে আবাহন করার জন্য গান গেয়ে থাকে। যেমন-
আইজ রে মা-মঘিনী মইঘ্যা রাজার ঝি
আইয় তুই সোনার নাধং কানত দি
তোয়ার জয়গান গাইতে মাগো আর জনম যায়
মগধেশ্বরী মারে মা শ্রীঘ্র দেখা দেঅ
তোয়ার আসন সজায়ইয়াছি বড় আশা করে
তুমি মাতা দিষ্টি দেঅ এই গাছার উ অরে
তোয়ার জলি দিয়ম মাগো শনি মঙ্গলবারে
তুমি মাতা কিরপা করঅ এই রোগীর উঅরে।১৪
ইত্যাদি বলে থাকে ছলনা বশে।
বৃক্ষ পূজা : বৌদ্ধরা বৃকে অর্থাৎ বৃ দেবতাকে প্রায় সময় পূজা ও বন্দনা করে থাকে। বড়–য়া ও পার্বত্য বৌদ্ধরা অমাবশ্যা ও পূর্ণিমা অষ্টমীর সময় সকালে বৃ পূজা করে থাকে। তাদের ধারণা বুদ্ধ বোধিবৃ তলে বসে ছয় বৎসর কঠোর তপস্যা সাধনা করে বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন, তাই বৃকে পূজা ও বন্দনা করে থাকে। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম মতাদর্শে বৃকে পূজা করা কুসংস্কার। কারণ বুদ্ধ নিজে কখনো এমন উপদেশ কাউকে দেননি যে বৃকে পূজা কর। বরং বুদ্ধ আমৃত পরায়ণ মানুষ যেন নিজেকে শুদ্ধ করে তার জন্য বলেছেন। প্রকৃত অর্থে বৃ বৌদ্ধধর্মে লৌকিক পূজা। কিন্তু দেখা যায় বোধিবৃরে ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনা করে শ্রীলংকাবাসীরা সবসময় অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে বোধিবৃ পূজা করে থাকে।
আট্কী মা পূজা : চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় তাকে আট্টক্কিনি পূজা বলা হয়। এ আট্কী মা পূজা বাঙালি বৌদ্ধদের বহুল প্রচলিত একটি পূজা। আর এই পূজা জনমানসে বহুলভাবে সমাদৃত হয়ে আসছে। বলা যায় সমাজ ব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে কুসংস্কার প্রথা। প্রচলিত আছে যে কেউ যদি বিপদে পড়ে বা ব্যধিগ্রস্ত হয় তাহলে এইসব কিছু থেকে অমঙ্গল রা পাওয়ার জন্য এই পূজা অর্চনা করে থাকে। বাস্তব প্রোপটে এই আট্কী মা পূজার কোন ভিত্তি আছে বলে মনে হয় না।
বৌদ্ধধর্ম সত্যের ধর্ম। লৌকিক বা কুসংস্কারের কোন স্থান নেই বৌদ্ধধর্মে। অথচ তবু মানুষ কুসংস্কার ও লৌকিকভাবে বিশ্বাসী হয়ে এ পূজা করে থাকে। বাঙালি বড়–য়াদের লৌকিকতা ছাড়া আর কিছু নয়। এবার আট্কীমার পূজার উপকরন সর্ম্পকে আলোচনা করা যেতে পারে। যদি পূজা দুটি বসানো হয় তাহলে পূজার উপকরণ লাগে কলা ১৬টি, পিঠা ১৬টি, দূর্বাঘাস (দুলা কের) ১৬টি, কাঁঠাল পাতা ১৬টি, যব ২টি, কলাপাতা ২টি, মোম ও ধূপ ১ প্যাকেট, প্রতিটি ভাগে থাকবে সিন্দুর ইত্যাদি।
এই আট্কী মার পূজার একটি ঐতিহাসিক গল্প আছে। পূজা করার সময় এ গল্প বলতে হয়। গল্প না বলে পূজা ভাঙ্গা যায় না। আর এ পূজার গল্প বাঙালি বৌদ্ধ পুরুষ ও নারীরা কম বেশী জানে। প্রতিটি পূজায় এ গল্প সকলের সামনে বলা হয়। গল্পের নমুনা বা কিছু অংশ প্রদত্ত হলো – এক ছিল রাজা তার ছিল এক মেয়ে। হঠাৎ যখন রাজা তার মেয়ের কথা জানতে পারল তখন যে প্রতিজ্ঞা করল আগামী কাল সকালে যাকে পাবে তার সঙ্গে তার বিবাহ দিয়ে দিবে। আর এ কথা তার মেয়ের খেলার সাথী শুনে তার বাবাকে বলে দিল তখন ঐ মেয়ের বান্ধবীর বাবা সকালে রাজার বাড়ীতে গিয়ে…..।
নদীতে মনসা পূজা : বেহুলার বাসর ঘর একটি ঐতিহ্যবাহী স্মৃতি। হাজার হাজার বৎসর পূর্ব থেকে মানুষের মনে নিয়ে এসেছে এক মহা বিস্ময়, মহাজিজ্ঞাসা। এই স্মৃতি চাঁদ সওদাগরের দৃঢ়তা, পদ্মার কোপ, মনসা মঙ্গল, নিতাই বাবু ও বেহুলার আলৌকিক সতীত্বের করুন কাহিনির সঙ্গে বিজড়িত। প্রাচীন প্রবীণ ব্যক্তিদের মুখ থেকে যা কিছু পাওয়া গেছে তাও এতে সংযুক্ত হয়েছে। কাহিনি স্থল বগুড়া। বেহুলা ও লক্ষ্মিন্দরের কাহিনি সেন যুগের অনেক পূর্বেকার ঘটনা। বেহুলার বাসর ঘর একটি কাল্পনিক মনুমেন্ট। বাসর ঘর বেহুলার দুঃসময় রজনীর একটি অম্লান স্মৃতি চিহ্ন। অভাগিনী বেহুলা তার মৃত স্বামী লক্ষ্মিন্দরকে নিয়ে বাসর ঘরের দরজায় বসে অঝোর নয়নে কাঁদছে। কারণ লন্দিরের লোহার বাসর ঘর। তাতে এ করুণ বিলাপ মনে হয় আজো শোনা যায়। বেহুলা বদ্ধ দরজার পাশে বসে বিনয় কণ্ঠে গাইতে লাগলো-
দাও মা দরজা খুলে
সিথির সিদুঁর মুছিয়াছি নয়নের জলে,
বাসর ঘরে দংশিল মা কাল নাগ আসিয়া,
তোমায় বুঝাব মাগো কোন ধন দিয়া।১৫
বেহুলার ধোপানীর প্রতিউত্তরে বললেন,
বিয়া রাতে পতিমোর খাইল নাগিনী
পতি লয়ে ভেসে যাই আমি অভাগিনী
কি আর কহিব মাসী তোমার নিকট
অভাগিনী নারী আমি পড়েছি সংকটে।
লক্ষ্মিন্দরের পিতা ছিলেন চাঁদ সাওদাগর, মাতা সুনুকা রাণি। বেহুলার পিতার নাম মুত্তেশ্বর ওরফে বাসোবানিয়া আর মাতার নাম কমলাদেবী। বেহুলার করুণ কাহিনী আলোকপাত করতে গেলে পদ্মাদেবীর কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। পদ্মার কূলে জন্ম হয়েছে বলে এই দেবীর নাম পদ্মা। এই দেবী বিষহরী নামেও পরিচিত। পদ্মা অযোনি সম্ভাবা চতুর্ভূজা ও ত্রিনয়ী স্বামীর নাম জরৎকারু মণিরাজ। পদ্মাদেবীর আটটি সর্প সন্তান ছিল।
পদ্মা পুরাণে আছে :
‘কাঁদরে সুনুকা দেবী কাঁদে সদাগর
কাঁদে আজো বেহুলার বিরহ বাসর।’
প্রকাশ থাকে যে এই দেবীর পূজা মন্সা পূজা। শ্রাবণ সংক্রান্তিকে অনুষ্ঠিত হয়। তবে স্থান বিশেষে সময়ের ব্যবধান বিচিত্র নয়। পূজা সকাল ১০-১২ টায় নদীতে ভেসে দিয়ে থাকে। ভেদে দেওয়ার আগে জোয়ার বা উলু দিয়ে থাকে আর সাথে সাথে স্নান করে থাকে। কিন্তু লোক এই মন্সা পূজা ডান হাতে এবং কিছু লোক বাম হাতে দিয়ে থাকে এরও অনেক কারণ আছে। ভেওলা উজান যাওয়ার ছয়মাস পর লন্দির জীবিত হওয়া, যাদু দিয়ে জীবিত মৃত হওয়া ইত্যাদি। হিন্দুধর্মের জাত কাহিনীর এই বেহুলা লèিন্দর তথা পদ্মা দেবীর মন্সা পূজা লৌকিক কুসংস্কার রীতি হিন্দুধর্মে নয়। যুগের সন্ধিণে বাঙালি বৌদ্ধদের রীতি-নীতিতেও পরিণত হয়। বড়–য়া বৌদ্ধদের মাঝে এখনো কিছু লোক এই লৌকিক মন্সা পূজা অপসস্কৃতির পূজা নদীতে বা পুকুরে তার স্মরণে পূজা দিয়ে থাকে। মান্সা পূজার উপকরণ সাধারণত যেসব লাগে তা হল- চাউল, দুধ, কলা, নারিকেল, ফুল, আখ, মোমবাতি, আগরবাতি, দুলাকের কলার বাক্ল, সিদুঁর প্রভৃতি।
নদীতে (গাং) পূজা : বড়ুয়া, চাকমা ও মারমা বৌদ্ধদের মধ্যে আর একটি হল নদীতে পূজা। যখন ঘট তোলার জন্য পুকুরে বা নদীতে গিয়ে ঘট ও ফুল পরিষ্কার করে তৈরি করে। তখন কিছু ফুল ও অন্যান্য পূজার উপকরণ নদীতে বা পুকুরে ভাসিয়ে দিয়ে থাকে। বিজ্ঞজনের মতে এটি হল নদীতে উপগুপ্ত স্থবিরকে পূজা করা। গ্রামে গঞ্জে এ প্রথা বিশেষ ভাবে প্রচলিত কিন্তু বার পূজা দেয় তারা কেন দেয় তা প্রকৃতগত ভাবে জানে না। বৌদ্ধধর্মের কোথাও এ পূজা সম্পর্ক জানা যায় না। তথা বড়–য়া বৌদ্ধরা তা করে থাকে। নদীতে বা পুকুরে এ পূজা দেওয়ার কাল্পনিক প্রথা লৌকিকতা ছাড়া আর অন্য কিছু নয়। সকল সচেতন আধুনিক যুগের মুক্ত মনের অধিকারী মানুষকে এ লৌকিক কুসংস্কার পরিহাস করে সত্যের অনুসন্ধান করতে হবে, তখনই সমাজ কুসংস্কার মুক্ত হবে, সত্য ধর্ম, সত্য ধারণা, সঠিক ইতিহাস জানতে সক্ষম হবে।
বৌদ্ধধর্মে বিভিন্ন দেব দেবীর পূজা : বৌদ্ধ সংস্কৃতি চর্চার উজ্জল নিদর্শন শিলালিপি ও তাম্রশাসনের মধ্যেও স্থানে স্থানে বর্ণিত আছে। বাংলার ইতিহাসের পালযুগ ছিল বৌদ্ধধর্মের সুবর্ণ যুগ। মঙ্গল কাব্যের দেবদেবীর পরিকল্পনা ও পূজা পদ্ধতির মধ্যে বুদ্ধমূর্তি তত্ত্ব এবং লোকাচার, ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রীর বিধি, লোকিক আচার ও ধর্ম বিশ্বাস সমন্বিত হয়েছে। এইজন্য মন্সা, চণ্ডী, ধর্ম ঠাকুর, শিব, দেবদেবী পরিকল্পনার সঙ্গে বিমিশ্রিত হয়ে পৌরাণিক দেবদেবীদের সঙ্গে একাসন অধিষ্ঠিত হয়েছেন।১৬
ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মে মহাশক্তির পূজা বিশেষ স্থান অধিকার করে। অন্যান্য দেব দানবের মূর্তির পাশে স্থান পেল ভীষণ দর্শনা মহাশক্তিরুপিনী নারীমূর্তি। ক্রমে এদের পাশে স্থান পেল ভুত, পিচাস ও পিচাশিনীদের মূর্তি। অলৌকিক শক্তির আধার রূপে এদের পূজা শুরু হয়। সপ্তম শতকের মধ্যভাগে ভারতে অনেক বোধিসত্ত্ব মূর্তির আবির্ভাব ঘটে। এসব মূর্তির পাশে ও স্থান পেয়েছিল নারীমূর্তি। এবং ভূত পিচাশাদির করাল মূর্তি। ওর পর নানাবিধ পূজা, ক্রিয়াকলাপ আচার উপাসনা ইত্যাদি বৌদ্ধধর্মে প্রবেশ করে। বৌদ্ধধর্মের বিকৃত হয় এবং এ বিকৃত বৌদ্ধধর্ম প্রথমে মধ্য এশিয়া দণি এশিয়ার রাষ্ট্রগুলিতে প্রচারিত হয়। পরবর্তী তিন চার শতাব্দী ধরে অন্তসার শূন্য এ বৌদ্ধধর্ম আরও শোচনীয় পর্যায়ে এসে পড়ে।
এবার অতীতে এবং বর্তমানে বৌদ্ধধর্মের অন্তরালে সমাজ সংস্কৃতিতে যে সব লৌকিক বা কাল্পনিক বিকৃত দেবদেবীর পূজা করতো এবং হচ্ছে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-
(ক) মাকাল ঠাকুর : প্রাচীন ভারতবর্ষে যখন বিভিন্ন প্রকার মতবাদ প্রচলিত ছিল, সেখান থেকে বিকৃত হয়ে এ মাকাল ঠাকুরের পূজা করা হতো। সে লৌকিক পূজা বৌদ্ধদের একটি দেবতা হল মাকাল ঠাকুর। বর্তমান ধর্ম বিশ্বাস ও সমাজে এর পূজা দেওয়ার প্রথা মাঝে মাঝে দেখা যায়। এটি বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের মৎস্য জীবিদের উপাস্য এক লৌকিক দেবতা। মৎস্যজীবিরা আবার দেবীর পূজাও করে থাকে তার মধ্যে বিশা লক্ষ্মী, খাল কুমারী প্রভৃতি দেব-দেবীর পূজা। বাঙালি বৌদ্ধদের সচেতনা ও আধুনিক শিায় শিতি হচ্ছে দিন দিন। তাই প্রাচীন কালের এই লৌকিক, কাল্পনিক, অপসংস্কৃতিসমূহ পরিহার করছে। অদূর ভবিষ্যতে এর বিলুপ্তি হবে বলে ধারণা করা যায়।
(খ) পাঁচু ঠাকুর : দেবদেবীর পূজা পাক ভারতে বহুল প্রচলিত ছিল। লোকরীতিতে আজো পল্লী অঞ্চলে অনেক বিচিত্র ও ভয়াবহ আকৃতির লৌকিক দেবতার পূজা পার্বণ দেখা যায়। এ পাঁচু ঠাকুরকে সকলে পেচোঁ ঠাকুর নামে পূজা দিয়ে থাকে।
(গ) ধর্ম ঠাকুর : মহাযানী বৌদ্ধদের উপাস্য ছিল ধর্ম ঠাকুর। বৌদ্ধ পার্বণ বা পূর্ণিমার সময় ধর্ম ঠাকুরের পূজা অনুষ্ঠিত হতো এবং তাদের সকলে ধর্ম ঠাকুরের প্রতি ছিল অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। তৎকালে বৌদ্ধদের ধারণা ছিল একে পূজা দিলে নৈবেদ্য ফল লাভ করা যায়। কিন্তু সে বিকৃত দেবতা পূজা বর্তমানে সমাজে প্রায় বিলুপ্ত।
(ঘ) বৌদ্ধ দেবদেবী : প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্ম বলতে মহাযানীদেরই বুঝায়। এই মহাযানীরা বুদ্ধকে একমাত্র পূজ্য স্বীকার করতেন না, নানা দেবদেবীর উপাসনা করতেন। সকল প্রকার ধর্মমতও স্বীকার করতেন। খ্রিষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে প্রচলিত তান্ত্রিক ধর্মের প্রভাবে মহাযানীদের তিনটি শাখার সৃষ্টি হয়। কালচক্রযান, বজ্রযান, মন্ত্রযান ও সহজযানীরা বিশালাীকে তাদের অন্যতম উপাস্য করে নেয়। এদের সাহিত্য চর্যাপদে বাচদালী নামে যে দেবীর উল্লেখ আছে তা ‘বাসলী’ বলে মনে হয়।১৭ সাধারণ মানুষের ‘বাসলী’ দেবীকে রোগ মুক্তি নজর পড়া অলণ কুলণ ইত্যাদি থেকে রা পাওয়ার জন্য আজও তেমাথা বা চৌরাস্তার মোড়ে পূজা অর্চনা করে থাকে।
ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে বলা হয়েছে যে-
‘মনের হরিয়ে আজি পূজিব বাসলী
নবল বিপ সম্মুখে দিব বলি।’
আবার অনিল পুরাণে উল্লেখ আছে-
‘মন দিয়া শোন সেই বাসুলী ব্যবহার
তাহার উঠিল কলঙ্ক আসুর ভাতার।’
(ঙ) অন্যান্য দেবদেবী : অতীতে অসংখ্য দেব দেবীর পূজা করা হতো তার প্রভাব আজো আছে। যেমন – হাড়িনী বা হারীতি, শীতলা দণিরায় (একজন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য ছিলেন), ত্রেপাল, সত্যপীর, পীরঠাকুর প্রভৃতি। বৌদ্ধরা হিন্দুধর্মের লক্ষ্মী পূজা, শনি পূজা, কার্তিক পূজা, মগদ্বেশ্বরীর পূজাও করতেন।
বর্তমান প্রোপটে সমাজ অঙ্গনের দিকে তাকালে ল্য করা যাবে যে- বাঙালি বৌদ্ধরা সেই প্রথম থেকে বিরোধিতা করছে। এ দেব দেবীর পূজা বড়–য়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে বিশেষ আধিপত্য জুড়ে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। শুধু ভিন্ন মতে কারণে বিকৃত ভাবে কিছু দেবদেবীর পূজা বড়–য়া বৌদ্ধরা করে ছিল এবং সে দেবদেবীর পূজা আজোবধি মাঝে মাঝে দেখা যায়। প্রকৃত পে এ দেব দেবীর পূজা কাল্পনিক, লৌকিক পূজা, চট্টগ্রামে নিভৃত গ্রামের অশিতি অজ্ঞ, দারিদ্র লোকের মধ্যে এ দেবদেবীর পূজা কিছুটা কম হয়ে থাকে। মিথ্যা ধারণায় বশবর্তী হয়ে এ লৌকিক দেবদেবীর পূজা করা হয়।১৮
কালী পূজা : হিন্দুধর্মের ধর্মীয় শাস্ত্র পুরাণের বর্ণনা মতে, হাজার হাজার বছর পূর্বে এক সময়ে রক্তবীজ নামে এক অসুর কোন এক শক্তিশালী দেবতা যা দেবীকে বসে এনে অমর বর লাভ করেছিলেন এবং লাভ করার সাথে সাথে স্বর্গ রাজ্য আক্রমণ করে স্বর্গের রাজা ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবদেবীকে মর্তে এনে দিলেন। ফলে তারা অকল্পনীয় দুঃখ দুর্দশার মধ্যে দিনযাপন করতে লাগলেন। দেবদেবীর চেষ্টায় নিজেদের সম্মিলিত শক্তির রূপকালী রক্তবীজ বধের জন্য যুদ্ধ শুরু করেন। আর এক সময়ে রক্তবীজ পরাজিত হন। এই তাৎপর্যের একটা রূপ/অবস্থা তৈরি করে পূজা করেন। মহাপরী এক শক্তিশালী কালী দেবীর শক্তিও কৌশল লাভের জন্য তার পর থেকেই কালী দেবীর অনুসারীরা পূজা শুরু করেন। কিন্তু বর্তমানে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজেদের তথা নিজ সমাজের অকল্যাণ বা অশুভ লণ দূর করার জন্য কালী পূজা করেন।
হিন্দুরা এক বাক্যে স্বীকার করে থাকেন যে, এ কালি দেবী এক মহান শক্তির দেবী। ১৯ মানুষ যেকোন জাগতিক বিপদ আপদ হতে রা পেতে যেন শক্তিমানের শরণাপন্ন হয় ঠিক তেমনি আধ্যাত্মিক ও জাগতিক সব বিপদ আপদ হতে মুক্তি বা রা পাওয়ার জন্য মানুষ কালী পূজা করে থাকে। প্রথম দিকে কলকাতায় কালী পূজা অনুষ্ঠিত হয় বলে ধারণা করা হয়। হিন্দুদের কালী পূজাকে বাংলাদেশী বড়ুয়ারা বর্তমানে না করলেও এক সময় এ পূজার ব্যাপক প্রচলন ছিল। প্রকৃত অর্থে এটি একটি লৌকিক পূজা বিশেষ। বৌদ্ধধর্মের কোন শাস্ত্র তথা বৌদ্ধ সমাজে এ পূজার কোন স্বীকৃতি নেই।
ভাতরান্না ও কার্তিক পূজা :
আশ্বিনে রান্না, কার্তিকে খায়
যে রব মাগে সে রব পায়।
যে রব মাগে অর্থাৎ প্রার্থনা করে তা পূরণের আশায় মানুষ এ কার্তিক পূজা বা কার্তিকের পান্তা ভাত রান্না করে থাকে। বস্তুত এ কার্তিক পূজা হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান পূজা।২০ এ পূজা বাঙালি বৌদ্ধ সমাজে বহুল ভাবে সমাদৃত। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল বা স্থান বিশেষে বড়ুয়া বৌদ্ধরা এ কার্তিক পূজা বা কার্তিকের ভাত রান্না করে থাকে। বাঙালি বৌদ্ধদের মাঝে প্রচলিত আছে যে কোন লোক যদি তার মনের আশা, বা অভাব অনটন, দুঃখ মুক্তি, যশখ্যাতি অর্জন ইত্যাদি থেকে রা বা উন্নতি লাভ করার জন্য যদি এ কার্তিক পূজা করা হয় তা হলে তার সে আশা পূরণ হয়। লোক সমাজে এ পূজার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। এটি লৌকিক কুসংস্কার ছাড়া আর কিছু নয়। এ ধরনের অনেক অলৌকিক অবাস্তব কাল্পনিক ও কুসংস্কার পরিপন্থী পূজার কথা প্রচলিত আছে এবং মানুষ তা অনুসরণ করছে। আসলে এসব লৌকিক পূজা পার্বণ।
সীবলী পূজা : সুন্দর ও অসুন্দর, বাস্তব আর লৌকিকতার মাঝে মানুষের বসবাস। সুন্দর চিন্তা চেতনা মানুষকে নানাগুণে গুণান্বিত করে। গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক। তাঁর ধর্মের মধ্যে কাল্পনিক, কুসংস্কার, অবাস্তব ও লৌকিক বলতে কিছুই ছিল না। কুসংস্কার ও কাল্পনিকা বর্জিত ধর্ম হল বৌদ্ধধর্ম। বুদ্ধ শুধু শাশ্বত ও চির সুন্দর অমৃত বাণী প্রচার করেছিলেন।
বুদ্ধের সময়ে পূজার কোন বিধান ছিল না এবং বুদ্ধের পরিনির্বাণে শত শত বৎসর পরেও সীবলী পূজা করা হতো না। যতদূর বিশ্বাস বুদ্ধের দেশিত, প্রচারিত ও প্রসারিত রীতি নীতিকে ঘিরেই বৌদ্ধধর্ম ও Buddhist Culture একথা বিশ্বাস করতে দ্বিধা নেই যে বুদ্ধের সময় বুদ্ধের মতাদর্শ ও বাণী লিখিত হয়নি।২১ প্রাজ্ঞ পণ্ডিত ভিক্ষু, দার্শনিক ও বিদগ্ধ ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় বুদ্ধবাণী ত্রিপিটক সংকলিত হয়। এই আলোচনা এতো গভীরে না নিয়ে সংক্ষেপে সীবলী পূজা কথা বলা যাক।
বাংলাদেশে বড়ুয়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে শীতলা পূজা ও তারাদেবীর পূজা করার প্রথা প্রচলিত। মূলত এ শীতলা ও তারাদেবী ছিল হিন্দুদের লৌকিক দেবতা পূজা। বৌদ্ধদের মধ্যে এ শীতলা ও তারা দেবীর পূজা পরিহার করার জন্য সীবলী পূজা প্রথা চালু করা হয়। বাংলাদেশের বৌদ্ধ পণ্ডিত বিশুদ্ধাচার মহাস্থবির এ সীবলী পূজার উদ্ভব করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলার কোথাও এ সীবলী পূজা প্রচলিত ছিল না। বিশুদ্ধাচার তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় লিখেছেন মহালাভী সীবলী স্থবিরের ব্রত কাহিনি। তিনি যে পুস্তক লিখেন তার নামকরণ করেন ‘সীবলী স্থবিরের ব্রতকথা’।২২ উক্ত গ্রন্থে লাভীশ্রেষ্ঠ অর্হত সীবলীর পুর্ণজীবন বৃত্তান্ত, গর্ভে বসবাস, জন্ম, নামকরণ, প্রব্রজ্যা, বুদ্ধের দর্শন, ভিু সংঘের সাক্ষাত, স্রোতাপত্তি ও অর্হত্ব লাভ, পুর্নজন্মের কর্মফল, পঞ্চশত ভিক্ষু ইত্যাদি। সীবলীর পিতা ছিলেন লিচ্ছবি রাজ মহালী কুমার আর মাতা ছিলেন সুপ্রবাসা রাণী। সীবলী কুমার সাত বৎসর সাত মাস গর্ভে মহাদুঃখী ভোগ করে জন্ম নিয়েছিলেন।
প্রচলিত আছে যে, সীবলী পূজা করলে মানুষের দুঃখ দুর্দশা দূর হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি হয়, খাদ্য বস্ত্র অভাব দূর হয়। দারিদ্রের বিত্ত, ধনীর মহাধন লাভ হয়। শত্রুতা থাকলে মিত্রতা লাভ হবে। জলে স্থলে যজ্ঞ দেবতা থেকে রা, সীবলী গুণকথা স্মরণ করলে মুক্ত হওয়া যায়। বৌদ্ধরা আজও বিশ্বাস করেন সীবলী পরিত্রাণ সূত্রপাঠ ও পূজা করলে কেউ অভাবী হন না। তাই বৌদ্ধরা ঘরে ঘরে সীবলী পরিত্রাণ সূত্র পাঠ ও সীবলী পূজা করেন। এ সীবলী ব্রতকথা নামক পুঁথি বা কাহিনী পড়তে হয়। পূজার সময় বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এ সীবলী পূজা এক ধরনের দেবদেবীর পূজার প্রথা রহিত বা দমন বা সাজ থেকে পরিহার করার জন্য এ প্রথা প্রচলন করা হয়। বুদ্ধের মতাদর্শ ও উপদেশবাণী ছাড়া সব কিছুকেই কুসংস্কার ও মিথ্যা বলে ধারণ করা হয়। সে দিক থেকে সীবলী পূজা লৌকিক পূজা। সময়ের প্রোপটে বৌদ্ধধর্মকে রার্থে সীবলী পূজা প্রচলন ধর্ম ও সমাজের জন্য ছিল মঙ্গলপদ। সুখ লাভ, দুঃখ দুর্দশা কিংবা বিপদ হতে মুক্তি লাভে মানুষ মানত স্বরূপ এ পূজা লোকাচারে প্রচলিত আছে।২৩
বৌদ্ধশাস্ত্র ত্রিপিটকে থেরগাথা গ্রন্থে এবং অন্যান্য পুস্তকে সীবলীর জীবন কাহিনি ও সীবলী পরিত্রাণ সূত্র আছে। সীবলী পূজার নানা উপকরণ হল মধু, ঘি, নারিকেল, চিড়া, আপেল, কমলা, মুড়ি, কলা, বিস্কুট, পেপে, আখ, মঙ্গলঘট, ছবি (বুদ্ধ ও সীবলী), ফুল, পান, সুপারি, মোম, ধূপ ও অন্যান্য উপকরণ। সীবলী পূজা করার সময় এক সাথে বুদ্ধ পূজাও করা হয়। পূজার সময় সীবলী ও বুদ্ধের ২টি ছবি সম্মুখ ভাগে রাখতে হয়।
সীবলী স্থবির বন্দনা : বৌদ্ধ শাস্ত্রে সীবলী স্থবিরের পালি ভাষায় বন্দনা হলো- সীবলী যং মহাথেরো লাভী নং সেটা তং গহতো মহন্তং পুঞঞাবতং তং অভিন্দামি সব্বদা।
বিভিন্ন সাহিত্যের উদ্ধৃতি থেকে প্রমাণিত হয় যে, পরিত্রাণ সূত্রের উদ্ভব বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পরবর্তী অন্যূন একশত বৎসর পরবর্তী যেমন রতন সূত্র, খণ্ড পরিত্ত, মেরাপরিত্ত, ধজগপরিত্ত, আটানটিয় পরিত্ত, আঙ্গুলিমাল পরিত্ত ইত্যাদি। বৌদ্ধ গৃহস্থদের বিশ্বাস জালো হাজালো জালং মহালাং জাল্লি, রিত্তি, মিত্তি, বিত্তি, ধনি, ধারণীতি -এ মন্ত্র পাঠক করে ধুল পাড়া দিলে গৃহের আগুন নিবে যায়, মিথ্যা ধারণা বশবর্তী হয়ে পড়ে। ফলে মৌলিক বৌদ্ধধর্ম লুপ্ত হয়ে পরিত্রাণ ও ধারণীর লৌকিকতা বৃদ্ধি পেতে থাকে।
মাংস ভক্ষণ : মাংস খাওয়া সম্পর্কে আলোচনার আগে আলোচনা করা যাক ভগবান বুদ্ধের পঞ্চনীতি নিয়ে। পঞ্চশীল হল- প্রাণী হত্যা থেকে বিরত, অদত্ত বস্তুগ্রহণ/ চুরি হতে বিরত, মিথ্যাকথা হতে বিরত, অবৈধ কামাচার হতে বিরত, সুরা-মদ/নেশা জাতীয় বস্তুগ্রহণ হতে বিরত থাকা। আমরা বুদ্ধের প্রচারিত মতকে দৃঢ়ভাবে ধারণ ও পালন করে থাকি। কিন্তু সকলে বলে থাকি যে প্রাণী হত্যা করা মহাপাপ। আসলে বুদ্ধ এমন করে উপদেশ করেননি; কখনও মহাপাপ বলে ভাষণ করেননি। তিনি বারংবার উপদেশ দিয়েছেন তোমরা প্রাণী বধ বা হত্যা থেকে বিরত থাকিও। অর্থাৎ অকারণে প্রাণী বধ না করা। মানুষকে চিরাচরিত নিয়মে জীবন যাপন করতে হলে কিছু না কিছু অবলম্বন করতে হয়। একটার উপর একটা নির্ভরশীল। বুদ্ধের কার্যকারণনীতি হল কোনটি বাদ দিয়ে মানুষের জীবন চলে না। এর অর্থ এই নয় যে, অহেতুক ভাবে কিছু করা। মানুষের জীবন ধারণ করতে গিয়ে প্রাণী বধ করত হয়। কিন্তু তা আমরা প্রাণী হত্যাকরলেও তার প্রতি অত্যন্ত বিমুখ। সম্যক দৃষ্টিতে প্রাণীবধ অপরাধ। কিন্তু জীবন ধরনের তাগিদে তা ত্রে বিশেষে বধ হয়।
সমাজে প্রথা সিদ্ধরীতি হলো বাঙালি বড়ুয়া বৌদ্ধদের গরু ও মহিষের মাংস খাওয়া যাবে না। আর প্রচলিত আছে যে, বড়ুয়া ও পার্বত্য বৌদ্ধদের অন্যতম প্রিয় খাদ্য শুকর, ছাগল, মুরগি মাংস। কি করে তা হতে পারে সবইতো প্রাণী। খেতে হলে বধ করে খেতে হবে। বৌদ্ধদের প্রচলিত রীতি নীতি মতে, প্রমার্জন অর্থে প্রাণী হত্যা না করে ক্রয় করে মাংস খাওয়া যাবে। অর্থাৎ পরোভাবে বলা। সুক্ষ্মদৃষ্টিতে এ নিয়ে একটু ভাবলে অনুধাবন করা যায় এটা এক ধরনের সামাজিক লোকাচার।
বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ এর পূর্বে প্রধান সেবক আনন্দকে বলেছিলেন যে, আনন্দ দশ প্রকার প্রাণীর মাংস ভণ করা নিষেধ। সেই দশ প্রকার প্রাণী কি কি ? যথা: মানুষের মাংস, বাঘ্রে মাংস, দীপিকার মাংস (বিড়াল), সিংহের মাংস, কুকুরের মাংস, অশ্বের মাংস, হস্তির মাংস, নেকড়ে বাঘ্রের মাংস, ভল্লুকের মাংস এবং সর্পের মাংস। বুদ্ধের মতে এসব অখাদ্য। আবার বুদ্ধ পরিনির্বাণ কালে আনন্দকে দুই প্রকার পিণ্ডপাত সমান ও সমফলপ্রদ দায়ক, সমান বিপাক দায়ক বিশিষ্ট অর্থাৎ অতীব ফলপ্রদ ও মহাপুণ্যপ্রদ বলে ভাষণ করেন- ১. সুজাতার পায়সান্ন ও ২. স্বর্ণকার চুন্দের শুকর মদ্দব (মাংস)।২৪
প্রকৃত পে বৌদ্ধরা মিথ্যা ধারণা ও লৌকিকতার আশ্রয়ে আদৃত হয়ে মাংস ভণ করে না। বড়ুয়া বৌদ্ধরা বিভিন্ন মাছ মাংস, তথা মুরগী, শুকুর ও অন্যন্যা প্রাণীর মাংস অনায়সে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। আর গরু, মহিষ, ছাগলের মাংস না খাওয়ার ফতোয়া লৌকিকতা ও কুসংস্কার ছাড়া আর কিছু নয়। প্রকৃত পে বড় প্রাণী কারণে বধ না করা এবং নিরামিষযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করার প্রতি বুদ্ধ সব সময় উপদেশ দিয়েছেন। বুদ্ধ পাঁচ প্রকার বাণিজ্যকে নিষেধ করেছেন- প্রাণী, মাংস, অস্ত্র, মদ, বিষ বাণিজ্য। বৌদ্ধধর্মে হিন্দুধর্মের প্রভাব ছিল একথা সত্য। কিন্তু আজও হিন্দুদের আচার, কৃষ্টির লৌকিক প্রথাগুলো আমাদের বৌদ্ধ ধর্মীয় কৃষ্টি সভ্যতা ও পূজা-পার্বণ থেকে বৌদ্ধরা আজো মুক্ত হতে পারছে না।
আল্পলানি : বৌদ্ধরা প্রধানত কৃষিজীবি। বর্তমানে ত্রে বিশেষে ব্যবসা ও চাকরি পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। বাঙালি বৌদ্ধরা কৃষি চাষ করার পূর্বে একটি বিশেষ উৎসব বা পূজা অনুষ্ঠান করে থাকে। এই উৎসবকে বলা হয় আল্পলানি বা অম্বুবাচী। একে হালপলানী পুজাও বলা হয়।২৫ বৌদ্ধদের সামাাজিক এ লৌকিক ক্রিয়াকলাপকে অনেক ভাবে বলে থাকে। হিন্দুরা বলেন আম্বুবাচীর দিন বড়–য়া চাকমারা বলে আল্পলানি। প্রচলিত আছে যে, চাষাবাদ করার আগে আল্পলানি নামক উৎসব বা পূজা করতে হয়। যদি এ আল্পলানি না করে তাহলে জমিতে ফসল ভাল হবে না। বড়ুয়াদের যেহেতু কৃষি প্রধান পেশা সেহেতু তারা এ আল্পলানিতে প্রচণ্ড ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে পূজা ও ক্রিয়াকলাপ করে থাকে। যাতে ফসল অধিক হারে জন্মায়। প্রকৃত পক্ষে বড়ুয়া বৌদ্ধদের মধ্যে এটা লৌকিক প্রথা। তারা মিথ্যার বশবর্তী হয়ে এ পূজা করে থাকে। কারণ তাদের বিশ্বাস ঐ দিন ধরিত্রী রাজস্বল হন।
আল্পলানির দিন বিশেষ খাদ্য তৈরী করা হয়। এ খাদ্য দ্রব্য গুলো লোকজনকে বিতরণ করে থাকে। তৈরীকৃত সামগ্রীর কিছু অংশ (কাঁঠাল, আম, সুজি, ভাত ও পিটা) চাষের জমিতে গিয়ে সকলকে প্রদান করে থাকে। আর সকলে এসব খাদ্য খেতে খেতে হৈ, হৈল্লা ও আনন্দ প্রকাশ করে থাকে। প্রকৃতপে এর দ্বারা কৃষকরা দেবতাকে পূজা করে থাকে। এটা আসলে এক ধরনের কুসংস্কার।২৫
কুসংস্কারের (Superstiotion) বেড়াজালে বৌদ্ধরা আষ্টে পৃষ্টে বাঁধা। এই কুসংস্কার প্রথা আমাদের সমাজ ও ধর্ম সত্য রীতিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কবি সুইফট বলেছেন, ধর্মীয় ও সামাজিক গোঁড়ামী দারিদ্রকে আরো দারিদ্র করে তোলে। এতদ্সত্ত্বেও ধর্ম মানুষ যা ভালো মনে করেছে তাকে দিয়েছে প্রচণ্ড সমর্থন, বলবৎ করেছে অবশ্য পালনীয় বিষয়। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের জন্য যা কল্যাণকর, উপকারী ধর্ম তাকে অনুমোদন দিয়েছেন দ্বিধাহীন ভাবে। আর ধর্ম মানুষকে সন্দেহ মুক্ত করেছে সাহস যোগিয়েছে। মেলিনোতস্কির মতে, ধর্ম সমাজে সংহতির স্তম্ভ স্বরূপ। তিনি তাঁর Magic, Secince and Religon (নিউইর্য়ক, ১৯৫৪) নামক গ্রন্থে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন, কিভাবে ধর্মীয় ক্রিয়া অনুষ্ঠান মানুষকে হতাশা, ভয় ও চরম নৈতিক অধঃপতন থেকে রা করেছে।২৪ ব্যাডফিক ব্রাউন তাঁর Structure and Function in Primitive Society (লণ্ডন, ১৯৫২) নামক গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন, কিভাবে ক্রিয়া ও অনুষ্ঠান সামাজিক ও ধর্মীয় সংহতিকে রা করে, মানুষের অস্তিত্বকে ধরে রেখেছে। ধর্ম যদি ব্যক্তি চরিত্র, বিশ্বাস, বিশুদ্ধ সংহতি, সামাজিক সমঝোতা রা না করতো, তাহলে মানব সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তো। মানব সমাজের ধর্মীয় পূজা পার্বণ, সমাজ সংস্কৃতি, আদি ঐতিহ্য জীবনের সঙ্গে তা গভীর ভাবে সম্পৃক্ত। জীবনের সকল পর্যায়ে তা আজ মজ্জা প্রোথিত, জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি পরিব্যাপ্ত।
একথা সত্য যে, শত কুসংস্কার, অপসংস্কৃতি ও বিভিন্নতা সত্ত্বেও ধর্মীয় বিশ্বাস, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, পূজা, পার্বণ ও সামাজিক রীতিনীতি মানুষকে অনিশ্চয়তার হাত থেকে রা করেছে। তাই বর্তমান এ প্রোপটে এর গুরুত্ব ও অপসংস্কৃতির শেকড় যতই গভীরে হোক না কেন, সকলের ঐকান্তিক স্বত:স্ফুর্ত সচেতনার মাধ্যমে এ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। বর্তমানে মানবতা ভুলুণ্ঠিত হচ্ছে। দ্বন্দ্ব, সংঘাত, হানাহানি, হিংসায় উন্মুক্ত পৃথিবীর সমস্ত অশুভ সংস্কৃতি ও মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতা পরিহার করে মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করতে হবে। এর মাধ্যমে সৃজনশীল মুক্তবুদ্ধির প্রগতিশীল আধুনিক সমাজ, দেশ ও জাতি বিনির্মাণ করা সম্ভব।
সামাজিক ক্রিয়াকলাপ:
বাংলাদেশের বৌদ্ধদের মধ্যে প্রাচীন কাল থেকে জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ ইত্যাদিতে বহ পুরানো নিয়ম-নীতি বা লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান করার প্রথা প্রচলিত আছে। নিম্নে সে বিভিন্ন সামাজিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-
সাধভক্ষুণ : সাধভণ হচ্ছে খাওয়ার স্বাধীনতা। গর্ভবতী রমনীকে সাতমাসে বা নবম মাসের সময় উৎকৃষ্ট খাদ্য ভোজ্যের মাধ্যমে সাধ ভণ করতে দেওয়া হয়। এসময় গর্ভবতীর পঞ্চম মাসে পঞ্চামৃত পান (দুগ্ধ, চিনি, ঘৃত, দধি ও মধু) করতে হয়। এছাড়াও গর্ভবতী রমনীকে বস্ত্র প্রদান এবং গুড়াপিটা, বাশুটি পিটা রান্না করে খাওয়ানো হয়। এ সময় সে যা খাওয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে তাকে সেই খাদ্য গুলো ভণ করতে দেওয়া হয়। কিছু দিন পর তাকে আবার বার মাসের নানান ফলও খেতে দেওয়া হয়। বড়ুয়া জনগোষ্ঠির মধ্যে ইহা ‘হাদি’ নামে পরিচিত। বৌদ্ধ দৃষ্টিতে সাধভণ একটি লৌকিক আচার অনুষ্ঠান।
সন্তানের জন্ম : বড়ুয়া বৌদ্ধদের রীতি অনুসারে সন্তান প্রসব হলে মহিলারা উলুধ্বনি দিয়ে থাকে। পুত্র সন্তান হলে পাঁচবার আর কন্যা সন্তান হলে তিনবার উলুধ্বনি দেওয়া হয়। বৌদ্ধ সমাজে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে ঘরে কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে রাখা হয়। প্রসূতি এবং নবজাতককে গরম পানি দিয়ে স্নান করে পাক পবিত্র করা হয়। তারপর নবজাতকের সারা গায়ে তৈল মেখে দেওয়া হয় এবং মধু খাওয়ানো হয়। শিশু জন্মের তিনদিন, পাঁচদিন বা সাতদিন পর মাথার চুল কামানো হয়। এ অনুষ্ঠানকে বলা হয় ‘হুদ’। প্রসবের প্রায় পনের দিন পর্যন্ত প্রসূতি অশুচি থাকে। সংসারের কোন কাজে তাকে অংশ নিতে দেওয়া হয় না। নবজাতকের নাভি ছেদন না হওয়া পর্যন্ত প্রসূতিকে বিহার কিংবা পূজার ঘরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না।
নামকরণ : বৌদ্ধদের মাঝে ছেলে মেয়েদের নামকরণ ও দোলনায় তোলা একটি বিশেষ আঞ্চলিক অনুষ্ঠান। শিশু জন্মের সপ্তাহ পর দোলনায় তোলা এবং আসল নামে নামকরণ করা হয়। জন্মের পরেই আদর করে অনেকে পছন্দ মত নাম রাখে। এটি ডাক নাম। আনুষ্ঠানিকভাবে দাদা-দাদী, আত্মীয়-স্বজনরা বই, খাতা, পেন্সিল, কলম (শিা ও জ্ঞানের প্রতীক), বোধিবৃরে পাতা (বীর্য ও প্রজ্ঞার প্রতীক), লজ্জাবতী পাতা (লজ্জার প্রতীক), নিদ্রালী পাতা (অধিক নিদ্রার প্রতীক), পাথর (গাম্ভীর্যের প্রতীক), মনকাঁটা (স্মরণ শক্তির প্রতীক), একখণ্ড লৌহা (শক্তি ও সাহসের প্রতীক) ইত্যাদি বিছানার পাশে রেখে শিশুকে দোলনায় শুইয়ে দেয়। মোমবাতি জ্বালানোর মধ্য দিয়ে পছন্দের নামটিসহ শিশুর আসল নাম রাখা হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে গণক ব্রাহ্মণ বা ভিুদের দিয়ে চিকুজী কুষ্ঠি করে তদানুসারে আসল নাম ঠিক করা হয়। আজকাল বড়–য়া সমাজে বৌদ্ধ হিন্দুরীতি মিশ্রিত আধুনিক নামই রাখা হয়ে থাকে। যেমন বেনীমাধব, সমরেন্দ্র, শশাংক, সুধাংশু, সারনাথ, মেঘনাথ, রাজপতি, সুবল চন্দ্র, শান্তিবালা, সুধাসিনী, দীপক, সুজাতা, নির্মল, তৃপ্তি, দীপা ইত্যাদি উপাধি হিসেবে চট্টগ্রামে বৌদ্ধরা লিখেন বড়–য়া আর পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধরা লেখেন চাকমা, মারমা, রাখাইন, তনচঙ্গ্যা, চাক, ম্রো, খুমি, খিয়াং, নেয়াখালি ত্রিপুরা অঞ্চলের বৌদ্ধরা লেখেন সিংহ, মাঝে মাঝে পেশাভিত্তিক উপাধি কিংবা প্রাপ্ত খেতাবও লিখতে দেখা যায়। যেমন- মুৎসুদ্দি, তালুকদার, চৌধুরী, সিকদার, মহাজন, রায় বাহাদুর, নাজির ইত্যাদি।
অন্নপ্রাসন : বৌদ্ধরা গৃহে পুত্র-কন্যার আগমনকে সুখের বলে মনে করে থাকে। সেই সাথে পুত্র-কন্যার মুখে প্রথম আহার দেওয়াকে অন্নপ্রাসন বলে। অন্নপ্রাসনকে আঞ্চলিক ভাষায় ‘ভাত ছোঁয়ানী’ বলা হয়। শিশুর মুখে অন্ন দেওয়া একটি আনন্দঘন অনুষ্ঠান। কোন পূর্ণিমাকে কেন্দ্র করে পঞ্জিকা তারিখ দেখে দিন ঠিক করা হয়। ঐদিন শিশুর মস্তক মুণ্ডিত করে স্নানের পর শিশুকে নববস্ত্র পরিধান করে মাথায় টোপড় পরানো হয়। তারপর বৌদ্ধ বিহার বা বোধিবৃরে মূলে শিশুকে নিয়ে যাওয়া হয়। উপাসনা শেষ করে বৌদ্ধ বিহারের প্রধান ভিুকে দিয়ে প্রথমে শিশুর মুখে অন্ন তুলে দেওয়া হয়। সাধারণত ছেলে হলে ৬ থেকে ৮ মাস এবং মেয়ে হলে ৫ থেকে ৭ মাস বয়সে অন্নপ্রাসন করতে হয়। সেদিন থেকে শিশুকে অল্প অল্প অন্ন খেতে দেওয়া হয়। এর আগে শিশুকে মায়ের দুধ বা বিকল্প দুধ খেতে দেওয়া হয়। এ উপলে ভিুদের পিণ্ডদান কিংবা সংঘদান এবং আত্মীয় স্বজনকে খাওয়ানো হয়। এ সময় অভিভাবকগণ নতুন থালা (অন্নের প্রতীক), গামছা (দীর্ঘায়ুর প্রতীক) এবং কাপড় (লজ্জা নিবারণের প্রতীক) উপহার স্বরূপ দেওয়া হয়।২৬
বিদ্যারম্ভ : বিদ্যারম্ভ বড়ুয়া বৌদ্ধদের আর একটি সামাজিক অনুষ্ঠান। আধুনিক বৌদ্ধ সমাজে এর বিধান আছে। প্রত্যেক পিতা-মাতারা বিদ্যারম্ভ মাঙ্গলিক কর্মাদির মাধ্যমে সম্পন্ন করে থাকেন। এদিনে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে পঞ্জিকা অনুসারে শিশুর বিদ্যারম্ভ করা হয়। শিশুর বয়স যখন তিন-চার বছর তখন এ অনুষ্ঠান হয়। এটি একান্ত ঘরের অনুষ্ঠান বলে অভিভাবকের আর্থিক সংহতি এবং সদিচ্ছার উপর এ অনুষ্ঠান নির্ভর করে।
প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা : বৌদ্ধ ধর্মীয় সামাজিক অনুষ্ঠানাদির মধ্যে দীক্ষা/প্রব্রজ্যা প্রদান একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় প্রথা। পারিবারিক জীবন ত্যাগ করে বৌদ্ধরীতিতে সন্ন্যাস অবলম্বনের নাম প্রব্রজ্যা। প্রব্রজ্যা বৌদ্ধ সন্ন্যাস জীবনের প্রথম পর্যায় বা শ্রমণ হওয়া। ‘পাপকানং মলং পব্বজেতী’তি।’ অর্থাৎ নিজের পাপমল বর্জনে সংকল্পবদ্ধ হন বলেই তাঁকে প্রব্রজিত বলা হয়। পরম প্রাপ্তি নির্বাণ প্রত্যাশাই প্রব্রজ্যা গ্রহণের অন্যতম উদ্দেশ্য। শ্রমণকে দশশীল প্রতিপালন করতে হয়। ন্যূনতম সাত বছর বয়স্ক শিশুকে দীা দেওয়ার রীতি আছে। প্রব্রজ্যার জন্য প্রয়োজন আট প্রকার দ্রব্য যাকে অট্ঠ পরিক্খার বলা হয়। তাহলো- ত্রি-চীবর (উত্তরাসঙ্গ, সংঘাটি, অন্তবাস), ভিাপাত্র, জলছাকনী গামছা, ক্ষুর ও কটিবন্ধনী, সূই-সূতার পিণ্ড। প্রব্রজ্যার পূর্বে তাকে প্রথমে স্নানাদি সেরে নতুন বস্ত্র পরিধান করা হয়। তার পর মাথার উপর প্রব্রজ্যার উপকরণসহ শোভাযাত্রা সহকারে বাড়ি হতে বিহারে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রব্রজ্যা প্রার্থীকে পিতা-মাতা ও অভিভাবকের অনুমতি নিতে হয়। এভাবে নানা পুণ্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে সাড়ম্বর ভাবে সংঘদান ও অষ্টপরিষ্কার দান দিয়ে প্রব্রজ্যা/দীা দান করা হয়। আগেকার দিনে নারীদের দীক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও বর্তমানে বৌদ্ধ সমাজে নারী জাতির দীক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে নারীরা সাধুমা হয়ে আলাদা ঘরে থাকে পারে।২৭ বিনয় বিধান মতে, ৭ বছরের ছোট শিশুকে প্রব্রজ্যা প্রদান করা হয়। কিন্তু তার Psychologe text বুদ্ধি পরীক্ষা করে দেয়া হয়। পালিতে একে ‘কাকাতুয়া’ প্রব্রজ্যা বলা হয়। একজন কুলপুত্র গাহস্থ্য বা সংসার দুঃখ, চিত্তের মল বা ধিকার বা পাপ মল পক্কালনের জন্য ভব দুঃখ হতে মুক্তি লাভের আশায় সকল বিষয়ে লোভ, দ্বেষ, মোহ, ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে।
প্রব্রজ্যা প্রার্থী পালিতে বলেন, ‘সব্বদুক্খ নিস্সরণ নিব্বানং সচ্ছিকরণত্থায ইমং কাসাবং গহেত্বা পব্বাজেত্থ মং ভন্তে, অনুকম্পং উপাদায’ (তিনবার)। এর পর ধর্মীয় বিধান মতে, ভিু তাকে সদ্ধর্মে দীক্ষা প্রদান করে থাকেন।
শ্রামণ থেকে ভিু হওয়ার যে অনুষ্ঠান তাকে উপসম্পদা বলে। প্রথমে কেউ উপসম্পদা গ্রহণ করতে পারে না। আগে প্রব্রজিত হয়ে শ্রামণ্যধর্মে দীক্ষা এবং বয়স বিশ হলে উপসম্পদা নিতে পারেন। প্রবীন প্রাজ্ঞ ভিুর নিকট অষ্টপরিষ্কার নিয়ে শরণাপন্ন হয়ে উপসম্পদা গ্রহণ করেন। উদক সীমায় উপসম্পদা গ্রহণ করার রীতি প্রচলিত আছে। উপসম্পদার জন্য সংঘ তথা কমপক্ষে পাঁচজন ভিুর প্রয়োজন হয়। উপসম্পদা প্রার্থী প্রার্থনা করেন – ‘সঙ্ঘং ভন্তে উপসম্পদং যাচামি, উল্লম্পতু মং ভন্তে সংঘো অনুকম্পং উপাদায।’ তখন ভিক্ষুসংঘ কর্মবাচা পাঠ করে উপসম্পদা প্রদান করেন। ভিুকে বিনয় পাতিমোক্খ বিধান মতে, ২২৭ টি শীল প্রতিপালন করতে হয়।
কর্ণছেদন ও নাসিকা ছেদন : বাঙালি বৌদ্ধ সমাজে মেয়েদের কর্ণছেদন ও নাসিকা ছেদনকে আঞ্চলিক ভাষায় কান ফুড়ানী ও নাক ফুড়ানী অনুষ্ঠান বলে। বিবাহের আগে বৌদ্ধ কুলপুত্রকে যেমন প্রব্রজ্যা দীক্ষা নিতে হয়, তেমনি মেয়েদের বিবাহের আগে কর্ণ ও নাসিকা ছেদন করা অনিবার্য বলে মনে করেন। কারণ বিয়ের আগে মেয়েদের কান ও নাক ফুড়ানো হয় তারা যেন বিবাহের সময় স্বর্ণালংকারগুলো নাকে ও কানে পরিধান করতে পারে।
বড়ুয়া বৌদ্ধরা এ অনুষ্ঠান আড়ম্বর পূর্ণভাবে করে থাকে। এ আনন্দঘন জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান আত্মীয় স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশী সকলকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করা হয়। আর সে উপলে সাধ্যমত অতিথি আপ্যায়নের খাওয়া ও মেলা দিয়ে থাকেন। এ অনুষ্ঠান সাধারণত দুপুর বেলায় করার হয়। ইহাতে কর্ণ ছেদনের পূর্বে বোনের জামাই ও দাদা-দাদীরা সকলে মিলে মেয়ের আত্মীয় স্বজন থেকে বায়না ধরে এবং সকলে আনন্দ উল্লাস করে থাকেন। কান ফুড়ানী ও নাক ফুড়ানী অনুষ্ঠানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বা আকর্ষণীয় দিক হল শিয়ালি প্রদান অর্থাৎ কান ফুড়ানোর পর এদিন মেয়ের সকল আত্মীয় স্বজন কানের বালি, স্বর্ণ, জামা, প্যাণ্ট, স্কাট, সেলোয়ার কামিজ, টাকা, বিভিন্ন উপকরণ ইত্যাদি দিয়ে থাকেন। এগুলো শিয়লি করে লিখে রাখা হয় এবং পরবর্তীতে তার ঐ ধরনের কোন অনুষ্ঠানে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। ত্রে বিশেষে বড়ুয়া মেয়েদের কর্ণ ছেদন করলেনও নাক ফুড়ানো হয় না।
বিবাহ ও যৌতুক প্রথা : বিবাহ বা পরিণয় প্রথা একটি বৃহৎ সামাজিক অনুষ্ঠান বর্তমান প্রোপটে বিবাহ প্রথার গুরুত্ব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বৌদ্ধ মতে, বিবাহের পূর্বে বর কনেকে বিবিধ গৃহকর্ম সম্পাদন ও ভিুদের নিকট ‘মঙ্গলসূত্র’ শ্রবণ করতে হয়। তবে বর্তমানে এ অনুষ্ঠানের কোন সর্ব সম্মত বিধি বা নিয়ম করা চলে না। তথাগত বুদ্ধ বিবাহ প্রথা সম্পর্কে কোন উপদেশ প্রদান করেননি। উল্লেখ থাকে যে বৌদ্ধ আচরণে বিবাহ বা পরিণয় প্রথা সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া যায় না। তাই বুদ্ধ পরিণয় প্রথা সম্পর্কে কোন মতামত প্রদান করেননি। কিন্তু তিনি তৎকালিন পরিণয় প্রথা সম্পর্কে কোন বিরোধিতাও করেননি বলে ধারণা করা হয়। তবে বুদ্ধ শুধু বারংবার বিবাহ প্রথা সম্পর্কে অনীহা ও অনুৎসাহ প্রদান করেছেন। এছাড়াও বুদ্ধ সব সময় মানুষকে প্রব্রজ্যা ধর্ম গ্রহণ করে সংসার ত্যাগী হওয়ার জন্য উৎসাহ দান করেছেন। বুদ্ধকালীন সমাজে সংস্কার সাধন করার মত অনেক অপসংস্কৃতি বা কুপ্রথা সমাজে বিদ্যমান ছিল। বুদ্ধ সব সময় তৃষ্ণামুক্ত, অবজ্ঞাহীন সৎজীবন ও মুক্ত বিহার করার কথা বলেছেন।২৮ বুদ্ধের বিবাহ প্রথার অনীহা ল্য করে প্লেটো বলেছেন- ‘এ জগৎ বা ভব পৃথিবীতে যদি পরিণয় প্রথা না থাকতো তাহলে এ জগৎ ক্রমে নিঃস্ব, জনশূন্য হয়ে যেতো।’
বিশ্বের সকল সভ্য মানব সম্প্রদায় বিবাহ প্রথাকে স্বীকার করে নিয়েছে। বৌদ্ধধর্মের চিরাচরিত নিয়মে ও বিধান অনুসারে বিবাহ প্রথা যুক্তি সঙ্গত নয়। বিয়ে শাদী সাধারণত লৌকিক আচার অনুষ্ঠান। প্রাচীন কাল থেকে প্রতিটি মানুষের মধ্যে এ বিবাহ প্রথার লৌকিক আচার অনুষ্ঠান হিসেবে প্রচলিত ছিল। আদিম জনগোষ্ঠির উদ্ভব কালে স্ব-স্ব গোত্রের আচার অনুষ্ঠানের সমন্বয়ে দ্বিতীয় শতকের দিকে বৃত্তের চট্টগ্রামের সংস্কৃতির লৌকিক আচার অনুষ্ঠানের প্রাথমিক রূপ লাভ করে। বিংশ শতাব্দীতে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার লাভ ও চর্চার ফলে এর কিছুটা শিথিল হলেও এখানকার লোকজীবন থেকে একে বারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। ধর্মীয় ইতিহাসে দেখা যায়, বিশাখার বিবাহের সময় তাঁর পিতা ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী প্রদত্ত দশটি উপদেশ বা বর: ১. ঘরের আগুন বাইরে নিও না ২. বাইরের আগুন ঘরে এনো না ৩. যে দেয় তাকে দেবে ৪. যে দেয় না তাকেও দেবে ৫. যে দেয় বা দেয় না তাকেও দেবে ৬. সুখে বসবে ৭. সুখে আহার করবে ৮. সুখে শয়ন করবে ৯. অত্রির বা সাধু সজ্জনের সেবা ১০. গৃহাগত দেবতার পূজা করবে।
তৎকালে প্রদেয় এসব উপদেশ কল্যাণময়। তবে বৌদ্ধ দৃষ্টিকোণ থেকে এ লৌকিক বিবাহ আচার অনুষ্ঠানের পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বৌদ্ধধর্ম বিবাহ প্রথার ঘোর বিবোধি ছিল। আর বিবাহ প্রথার সাথে যে যৌতুক প্রথা প্রচলিত আছে তা মূলত বৌদ্ধধর্মের অনুসারীদের নব বিধান থেকে সৃষ্টি হয়েছে। কেননা অন্যান্য ধর্মের বিধান মতে, নারীরা পিতা-মাতা বা আত্মীয়-স্বজনের ভূ-সম্পত্তির বা টাকা পয়সার কিছু অংশের অংশীদার হয়ে থাকে। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের বিধান ও নিয়ম অনুসারে নারীরা সমঅধিকার প্রাপ্ত হলেও বিবাহ প্রথায় নারীরা যেমন অবহেলিত তেমনি পিতামাতার সম্পত্তি ভোগের অংশীদার থেকেও বঞ্চিত। এর কারণে বৌদ্ধধর্মের অনুসারী মেয়েদের বিয়ে শাদিতে প্রচুর পরিমাণে যৌতুক প্রদান করতে হয় (সমাজে স্বীকৃত নয়)। কারণ তারা বিবাহিত হওয়ার পর পিতা-মাতার কোন অর্থ সম্পত্তির অংশীদার বা দাবিদার হতে পারে না। তাই দেখা যায় যৌতুক প্রথা বৌদ্ধধর্মেরই সৃষ্ট। বৌদ্ধধর্ম মতে, এ লৌকিক আচার অনুষ্ঠানের কোন বিধি-বিধান না থাকলেও যুগ যুগ ধরে এ বিবাহ ও যৌতুক প্রাথার লৌকিক আচার অনুষ্ঠান বৌদ্ধ সমাজে প্রচলিত হয়ে আসছে।
আবাহ-বিবাহ পরিণয় পদ্ধতি : ত্রিপিটক শাস্ত্রে পুত্রের বিবাহ পরিণয় প্রথাকে আবাহ আর কন্যার বিবাহ পরিণয় প্রথাকে বিবাহ বলে। বিবাহ সামাজিক জীবনের বৃহত্তর এবং জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান। বিবাহের আগে ছেলেকে একবার প্রব্রজ্যা ধর্মে দীা নিতে হয়। সচরাচর প্রথমেই বরের পে কন্যা নির্বাচন করে। পাত্রের যোগ্যতা অনুযায়ী পাত্রী নির্র্ধারণ গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বৌদ্ধরা সমরক্তের সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ বন্ধন থেকে বিরত থাকে। স্বগোত্র এবং স্ববংশের মধ্যে বিবাহ না হওয়া প্রতিষ্ঠিত সামাজিক রীতি। তবে মামাতো বোনকে অনেকে সিদ্ধার্থ গৌতমকে অনুসরণ করে এ প্রথায় বিয়ে করে থাকে। তাছাড়া পিসী, মাসী, পিসতুত ও মাসুতত বোনের সঙ্গে বিয়ে হয় মাঝে মাঝে। উভয় প ঠিকজী বা কোষ্ঠি বিচার করে ফোটক (প্রতিবন্ধকতা) আছে কিনা পরীা করে। এছাড়াও শারীরিক, মানসিক, চারিত্রিক, ধনী দরিদ্র বিচার করা হয়। জন্ম মাসে, জোড় মাসে, বর্ষাব্রত অধিষ্ঠানের সময়, পৌষ মাসে, চৈত্র মাসে, জ্যৈষ্ঠ মাসে, কার্তিক মাসে এবং মাতা পিতার মৃত্যুর এক বছরের মধ্যে বিয়ে হয় না। বিয়ে শাদী অনুষ্ঠান মাসের শুভাশুভ ধারণা। প্রবাদে প্রচলিত আছে-
ফাগুণের বিয়ে আগুন
চৈত্রের বিয়ে হারুগা
জেঠের বিয়ে হেট
কার্তিকের বিয়ে হাতি
পউষের বিয়ে পুষ্করা।২৯
বৈশাখ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ ও মাঘ এই সাতমাসে বিয়ে শাদী অনুষ্ঠিত হলে সে বউ স্বামী ও শ্বাশুর পরিবারের পে শুভ ও মঙ্গলজনক হয়। বিবাহ সাধারণত তিন রকমের (ক) বর গিয়ে কনের বাড়িতে বিয়ে করে আসাকে চলন্ত বিয়ে। (খ) কনেকে তার নিজ বাড়ী থেকে নিয়ে এসে বরের বাড়ীতে বিবাহ করা কে বলা হয় নামন্ত বিয়ে (গ) বর বিয়ে করে অপুত্রক শ্বাশুর বাড়ীতে চলে যাওয়াকে ঘরজামাই বিয়ে বলে। অনুষ্ঠান প্রস্তুতির সাথে সাথে চলে উৎসবের ঐতিহাসিক অহলা কেসেট বাজান, বিবাহের মন মাতানো সানাই, ঢোল বাদ্য, গান বাজনা ইত্যাদি। বিয়ে সম্পর্কীয় বাঙালি বড়–য়া বৌদ্ধরা যেসকল সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ও লোককর্মগুলো অনুসরণ করে থাকে তা সংপ্তি ভাবে তোলে ধরা হলো-
১) পাত্র-পাত্রী নির্বাচন ২) বউ জোড়লী বা অলংকার চড়ানী (৩) গদ গলানো (৪) লগ্ন আনা (৫) পানসল্লা (৬) বরের তেলোয়াইদেয়া বা তেল চড়ানী (৭) বর কনের সোহাগ ধরা (৮) বউ নামানী (৯) হাইচধরা (১০) কনের শ্বশুর বাড়ী যাত্রা (১১) গৃহদেবতা পূজা (১২) সিধা দেওয়া ১৩) ঢোলবিদ্যা ও অনুসরণসহ বিহারে গিয়ে বুদ্ধপূজা, প্রদীপ পূজা ও ত্রিরতœ বন্দনা ১৪) মঙ্গল সূত্র পাঠ (১৫) বিয়ে অনুষ্ঠান (১৬) বিয়ের মন্ত্র (১৭) সহমেলা (১৮) নব দম্পতি গোসল (১৯) নব দম্পতিকে গুরুজনের আশীর্বাদ গ্রহণ (২০) বেয়াই ভাতা (২১) মাটি হোঁড়ানী (২২) ভিুদের পিণ্ডদান (২৩) ছোয়াইং তোলা (২৪) বৌভাত খাওয়া (২৫) মাড়ি হোরানী (২৬) ন দিন্যা যাওয়া (২৭) ফিরাইন্যা ভাত (২৮) বারমাসে তের ফল বেয়ার (২৯) বেয়াই ভাতা (৩০) মঙ্গলঘট (৩১) কলসির জল ভরান (৩২) বরকলা (৩৩) বরকনের গায়ে হলুদ স্নান (৩৪) ঘাটা ঘরা (৩৫) পানমিটা (৩৬) বরসজ্জা, কনে সজ্জা (৩৭) ডুলিধরা (৩৮) নতুন বধুকে ভাত তরকারী ও ধান দেখানো (৩৯) বর বধুর ফুল শয্যা (৪০) নতুন জামাইর সালামী (৪১) বউ দেখা (৪২) রং ও ফুট খেলা (৪৩) ঢোলবাদ্য, মাইক, সানাই বাজনা (৪৪) বর কনের পিতা মাতার অনুমতি (৪৫) স্ত্রী পুরুষ স্বগ্রামী ও ভিন্ন গ্রামীদেরকের সান্ধ্য ভোজ (৪৬) যৌতুক প্রথা ৩০ (৪৭) বিবাহ আসরে মন্ত্রপাঠ ইত্যাদি ইত্যাদি।
এবার বিবাহের দুটি ঐতিহাসিক বিশেষ উপকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হলো-
মঙ্গলঘট : বাংলাদেশে বৌদ্ধ সমাজে মঙ্গলঘাট প্রথা প্রচলিত আছে। বাড়ির প্রবেশ পথে শুভ লণের প্রতীক মঙ্গলঘট স্থাপন করা হয়। বাড়ীর প্রবেশ পথে দু পাশে দুটি কলাগাছ পুতে তার উপর বা গোড়ায় জলপূর্ণ কলসী স্থাপন করত মুখে দুটি আম্রপল্লব, অশ্বথ, বাঁশ মুরাজী, বৈইল, মধুবাঁশের পাতা এবং কলা গাছের ডিক দিলে মঙ্গলঘট হয়। কোন কোন েেত্র দুটি ডাবও দেওয়া হয়। সপ্তদশ শতকের কবি মোহাম্মদ রফিক উদ্দীন বিরচিত জবল মুল্লক মনোরস কাব্যে তার উল্লেখ পাওয়া যায়-
‘কুম্ভ দুই জল ভরি পন্থ দুইপাশে
আম্রজল দিয়া তাতে রাখিছে হরিষে।’
বরণকুলা : বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিয়ে বা শুভ কাজে মাঙ্গলিক প্রতীক রূপে বরণ কুলা বা ডালা দেওয়া বহুল প্রচলিত আছে।৩১ এ প্রথা হিন্দু-মুসলিম সমাজেও প্রচলিত আছে। বৌদ্ধদের বরণ কুলার উপাদানের তালিকা নিন্মে প্রদত্ত হলো-
ক্র.ম উপকরণ বা দ্রব্য নাম পরিমাণ উপাদানের প্রতীক ধারণা
১. নতুন কুলা: ১ টি কল্যাণ ও শান্তির প্রতীক।
২. সাইল ধান:৫ পোয়া খাদ্য মানুষের জীবন ধারণ ও ধন সম্পদ লাভের প্রতীক।
৩. দূর্বাঘাস:১ গুচ্ছ বংশধারা বৃদ্ধির প্রতীক।
৪. কাঁচা কলা : ৫ টি সবুজ ফল, সুস্বাস্থ্য ও নিরাময় জীবনধারার প্রতীক।
৫. কাঁচা হলুদ: ২/৩ টুকরা,সৌন্দর্যের প্রতীক।
৬. শিলা: (ছোট পাথর) ১ টুকরা,শৌর্য-বীর্যের প্রতীক।
৭. ঘিলা:১ টি দৃঢ়তা ও গাম্ভীর্যের প্রতীক।
৮. সরিয়া তেলের মাটি সেজ দীপ: ১ টি আলো অন্ধকার দূরীভূত করে। জ্ঞানের বা আশার প্রতীক।
৯. পরিপূর্ণ মাটির কত্তি: ১ টি পানির অপর নাম জীবন।
১০. অশ্বথ পাতা:১ টি,সবুজ পাতা মানুষের জীবনের চির তারুণ্য ও দীর্ঘায়ুর প্রতীক।
১১. আম্রপল্লব:১ গুচ্ছ
১২. বাঁশ পাতা:১ গুচ্ছ
১৩. মুরাজী পাতা:১ থোকা
১৪. বৈইল পাতা:১ থোকা
১৫. কলা গাছের কচি ডিক:১ টি
সমাজ প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি বৌদ্ধদের বিবাহ পদ্ধতিরও অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। সমাজে ছেলে মেয়েরা আধুনিক শিায় শিতি হচ্ছে। বৌদ্ধদের মধ্যে বিবাহে যৌতুক প্রথা প্রচলিত থাকলেও তবে সামাজিক দায়বদ্ধতা নেই। তবে বর্তমান বৌদ্ধ সমাজে ছেলে মেয়েদের ধর্মান্তর বিষয়টি অতীব প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়ে। স্বধর্মে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিসর্জন দিয়ে পরধর্ম সংস্কৃতি গ্রহণ করছে। এ অশুভ প্রভাব ও সংস্কৃতিকে রোধ করতে হবে। বাঙালি বড়ুয়া বৌদ্ধ সমাজে বিধবা-বিবাহ, বিবাহ বন্ধনছিন্ন, সধবার পুনর্বিবাহ এবং স্থল বিশেষে বিবাহ বিচ্ছেদ প্রচলিত আছে। পুনর্বিবাহ ইচ্ছুক বিধবাকে প্রথমত: একটি কলাগাছের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার পর যথারীতি বরের হাতে সম্প্রদান করা হয়। এ প্রথা অনেক জাতিতেই আছে।
পরিত্রাণ দেশনা : বাঙালি বৌদ্ধরা পরিত্রাণ সূত্রপাঠ একটি পবিত্র অনুষ্ঠান বলে সম্পাদন করে থাকে। থেরবাদী বৌদ্ধদের কাছে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় কার্য। বৌদ্ধরা রতন সূত্র, মৈত্রী সূত্র, মঙ্গল সূত্র, করণীয় মৈত্রী সূত্র, পরাভব সূত্র, বোধ্যঙ্গ সূত্র, আটানটিয় পরিত্ত, মোর পরিত্ত, খন্ধ পরিত্ত প্রভৃতি সূত্রপাঠ করেন। এ পরিত্ত সূত্র সম্পর্কে ড. বেণীমাধব বড়ুয়া বলেন, ‘যখন কালক্রমে বৌদ্ধ গৃহস্থ সমাজ গঠিত হয় সেই সময় হতে প্রচলিত হিন্দু বা আর্য গুহ্যমন্ত্রের অনুকরণে পালি ও মিশ্রিত ভাষায় বৌদ্ধ পরিত্রাণ সূত্রের রচনা আরম্ভ হয়। বৌদ্ধ সাহিত্যে পরিত্রাণ সূত্রের উদ্ভব ও লৌকিক বৌদ্ধধর্মের অঙ্গ। এ সূত্রের দুটি দিক আছে- লৌকিক বা জাগতিক এবং লোকোত্তর বা পারমার্থিক। লৌকিক হলেও কালে কালে এ সূত্র পাঠের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ সাধিত হয় বলে এ ব্যাপক পরিচিতি লোকমুখে আছে। পালি পরিত্ত শব্দের অর্থ পরিত্রাণ, সংরণ বা নিরাপত্তা। বৌদ্ধ ভিুরা পরিত্ত সূত্রপাঠ করে থাকে।
শব সৎকার ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া : জন্মিলে মরিতে হবে। মৃত্যু ধ্রুব সত্য। মৃত্যু সকলকে আলিঙ্গন করতে হয়। বৌদ্ধদের সামাজিক কর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ চিরাচরিত প্রথা হলো শব সৎকার ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। সমাজে কোন মানুষের মৃত্যু হলে শবদেহ হলুদ ও সাবান দিয়ে উত্তম রূপে ম্লান করে নেওয়া হয়। তার পর নববস্ত্র পরিধান করে সুগন্ধ, পুষ্প ও গন্ধ দ্রব্যাদি দিয়ে শবকে শুচি পবিত্র করে উন্মুক্ত খাটে কিংবা উন্নত শয্যায় সজ্জিত করা হয়।
শবদেহ শ্মশানে নেওয়ার সময় ভিক্ষুসংঘের নিকট সকরে বসে ত্রিশরণ ও পঞ্চশীলাদি গ্রহণ করে অনিত্যতা বিষয়ক পালি সূত্র শ্রবণ করেন। মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ভিক্ষু সংঘ বলেন, ‘ইমং মতকাবত্তং ভিক্খুসঙ্ঘস্স দেথা।’ এ মন্ত্র তিনবার পাঠ করে সংঘদান করা হয়। ভিক্ষুগণ নিন্মোক্ত অনিত্য গাথা দেশনা করে থাকেন- ‘অনিচ্চা বত সংখারা উপ্পদাবযধম্মিনো, উপ্পজিত্বা নিরুজ্ঝন্তি তেসং বুপসমো সুখো। সব্বে সত্তা মরিন্তী চ মরিংসু চ মরিস্সরে, তাতে ওযহাং মরিস্সামি নত্থি মে সংসযো।’৩২ মৃতদেহকে বাঁশ বা কাঠ দিয়ে আলং বা শবাধার দিয়ে কীর্তন মাইক বাজনা, বাজি পোড়ান এবং আনন্দ উল্লাস করে শ্মশান খোলায় নিয়ে যাওয়া হয়। বৌদ্ধরা বয়স্ক ব্যক্তি নারীর শবকে দাহ (আগুনে পুড়ানো) করা এবং শিশুদের কবর দিয়ে থাকে। দাহ করার সময় চিতাতে সাতবার প্রদণি করে সাতবার অগ্নি সংযোগ করার পর অন্যান্যরা তাতে অংশ নেয়। বৌদ্ধদের শ্মশানে (দ্বিতীয়) নারীরা যেতে পারে না। মৃত ব্যক্তির জন্য শোক বা কান্না করার রীতি বৌদ্ধ বিধানে নেই। অন্ত্যেষ্টির সপ্তাহের দিন শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হয়। বৌদ্ধরা পুদ্গলিক দান কিংবা সংঘদান কিংবা অষ্টপরিষ্কার দান করে থাকে। ভিু-শ্রামনকে দান দিয়ে যথা সাধ্য লোকজনকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হয়। ঐ দিন হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক দিন সূর্যাস্তের পর ভিক্ষু বা ভিক্ষুসংঘ মৃতের বাড়িতে এসে মঙ্গলসূত্র পাঠ করেন। এই অনুষ্ঠানের নাম ‘ফারিক শ্রবণ’ বাড়ীর চারিদিকে ফারিক সূতা দেওয়া হয়।৩৩
সাপ্তাহিক শ্রাদ্ধের পর হতে প্রথম বছর প্রতিমাসেই ভিু বা সংঘকে খাদ্য ভোজ্য ও দান দণিাসহ অনুরূপ দান দেওয়া হয়। সাধারণত অশুভ তিথি নত্রের দিনে পরলোক গত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ষম্মাসিক ও বার্ষিক শ্রাদ্ধার ছোয়াই দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে।
পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের পূজা পার্বণ ও লোকবিশ্বাস এবং লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান
প্রাচীন বঙ্গে বসবাসকারী পাহাড়ী উপজাতিদের মধ্যে ধর্ম পূজার বিধান আছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অভিমত, ধর্মপূজা বৌদ্ধধর্মের শেষ পরিণতি। অনার্য জাতি বিশেষের মধ্যে প্রচলিত ধর্মপূজার প্রাচীন অনুষ্ঠান হতে ধর্মপূজার উদ্ভব হয়েছে। কারো কারো মতে উন্নত আর্য সংস্কৃতি হতে এর উৎপত্তি। এই অনুষ্ঠানকে চাকমা ভাষায় ধর্মকাম বলে। এর অন্য নাম সিদ্ধিপূজা, জাদি পূজা। উপজাতি সম্প্রদায়ের আনুষ্ঠানিক সকল পূজার মধ্যে এটি অন্যতম পূজা। মহাসমারোহে এ পূজা সম্পন্ন করেন। ইহার অনুষ্ঠান ঐহিত্য ও পারত্রিক মঙ্গলের কারন বলে লোকের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। অনেকে বিপদে পতিত হলে ইহা মানত করত। বর্তমানে আদিবাসী সমাজে আধুনিক শিার বিস্তারে ধর্মপূজার বিশ্বাস শিথিল হয়েছে। শ্রদ্ধাবান গৃহী সমস্ত গৃহদ্বার পরিষ্কার করে সস্ত্রীক স্রাতশুচি হয়ে পূর্বাহ্নে আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করেন এবং বৌদ্ধ ভিুগণকে আহবান করেন। বুদ্ধমূর্তির সামনে পূজা অর্পণ করে, বৈকালে ধুপ, দীপ, পুষ্প প্রভৃতি দ্বারা ঘন্টাধ্বনি সহকারে বুদ্ধের বন্দনা/অর্চনা করেন। এ সময় বিকৃত পালি ভাষার লিখিত চাকমা বৌদ্ধ শাস্ত্র ‘সাহস পুলুতারা’ এবং ‘মালেমতারা’ পাঠ করা হয়। (মৎ প্রণীত ‘চাকমা জাতির ইতিহাস’ (পৃ-৫৪) এবং সতীশ চন্দ্র ঘোষ প্রণীত ‘চাকমা জাতি’ (পৃ. ২০০)। প্রাচীন কুসংস্কার থাকলে ধর্মকাম, ধর্মঠাকুরের পূজা নয়, এতে বুদ্ধপূজা, দশ পারমিতা প্রার্থনা, ধর্মপদের বাণী এবং সাইত্রিশ প্রকার পায়ি ধর্মলোচনার প্রতীক।”৩৪
বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের নানামাত্রিক ভৌগোলিক, নৈসর্গিক ও নৃতাত্ত্বিক স্বজাত বৈশিষ্ট্যগুলো অন্যতম হলো এ অঞ্চলের ভাষাগত বৈচিত্র্য। পার্বত্য চট্টগ্রামেও বেসরকারি পর্যায়ে নানা ভাষা কেন্দ্রিক উদ্যোগ আয়োজন চলছে। বান্দরবানের উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনসটিটিউট সেখানকার বৈচিত্র্যমণ্ডিত ভাষা ঐতিহ্যের অধিকারী ক্ষুদ্র জাতিগুলো মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন প্রকাশ করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসি জনগোষ্ঠিগুলোর বর্ণমালাগত সমস্যা এখন খুব একটা নেই। প্রায় সব’কটি জনগোষ্ঠির হরফ বা বর্ণমালা সম্প্রতি কম্পিউটারের আওতায় এসেছে। যেমন: চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যাদের Aujhaapaat, মারমা ও চাকদের Myanmar বম, খুমি ও লুসাইদের Roman ম্রোদের Mruchow,, ত্রিপুরাদের Bijoy-sutonny প্রভৃতি ফ্রন্টে মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজও ইদানিং এগিয়ে চলেছে। এখন সেই লিপিগুলোর ব্যাপকচর্চা ও উন্নয়ন দরকার।
চীনা তিব্বতি (Sino –Tibetan) ভাষা গোষ্ঠিকে কেউ কেউ ভোট চীনীয় গোষ্ঠি বলেন। চাকমারা মঙ্গোলীয় গোষ্ঠির লোক হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য মঙ্গোলীয় গোষ্ঠিভূক্ত উপজাতিদের ভাষার মত তাদের ভাষা টিবটো বার্মান (Tibeto-Burman) বা সিনে টিবেটান (Sono-Tibetan) নয়। চাকমা ভাষা ইন্দো ইউরোপীয়ান ভাষাগোষ্ঠির অন্তর্গত একটি ভাষা। ইন্দো (ইউরোপীয়) এবং এরিয়ান (ভারতীয় ও ইরানীয় ভাষার ভিত্তিতে); এটি বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষার নিকটবর্তী একটি ভাষা।৩৫ চাকমা হরফে লিখিত পাণ্ডুলিপি গুলোর মধ্যে, তাহলিক শাস্ত্র, শাঙ্চে ফুলু তারা, আঘরতারা, রাধামন, বৌদ্ধ রঞ্জিকা, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।
১৮৫৬ সালের পূর্বে চাকমা এবং বড়–য়া সম্প্রদায় তান্ত্রিক মহাযানী বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী ছিল। উল্লেখ্য মহাযানী তান্ত্রিক বৌদ্ধরা যেমন ভগবান বুদ্ধকে আরাধনা করতেন, তেমনি তারা হিন্দুদের দেব দেবীকেও পূজা করত। সেজন্য তখন চাকমা এবং বড়ুয়ারা হিন্দুদের অনেক দেব দেবী, যেমন : স্বরস্বতী, লক্ষ্মী, কালী দেবীর পূজা করত। ১৮৫৬ সালে আরাকান হতে থেরবাদী বৌদ্ধ সারমেধ মহাথেরো চট্টগ্রামে আসেন এবং রাঙ্গুনিয়া রাজানগরে রাজ দরবারে আসেন। কালিন্দী রাণি তাঁর ধর্মোপদেশ শ্রবণ করে অভিভূত হন এবং থেরবাদী মতবাদে দীতি হন। এরপর রাণির প্রজা অনেক বড়–য়া এবং চাকমা থেরবাদী মতবাদে দীতি হন। তখন মহাযানী ভিুদের বলা হত রুলি বা রাউলি এবং টাউর বা ঠাকুর। তারা সংসারী ছিলেন। ১৮৬৪ সাল ৭ জন মহাযানী রউলী সারমেধ মহাথেরের নিকট সর্বপ্রথম থেরবাদ সম্মত উপস্পদা গ্রহণ করেন। কিভাবে চট্টগ্রামে থেরবাদ মতবাদ প্রচার শুরু হয় এবং ক্রমে ক্রমে বিস্তার লাভ করে। এখন চাকমা বড়–য়া এবং সারা বাংলাদেশে বৌদ্ধ সমাজ থেরবাদ মতবাদে বিশ্বাসী। তবে এখনও নাকি পার্বত্য চট্টগ্রামের অত্যন্ত প্রত্যন্ত অঞ্চলে মহাযানী বা রুলি ভিু দেখা যায়। কালিন্দী রানী তাঁর রাজধানী রাজানগরে (বর্তমান রাঙ্গুনীয়া থানার কিছু দূরে) একটি বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা করে তার নাম রাখেন শাক্যমুনি বিহার। তিনি বার্মা থেকে মহামুনি নামের একটি বুদ্ধমূর্তি এনে মন্দিরে স্থাপন করেন। একই ভাবে মং চীফ বর্তমান রাউজান থানার একটি বৃহৎ এবং সমৃদ্ধ প্রাচীন বড়ুয়া গ্রাম পাহাড়তলীতে একটি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করান এবং সেই বিহারে বার্মা থেকে এনে মহামুনি নামের বুদ্ধমূর্তি স্থাপন করেন। এখন গ্রামটির নামই পরিবর্তিত হয়ে মহামুনী পাহাড়তলী নামে পরিচিতি লাভ করে।৩৬
ব্রিটিশ আমলে উভয় বিহার প্রাঙ্গণে চৈত্র সংক্রান্তি অর্থাৎ চাকমাদের বিজু/বিঝু উৎসবের সময় একমাস ব্যাপী বৌদ্ধ মেলা বসত তবে উভয় স্থানে প্রথম ৩ দিন মেলাটি কেবল মাত্র উপজাতি বৌদ্ধদের জন্য নির্ধারিত ছিল। মেলায় আইন শৃঙ্খলা রা করত পার্বত্য চট্টগ্রামের পুলিশ। ৩ দিন পরে পার্বত্য চট্টগ্রামের পুলিশ চলে গেলে মেলা সবার জন্য উন্মক্ত থাকত। তখন চট্টগ্রাম জেলার পুলিশ আইন শৃঙ্খলার দায়িত্বে নিয়োজিত পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ উপজাতি নারী পুুরুষ যুবক যুবতী অংশগ্রহণ করতেন। পাকিস্তান হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম পুলিশ বাহিনীকে অবলুপ্ত করে দেয়া হয় এবং মেলায় আইনশৃঙ্খলা রায় দায়িত্ব দেয় চট্টগ্রাম জেলার পুলিশ বাহিনীকে। এরপর পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি বৌদ্ধরা মেলায় আগের মত নিরাপদ বোধ করত না। ক্রমে ক্রমে আইন শৃঙ্খলাও শিথিল হতে থাকে। উপজাতিরা বিশেষ করে মেয়েরা নানাভাবে হয়রানি হতে থাকে এবং মেলায় বাঙালি-উপজাতির মধ্যে দাঙ্গা বিবাদ হয় এবং শেষ পর্যন্ত ষাটের দশকে বন্ধ হয়ে যায়।
ব্রিটিশ আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে সব স্থানে বড় বড় বৌদ্ধ বিহার ছিল, সে সব স্থানে মাঘী পূর্ণিমা, ফাল্গুনী পূর্ণিমা, বৈশাখী পূর্ণিমা এবং চৈত্র সংক্রান্তি অর্থাৎ বিজুর সময় কমপে ৩ দিন হতে একমাস ব্যাপী বৌদ্ধ মেলা বসত। তখন ধর্মকর্ম করতে, যাত্রা অনুষ্ঠান দেখতে হাজার হাজার মানুষ মেলায় যেত। চট্টগ্রাম হতে বহু ব্যবসায়ী পণ্য সামগ্রী নিয়ে মেলায় দোকান খুলত। ১৯৭২ সাল ফাল্গুনি পূর্ণিমার সময় খাগড়াছড়ি বাজারে প্রায় শত বছরের প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরে শেষ বার বৌদ্ধ মেলার আয়োজন করা হয়। ঐ এক বছরের চৈত্র সংক্রান্তি উপলে রামগড় মহামুনি বৌদ্ধ বিহারে শেষ বার মেলার আয়োজন করা হয়। ষাটের দশকের প্রথম দিকে কর্ণফুলী প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শেষ হলে কাপ্তাই হ্রদে কয়েকটি বৌদ্ধ বিহার ডুবে যায়। তখন ঐ সব বিহারে মেলা বন্ধ হয়ে যায়।
আগেই বলা হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামে ৩ জন সার্কেল চীফ বা রাজা আছেন। তিন রাজাই তাদের জুম খাজনা আদায় উপলে প্রতিবছর আগস্টের পৌষ মাসে পূর্ণিমার সময় তাদের রাজবাড়ী প্রাঙ্গণে পুণ্যাহর আয়োজন করতেন। তখন প্রত্যেক সার্কেলের হেডম্যানগণ তাদের আদায়কৃত জুমের খাজনা একটি বাৎসরিক অনুষ্ঠানে রাজার কাছে জমা দিতেন। সেই অনুষ্ঠানকেই পুন্যাহ বলা হয়। সেই উপলে নাচ, গান, যাত্রা, ঘোড়দৌড় এবং অন্যান্য বিনোদনের আয়োজন করা হত। ৩ দিন বা সপ্তাহ খানেকের জন্য মেলা বসত। সেই উপলে চট্টগ্রাম হতে অনেক ব্যবসায়ী দোকানদার তাদের বিভিন্ন মালামাল নিয়ে ছোট ছোট অস্থায়ী দোকান খুলে বসত। পুন্যাহ শেষে মেলা হতে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় মালামাল ক্রয় করে বাড়ীতে চলে যেতেন। বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলায় এখনও কম বেশি জুম চাষ রয়েছে। তাই মাঝে মধ্যে অনিয়মিত হলেও ঐতিহ্যবাহী রাজাপুণ্যাহ অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। বৌদ্ধ মেলা বা রাজাপুন্যাহ না থাকলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধরা এখন চীবর দান অনুষ্ঠান করে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বৌদ্ধ ভিুদের চীবর দানানুষ্ঠান করা হয়। সেটা সাধারণ ভাবে কঠিন চীবর দান হিসাবে পরিচিত। প্রত্যেক বৌদ্ধ বিহারে যেখানে ভিক্ষুরা বর্ষাবাস করেন, কেবল সেই মন্দিরে চীবর দান অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।
ইতিহাসে দেখা যায়, এয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত বৌদ্ধ ধর্মীবলম্বীগণ নামে মাত্র বৌদ্ধ ছিলেন। ধর্মীয় কুসংস্কার, নানা মিথ্যাদৃষ্টি, লৌকিক ক্রিয়াকর্ম, প্রকৃতি পূজা, লোকবিশ্বাস এবং অবৌদ্ধোচিত ধর্মীয় কার্যক্রম ছিল অত্যন্ত প্রবল, ভিুদের মত মুণ্ডিত মস্তক পুরোহিত নামে এক শ্রেণির ধর্মীয় গুরু ছিলেন তারা সংসার জীবন যাপন, চাষাবাদ করতেন আবার ধর্মীয় কার্যাদিও পরিচালনা করতেন। কেউ কেউ একে লুরি বা লাউরী বলতেন। এরা ধর্ম বিনয় নীতিতে ছিলেন অজ্ঞ। রাউলীরা ধর্ম বিনয় প্রশিণ ও শিার অভাবে পার্বত্য বৌদ্ধ সমাজে নেমে এসেছে অবিদ্যা অন্ধকার। তারা ধর্মীয় কাজে ‘আগরতারা’ নামক গ্রন্থ থেকে তন্ত্র-মন্ত্র পাঠ করতেন।
অধ্যাপক দিলীপ কুমার বড়ুয়া লিখেছেন, মিথ্যাদৃষ্টিতে আচ্ছন্ন হয়ে আদিবাসীরা বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা অচর্না, থানমান, দানপাং পূজা, ধুবলাপূজা, গাংপূজা, গ্রাম রাপূজা, বৃপূজা, কালীপূজা, লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতী পূজা, দুর্গা-শিবপূজা, হোইয়া পূজা এমন কি প্রকৃতির পূজাও করতো। আর কখনো কখনো মগধেশ্বরী ও চট্টেশ্বরীর পূজা ছিল তাদের নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম। এসব পূজা পার্বণে ভুত-দেবতা সন্তোষ সাধনে পশুবলির প্রচলনও ছিল। রাউলীদের পাশাপাশি ওঝা-বৈদ্যের প্রভাবও পরিলতি হয়। আদিবাসী উপজাতিদের চিকিৎসা শাস্ত্র লৌকিক পন্থা হলেও বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা ও লোকাচারে বহুল প্রচলিত আছে।৩৭
পার্বত্য চট্টগ্রাম এমনকি বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার প্রসার, পুনরুত্থান, সংরণ ও সংস্কারে চাকমা রাজবংশের আবদান অপরিসীম। এতে বিশেষ করে চাকমা রাজা ধরমবক্স খাঁর প্রধানা মহিষী বিদে্যুৎসাহী, পুণ্যশীলা মহিয়সী কালিন্দীরাণীর (১৮৪৪-৭৩) নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। বাংলায় বৌদ্ধধর্ম পুনর্জাগরণে মহান সাংঘিক ও প্রথম সংঘরাজ চকরিয়া হারবাং এর সারমেধ মহাস্থবির ও বৌদ্ধ সমিতির প্রতিষ্ঠা সভাপতি গুণমেজো মহাস্থবিরের সাথে কালিন্দী রাণির সাক্ষাৎ হয়। তখন সারমেধ মহাস্থবিরের কাছে বুদ্ধের জীবন ও দর্শনের-উপর তাৎপর্যপূর্ণ দেশনা শুনে উদ্বুদ্ধ হন। তখন তিনি তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম থেকে পরিবর্তত হয়ে থেরবাদ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৮৫৭ সালে রাজ পুন্যাহ উপলে সারমেধ মহাথেরকে স্মারক ও সম্মাননা প্রদান করেন।৩৮ সদ্ধর্ম হিতৈষীণী রাণি কালিন্দী ১৮৬৬ সালে রাজধানী রাজানগরে শাক্যমুনি বৌদ্ধ বিহার, ১৮৭০ সালে ভিক্ষুসীমা (চিং বা গেং), ১৮৫৭ সালে বুদ্ধের জীবনী সমন্বিত ফুলচন্দ্র বড়ুয়ার ‘বৌদ্ধ রঞ্জিকা’ পুস্তক প্রকাশ করে প্রচার করেন।
পরবর্তীতে চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়ের আহবানে রেঙ্গুন হতে অগ্রবংশ মহাথের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে পার্বত্য চট্টগ্রামে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম থেকে প্রকৃত ধর্ম বিনয় শিাদর্শ প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথের পার্বত্যবাসীকে ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রব্রজ্যা প্রদান করেন আদিবাসী যুবকদের। প্রতিষ্ঠা করেন পার্বত্য বৌদ্ধ ভিু সমিতি ও গ্রামে গ্রামে বৌদ্ধ বিহার, প্রতিটি বৌদ্ধ বিহারে ভিুসংঘের মাধ্যমে প্রচলন করেন ত্রিরত্ন বন্দনা, শীলগ্রহণ, বুদ্ধপূজা, সংঘপূজা, সীবলীপূজা, সংঘদান, অষ্টপরিস্কার দান, চীবর দান ইত্যাদি। এছাড়াও বুদ্ধপূর্ণিমা, আষাঢ়ী পূর্ণিমা, মধূপূর্ণিমা, প্রবারণা পূর্ণিমায় পঞ্চশীল ও অষ্টশীল ব্রতপালন ইত্যাদি। এভাবে পার্বত্যবাসী বৌদ্ধদের মধ্যে ধর্মের জাগরণ এবং সমাজ সংস্কার সূচিত হয়েছিল।
নবকুমার তনচঙ্গ্যা উল্লেখ করেছেন, ‘সে সময় চাকমা ও তনচঙ্গ্যা সম্প্রদায়ের কোন ভিু নাই বললেও চলে। মারমা ও বড়ুয়া সম্প্রদায়ের ভিুরা পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহারে ধর্মীয় গুরু হিসেবে অবস্থান করতেন। …. পর্যায় ক্রমে মারমা, চাকমা ও তনচঙ্গ্যা সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে শ্রামণ্য ও ভিুধর্মে দীতি হয়ে ধর্মবাণী প্রচারে ভূমিকা রাখেন।৩৯
বর্তমান সময়ে পার্বত্য বৌদ্ধদের শিক্ষা-দীক্ষা ও অগ্রগতিতে শ্রীমৎ মোঙ্কর মহাস্থবির, শ্রীমৎ আর্যনন্দ মহাস্থবির, শ্রীমৎ শান্তজ্যোতি মহাস্থবির, শ্রীমৎ ধর্মপ্রিয় মহাস্থবির, রাজগুরু অগ্রবংশ মহাস্থবির, জ্ঞানশ্রী মহাস্থবির, আর্যশ্রাবক সাধনানন্দ মহাথের, সুমনালঙ্কার মহাস্থবির, প্রজ্ঞানন্দ মহাথের, উপঞ্ঞা জোত থের, গিরিমানন্দ ভিক্ষু, স্মৃতিমিত্র থের, শীলানন্দ থের প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫৭ সালে পালি ভাষা-সাহিত্য ও ধর্মীয় শিার জন্য চাকমা রাজ বিহারে পালি টোল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। পার্বত্যবাসী বৌদ্ধদের মধ্যে ধর্মীয় কুসংস্কার ও অজ্ঞতা দূর করার জন্য পাহাড়ের নির্জন অরণ্যে বহু বিহার, চৈত্য, ধ্যানকুটির, ধর্মীয় পুস্তক, ত্রিপিটক গ্রন্থ প্রকাশ, পালি কলেজ ও মেডিকেল প্রতিষ্ঠা করেন।
ধর্মবিশ্বাস : চাকমারা প্রধানত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তবে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে কিছু সংখ্যক চাকমা খৃষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত হন। জানা যায় যে, অনেক দরিদ্র চাকমা রোববার দিন পাদ্রিদের কাছ হতে বিবিধ দ্রব্যাদি পাবার জন্য চার্চে সমবেত হত। আবার বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে রাজনৈতিক সহিংসহতায় কেহ কেহ বাধ্য হয়ে ইসলাম ধর্মে দীতি হন। তবে উভয়ের সংখ্যা খুবই নগণ্য। অতীতে চাকমাদের বৌদ্ধধর্ম চেতনাবোধ লুরিরা রা করেছিলেন। অতীতে চাকমারা বৌদ্ধধর্মের অনুসারী হলেও তাদের মধ্যে হিন্দু ধর্মের প্রভাব ল্যণীয়। চাকমাদের বিভিন্ন রাজা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। স্বয়ং রাণী কালিন্দিও প্রথম দিকে হিন্দু ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন বলে জানা যায়। ফলে রাজার ধর্মই চাকমা জাতির ধর্ম বলে বিবেচিত হয়ে এসেছে।
ব্রহ্মদেশে অবস্থানকালে চাকমারা বাংলায় সংস্পর্শে এসে পুরোপুরি বৌদ্ধধর্ম অনুসরণ করতো না বলে জানা যায়। পার্বত্য আদিবাসীরা বাহ্যিক যে আচার-অনুষ্ঠানগুলি পালন করতেন আসলে সেগুলো তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম প্রভাবে। চাকমা রাণি কালিন্দি আরাকান হতে সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবির ও চকরিয়া হারবাং এর গুণমেজো মহাস্থবিরসহ প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ভিুগণকে আমন্ত্রণ করে রাজধানী রাজানগরে মহামুনি বৌদ্ধ বিহার স্থাপন করেন। তিনি সে সময়ে থাধুথং নামক বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ পঞ্জিকা নামে অনুবাদ করে প্রচারের ব্যবস্থা করেন। অন্যদিকে বড়–য়া বৌদ্ধগণও চাকমাদের বৌদ্ধধর্ম লালনে উৎসাহ যুগিয়ে চলেন। পাকিস্তান আমলে ইসলাম ধর্মের আগ্রাসন বেড়ে গেলে চাকমা সমাজ প্রতিটি গ্রামে বৌদ্ধ বিহার নির্মাণে উদ্যোগী হয়। কিন্তু প্রয়োজনীয় নীতিবান ভিু তখন খুঁজে পাওয়া মুশকিল হয়ে পড়ে। মারমা ও বড়–য়া ভিুরা এসব বিহার বা ক্যাংএ বিহারাধ্য রূপে বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসার ঘটান চাকমা রাজ পরিবারের এেেত্র বিশেষ অবদান রয়েছে। চাকমা রাজা নিজেই রাজ বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। রাঙ্গামাটিতে গড়ে উঠে রাজবন বিহার। চাকমা রাজা ভূমি দান করে রাজবাড়ির উত্তর পার্শ্বের সমতল পাহাড়ে এই বিহার স্থাপন করেন। এই রাজ বন বিহারের অধ্য হলেন বনভন্তে। মুখ্যত চাকমাদের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণ ঘটে বনভন্তের (শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাথেরো) মাধ্যমে। বনভন্তের গৃহস্থ জীবনের নাম ছিল রথীন্দ্র। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম সহ গোটা বিশ্বের বৌদ্ধ ধর্মালম্বীদের কাছে অতিশয় পূজনীয় একজন ভিু। অনুত্তর ভিু সংঘ ত্রে ও স্বধর্মপ্রাণ দায়ক দায়িকাগণ মনে করেন যে তিনি অর্হৎ লাভ করেছেন। তাই তিনি শ্রাবক বুদ্ধরূপে সকলের কাছে পূজনীয়।
পূজা অর্চনা : চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও তারা নিজস্ব কতকগুলি পূজা-অর্চনা করে থাকে। এসব পূজার মধ্যে ভাতদ্যা অন্যতম। যা পূর্ব পুরুষের উদ্দেশ্যে অন্নদান করা বুঝায়। মাথা ধোয়া হলো আরেকটি পূজা যার মাধ্যমে কোন পরিবার পবিত্র হয়ে উঠে। অনেক সময় কোন গোজার লোক বাঘের কামড়ে মারা পড়লে তখন সে গোজার লোকেরা মিলে মাথা ধোয়া পূজা করে। মা লক্ষ্মীমা পূজা করা হয় নতুন ধান খাওয়ার আগে। ভাত ঝরা পূজা দেওয়া হয় সন্তানের অসুখ হতে আরোগ্য লাভ কামনা করার উদ্দেশ্যে। জুমের দোষ নিরসনের জন্য পূজা দেওয়া হয়। এটাকে ধুজ মারা পূজা বা জুম মারানো বলে।
গ্রামবাসীর মঙ্গলের জন্য সবাই মিলে থানমানা করা হয়। থানমানার সময়ে মা গঙ্গা বা গাঙ পূজা করা হয়। এ পূজা দেয়ার সময় একজন ওঝা পৌরহিত্য করেন। সাধারণত অগ্রহায়ণ মাসে থানমানা করা হয়। থানমানার সময়ে গ্রামবাসীরা সামর্থ্য অনুসারে চাল, শুকর, অন্যান্য দ্রব্যাদি ও নগদ টাকা দেয়। এ সকল আয়োজন করে সবাই মিলে আহার করেন। তখন বিভিন্ন ধরণের আলাপ আলোচনাও চলে। বিশেষ করে কে কত আড়ি জুম কাটবে, কোথায় কোন জায়গায় কে জুম কাটবে এসব নির্ধারিত হয় থানমানার আলোচনায়। যাদের বাড়তি বীজ ধান থাকে এবং যাদের বীজধানের ঘাটতি থাকে তখন সেখানে তার ভাগাভাগি বা সমাধা করা হয়। চাকমাদের আরেকটি পূজা হলো আদাম বন। বন মানে ‘নিষেধ’, কোন গ্রামে বা পার্শ্ববর্তী গ্রামে সংক্রামক ব্যাধি যেমন কলেরা ও বসন্ত দেখা দিলে আদাম বন করা হয়। একজন বৈদ্য গ্রামের প্রবেশ ও বাহির পথে বাঁশের চিহ্ন টাঙিয়ে দিয়ে আদাম বা গ্রাম বন করে। আদাম বন করার প্রধান কারণ হলো সতর্কতা অবলম্বন। যেন সে গ্রামে সংক্রামক রোগ থাকলে অন্যরা গ্রামটি এড়িয়ে চলেন বা সংক্রামক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি যেন ঐ গ্রামটি এড়িয়ে চলেন। আদাম বন করলে গ্রামবাসীদের কিছু সতর্কতা বা নীতি পালন করতে হয়। যেমন কোন কিছু মাটিতে হেছঁতে নেয়া যাবে না, দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা করা যাবে না, সন্ধ্যার সময়ে বড়ো ধরণের শব্দ করা যাবে না ইত্যাদি। অনেক সময় ভিন্ন কারণে আদাম বন করা হয়ে থাকে।
চাকমাদের আরেকটি পূজা হলো এদা দাগা। নিম্নে এদা দাগা সম্পর্কে বলা হয়েছে, ‘বাংলায় একটা কথা ভয়ে ‘আত্মরাম খাঁচা ছাড়া’ চাকমাদের মধ্যে এই কথাটার একটা অদ্ভুত বাস্তব নজির আছে। ক্ষেত্রে কিন্তু আত্মরামকে আবার বিশেষ প্রক্রিয়ায় খাঁচায় আনা যায়। এটাকে ভাতদ্যার মতো একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সংস্করণ বলা চলে। হাঁটি হাঁসি পা পা এই বয়সের ছোট ছেলেমেয়ে হঠাৎ যদি খুব ভয় পায়, অনেক ক্ষেত্রে সে ভয়ে একেবারে নেতিয়ে পড়ে। ছেলেটার বাবা, মা, যাদের খুব ন্যাওটা অনেক সময় তাদেরই কেউ রাগের বশে ছেলের উপর তর্জন গর্জন করে এরূপ বিপত্তি ঘটিয়ে থুাকে। তখন সন্তানটি ঘাড় সোজা করতে পারে না, চোখ বোঁজা অবস্থায় ভাতদ্যায় আবিষ্ট হয়ে পড়া লোকের মতো একঘেঁয়েভাবে কাঁদতে থাকে আর শিউরে উঠে। এসময় হয়ত গা সামান্য গরমও হয়ে থাকতে পারে। সহসা এর উপশম ঘটাতে না পারলে ছেলের প্রাণহানির আশংকা থাকে। এ অবস্থাকে বলে এদা জুরানা অর্থাৎ কিনা আত্মরাম খাঁচা ছাড়া হওয়া।৪০
যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় এরূপ ছেলেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায় তাকে বলে এদা দাগা। এই অনুষ্ঠানে কোন দেবতার পূজা হয়না এবং বিশেষ কোন মন্ত্রোচ্ছারণেরও কোন বালাই নেই। অঝা বা যে কোন অভিজ্ঞ লোক এ ব্যাপারে পৌরহিত্য করতে পারে। এ অনুষ্ঠানেও ভাতদ্যার মতো মেজাং এর উপরর আগ কলা পাতা পেতে আদারাহ সাজাতে হয়। তবে সেখানে ভাত তরকারী ইত্যাদি কিছু দিতে হয় না। উপকরণের মধ্যে লাগে মুরগীর বাচ্চা, কলা, আখ, আখের গুড় দুয়েকখানা বেঙ পিঠা আর একটি টাকা। আগের দিনে রুপোর টাকা দেওয়া হত। একাধিক দিলেও তি নাই। অনুষ্ঠান শেষে এগুলোতে সূতা জড়িয়ে কিংবা গেট লাগিয়ে ছেলে কিংবা মেয়ে তাকেই পড়তে দেয়া হয়। যার প্রস্তুত প্রণালী নিন্মরূপ:
মুরগীর বাচ্ছাটাকে জবাই করে সেটার পালক ছাড়িয়ে নাগিয়ে ফেলে মাথাটাকে ঘুরিয়ে এনে বুকের ছিদ্র দিয়ে পেটের ভিতর ঢুকিয়ে দিতে হবে। অনুষ্ঠানের সময় ছেলের মা সন্তানকে কোলে বাড়ীর সদর দরোজায় বসে থাকে আর নিজে মাটিতে অঝা আদারাহ বসায়। আদারাহ বসানো মেজাং এর সঙ্গে সাতগছি সুতো বেঁধে তার অপর প্রান্তে ছেলের মা হাতে ধরে থাকে। আদারাহ যার জন্যে সে যদি ছেলে হয় তবে একখানা গামছা দিয়ে আর মেয়ে হলে একখানা খবং কিংবা খাদি দিয়ে আদারাহ ঢেকে দিতে হয়। সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে গেলে অঝা আদারার ঢাকনা ঈষৎ ফাঁক করে এদা ডাকে। পাত্তুরু-তরু, ত বাবে কেচকেজেয্য, তম্মা কেচকেজেয়্যে ইত্যাদি ইত্যাদি। যার ভাবার্থ হলো তোকে বাপ শাসিয়েছে মা খেদিয়েছে এখন তারা তোকে কলা দিয়েছে, আখ দিয়েছে, আয় আয় তুই বুঝে নে। অঝা একখানা গামচা দিয়ে ডাকার মতো করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে থাকে এভাবে যতণ না একটা মাছি বসলে। তখন আদারাহ তুলে ছেলেকে গচানো হয়। অর্থাৎ তার সামনে ধরা হয়ে থাকে। সে সেখান থেকে যা খুশী একটা কিছু তুলে নেয়। তারপর ভালো হয়ে যায়।’ -বঙ্কিম কৃষ্ণ দেওয়ান
পার্বত্য বৌদ্ধদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে এ লৌকিক পূজা-অচনা ও অনুষ্ঠানাদি হয়ে আসছে। বর্তমান পার্বত্য বৌদ্ধরা অনেক সচেতন ও আধনিক শিায় শিতি হচ্ছে এবং ক্রমান্বয়ে এ সব কুসংস্কার ও লৌকিক ক্রিয়াকর্ম ও পূজা-অর্চনা পরিত্যাগ করে সম্যক ও যুক্তিনির্ভর ধর্মের আচরণে সচেষ্ট।
খাদ্যাভ্যাস : চাকমাদের খাদ্যাভ্যাস বাঙালি থেকে ভিন্ন ধরণের। খাদ্যাভাসের বিষয়ে চাকমাদের কোন সংস্কার নেই। চাকমাদের প্রধান খাদ্য ভাত। তারা সচরাচর শুকুর, মুরগি, ছাগল এবং বিভিন্ন বন্য প্রাণী ও পশুপাখির মাংস খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে থাকে। মাছ, শুটকি, কাঁকড়া, চিংড়ি, হাঙ্গর, ছিদোল (নাপ্পি) এবং বাঁশের অংকুর, বেতের ডগা, ওল, জুম চাষের বিভিন্ন সবুজ শাক সবজি খাদ্য তালিকায় প্রধান। তাদের খাদ্য রন্ধন প্রক্রিয়া ও স্বাদ বাঙালি খাদ্যের স্বাদ থেকে একটু ভিন্ন রকম। চাকমা সমাজে বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠানে এবং কর্মব্যস্ততা শেষে নিত্য কিংবা মাঝে মাঝে মদ পানের রীতি আছে। চাকমারা নিজেরাই ঘরে মদ তৈরী করে। এটা সমাজে স্বীকৃত এবং ইহা একটি অপরিহার্য পানীয়।৪১
মদ চাকমাদের অতি প্রয়োজনীয় একটি পানীয়। চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও সামাজিক প্রথায় মধের ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে দেখা যায়। সাধারণত মদের তিনটি রূপ দেখা যায়। যেমন- ১. মদ যা এক চুয়ানি ও দুচুয়ানিতে গুণগতমান দ্বারা ভাগ করা, ২. জগরা, আর ৩. কানজি। জগরা বিনি চাউল দ্বারা তৈয়ার করা হয়। কানজি এবং মদ সাধারণ চাউল দ্বারা প্রস্তুত করা হয়। চাকমাদের চুঙলাঙ পূজায় মদ লাগে। অতীতে বিবাহের ভোজের আগে উপস্থিত অতিথিদের এক চুমুক মদ দিয়ে আপ্যায়ন করা হতো। গ্রামাঞ্চলে এখনো এর সীমিত ব্যবহার রয়েছে। মৃতদেহ পোড়ানোর সময়েও ওঝারা মদ ব্যবহার করেন।
চিকিৎসা শাস্ত্র : চাকমারা নিজস্ব চিকিৎসা শাস্ত্র দ্বারা সমৃদ্ধ। চাকমা ভাষায় এটাকে তালিক শাস্ত্র বলা হয়। তালিক শাস্ত্র নিয়ে যারা চিকিৎসা কাজ করে তাদের বৈদ্য বলা হয়। সচরাচর বনজ ননান গুল্ম, লতাপাতা থেকে চিকিৎসার কাঁচামাল বা তালিক বানানো হয়। এছাড়া বিভিন্ন প্রাণী থেকেও চিকিৎসার কাঁচামাল সংগ্রহ করা হয়।৪২ অনেক সময় শুধু মন্ত্র দিয়েও চিকিৎসা করা হয়। চিকিৎসা ব্যতীত নানান কাজে চাকমা বৈদ্যরা মন্ত্র ব্যবহার করেন। যেমন- শিকার মন্তর, ফি বলা বা আপদ তাড়ানোর মন্ত্র, দুধ পিড়া মন্ত্র, হলুদ পড়া মন্ত্র, নুনপড়া মন্ত্র, চিগোনগুড়ার বমি প্রভৃতি।
ম্রোদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও কয়েকটি উৎসব : ম্রোদের জীবনচর্যা এবং কর্ম প্রক্রিয়ার অধিক বিচারে তাদেরকে প্রকৃতি ও সর্বপ্রাণবাদী বলা হলেও বর্তমানে তারা বেশির ভাগ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, অনেকে খ্রিষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হচ্ছে। তবে আবার অনেক তাদের নতুন ধর্মক্রামায় অনুরক্ত। প্রকৃতি পূজা, ম্রোরা প্রাচীনকাল থেকে বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী হলেও জীবনচর্চা ও কর্ম প্রক্রিয়ায় প্রকৃতি পূজার অনুসারী। তারা বৃপূজা, পাথর পূজা, মানত করা, গো হত্যা, জীবজন্তু বলি ইত্যাদি করে থাকে। অনেক সময় নানা কুসংস্কারে রীতি প্রতিপালন করেন। তারা আচার আচরণে আদিকালের।
ম্রোরা প্রধানত পাহাড়ে জুমচাষ করে জীবন নির্বাহ করে। খাদ্য হিসাবে ভাত প্রধান মাংস হিসেবে বন্য পশু পাখি, মুরগী, শুকর তাদের প্রিয় খাদ্য। এছাড়াও বিভিন্ন জীবজন্তু, গরু, কুকুর, সাপ, হরিণ, গিরাগিটি প্রভৃতি খায়। রোগব্যাধি হলে বিভিন্ন জীবজন্তু বলি দিয়ে বৃপূজা, পাথর পূজা, দেবতা পূজা ও মানত করে থাকে এবং মুক্তি কামনা করে। মুরুংদের দেবতার নাম ওরেং এবং উৎসবের নাম মুৎসলোং। ম্রোরা নিজেদের বৌদ্ধধর্ম বিশ্বাসী বলে দাবি করলেও অন্যান্য ধর্মের মতাদর্শেও বিশ্বাসী, ম্রোদের গ্রাম, বৌদ্ধ বিহারে (ক্যাং) নেই বললেই চলে। তারা সাংগ্রাইং হলে অবশ্যই বৌদ্ধ বিহারে যায়।
ম্রোদের বিভিন্ন উৎসব রয়েছে। যেমন- সুরাইলা পই, নিংসার কিয়োরী পই (নববর্ষ উৎসব), রামোলা পই/ত-থোয়াক পই (বনবাস উৎসব), লুদলা পই/নিংমানাই খাং পই (বাৎসরিক বিশ্রাম উৎসব), প্রাতলা পই/নিংচুর পই (বৎসর বিদায় উৎসব), তাংফুং (ধর্মীয় কৃত্য)। ফ্রান্সিস বুখানন বলেন, ম্রোরা ঈশ্বর, ঠাকুর রাম খোদার উপাসনা করে না, শুধু মহামুনির (বুদ্ধের) পূজো করে।৪১ ম্রোদের প্রধান উৎসবের নাম চিয়াসদ পই। ‘চিয়া’ শব্দের অর্থ হচ্ছে গুরু। ‘সদ’ শব্দের অর্থ ‘বল্লম’ এবং ‘পই’ বলতে নৃত্যানুষ্ঠান বোঝায়। জুম চাষের ফসল ঘরে তোলার পর মুরং পল্লীতে চিয়াসদ পই অর্থাৎ গো হত্যা নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। সদ্য বিবাহিত তরুণী ছাড়া এ নৃত্যানুষ্ঠানে সব বয়সের মুরং নারী পুরুষ অংশ নিয়ে থাকে। মুরংদের দেবতার নাম ‘থুরাই’। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মোফাজ্জলুল হক কর্তৃক ম্রো জনগোষ্ঠির কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ‘ম্রোচেট’।
ক্রামাধর্ম : ক্রামাধর্ম ম্রোদের স্বীয় ধর্ম, এ ধর্মের মূলকথা হলো একতা, সততা ও নিষ্ঠা। এ তিনটি নীতি প্রতিটি ম্রো শুনুক, বিশ্বাস ও নিঃশ্বাসের দ্বারা পালন করার জন্য ক্রামাধর্ম প্রবক্তা মেনলে ম্রো আহবান জানান। ১৯৮৪-৮৫ সালে বান্দরবানে লামার পোড়াপাড়ায় এ ম্রো কৃতি সন্তান ক্রমাধর্ম প্রবর্তন করেন। ম্রোদের ধর্ম বিশ্বাস ও আদর্শিক জীবন গঠনে তিনি এ ধর্মমত প্রচার করেন। তিনি ম্রো জাতির জন্য বর্ণমালাও আবিষ্কার করেন। ধর্মীয় উৎসবের সময় বা ধর্ম পালন ও ছুটির দিবসে তারা প্রাণী হত্যা করেন না। প্রয়োজন ছাড়া প্রাণী হত্যা নিষেধ। সারা বছরে ৩ বার ধর্মীয় উৎসব পালন করে থাকে। ম্রোদের মধ্যে সারা বৌদ্ধধর্ম ও খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারী তার স্ব স্ব ধর্মের বিধি বিধান পালন করে থাকেন। ম্রোদের পরিবারে কোন শিশু জন্মগ্রহণ করলে সাতদিন পর শিশুর নাম রাখা হয়। তখন ধাত্রী ও গ্রামের গণমান্য ব্যক্তিদের নিয়ন্ত্রণ করে আশির্বাদ কামনা করা হয়। শিশুটির বয়স ১২ বছর পূর্ণ হলে ‘তাং ফুং’ (ধর্মীয় কৃত্য) করা হয়।৪২ মেনলে ম্রো প্রবতিৃত ম্রো বর্ণমালাতে ব্যঞ্জনবর্ণ ২৩টি ও স্বরবর্ণ ৮টি অর্থাৎ সর্বমোট ৩১টি বর্ণমালা রয়েছে। ম্রো শব্দের নমুনা বাবা-পা, মা-উ, হাত-বাং, চুল-সাম, গরু-চিয়া,মাথা-লু প্রভৃতি।
ম্রোদের গরু হত্যার অনুষ্ঠান : গরু হত্যা ম্রো উপজাতিদের এক প্রকার বিশেষ ধর্মীয় পূজা, পূজাটি বৈচিত্র্যময়ভাবে পালন করে থাকে। গো হত্যা ম্রো উপজাতিদের একটি ধর্মীয় তান্ত্রিক পূজা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ম্রোদের ভাষায় সৃষ্টি কর্তার সন্তুষ্টির জন্য তারা এ গো হত্যা অনুষ্ঠান করে থাকে। তারা একটা বিশেষ নিয়ম নীতি মাধ্যমে গো হত্যা অনুষ্ঠান করে থাকে। ম্রোদের মাতৃমোচন পদ্ধতি, ম্রো সমাজের আদি বিবাহ প্রথা, ম্রো সমাজে সৎকার প্রথা প্রভৃতির নিজস্ব নিয়মনীতি মাধ্যমে সম্পাদন করে থাকেন।
মুরংরা তাদের উৎসবে ‘পুং’ নামে এক প্রকার বাঁশি বাজিয়ে থাকে। এ বাঁশি পাহাড়ে উৎপন্ন এক প্রকার জংলি লাউয়ের খোল এবং সুরু বাঁশের নল দিয়ে নিজস্ব কারিগরি কলা কৌশলে নিজেরাই তৈরি করে। চৈত্র সংক্রান্তি উৎসবকে মুরংরা ‘কবং পই’ উৎসব বলে। এছাড়াও ‘কংনাত’ নামে শীত ও বর্ষাকালে শহরে দুটি উৎসব উদ্যাপন করে থাকে।৪৫ ম্রোদের প্রাত্যহিক জীবনে জুম চাষের ক্ষেত বা পাহাড়ে শিকার একটি উল্লেখযোগ্য দিক। মুরাংরা সাদারণত জুম েেতর ফসল রা এবং খাদ্য সংগ্রহ করার জন্য ফাঁদ তৈরি করে থাকে। এ ফাঁদে নানা রকম বন্য জীবজন্তু ও পশুপাখি আটকা পড়ে থাকে। এত জুমচাষের ফসলও রা হয় এবং প্রাত্যহিক খাদ্যও সংগ্রহ হয়। শিকারের জন্য তারা বাঁশের বর্শা, তীল, ধনুক প্রভৃতি ব্যবহার করে থাকে। ম্রো জাতিসত্তার এ গো হত্যা অনুষ্ঠান বৌদ্ধধর্মীয়ভাবে গ্রহণীয় কর্ম নয়। এ অনুষ্ঠান তারা সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে করে থাকে।
খুমিদের সামাজিক ও ধর্মীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান-উৎসব
জুমচাষ অনুষ্ঠান : জুমচাষের উপর ভিত্তি করে খুমি সমাজে দুটি অনুষ্ঠান করা হয়। এর একটি ‘লবনা’ এবং অপরটি ‘চৌপলনা’।
লবনা : জুমে বীজবপনের পর যখন চারাগুলো ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করে জুমে তখনও বিভিন্ন, প্রকার আগাছা থাকে। এসব আগাছা মোট তিনবার পরিষ্কার করতে হয়। প্রথমবার পরিষ্কার করার পর অদৃশ্য ধান দেবতা ‘টিটো’ এর উদ্দেশ্যে পূজায় একটি মুরগি ও একজোড়া মুরগির ডিম উৎসর্গ করা হয়। এর ফলে ফসল ভালো ও উৎকৃষ্ট হয়। এ উৎসবই লবনা।
চৌপলনা : বছরের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে জুম থেকে ধান তোলার পর খুমিরা নবান্ন উৎসব করে থাকে। খুমি ভাষায় এ উৎসবের নাম ‘চৌপলনা উৎসব’। এ উৎসব পরিবার ভিত্তিক। কে কবে ধান তোলা উৎসব বা চৌপলনা করবে তা পরিবারের সদস্যদের উপর নির্ভর করে। এটি খুমি সমাজে অন্যতম প্রদান উৎসব।
আরাং চ্যাং : আরাং চ্যাং এর বাংলা অর্থ ‘রাজ উৎসব’ বা রাজমেলা। খুমি আদিবাসী যারা প্রাচীন ধর্মাবলম্বী এ উৎসবটি তাদের কাছে সবচেয়ে বড় উৎসব। যে কেই এ উৎসবটি ইচ্ছে করলেই করতে পারে না। এ উৎসবটি তাদের সমাজে সবচেয়ে ব্যয়বহুল এবং কঠিন নিয়ম-রীতি দ্বারা পালন করতে হয়। উৎসবটি পরিবার ভিত্তিতে করা হলেও এর সামাজিক সার্বজনীনতা ব্যাপক এবং বিশাল। এর আয়োজনও বিশাল। উৎসবটি সাতদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়। যে কোন ব্যক্তি এই উৎসবটি একবার আয়োজন করে থাকলে তার জীবদ্দশায় না হলেও তার সন্তানদেরকে অবশ্যই দ্বিতীয় বারের মতো উৎসবটির আয়োজন করতে হবে। যে পরিবারটি একবার এ উৎসবটি আয়োজনে সমর্থ হয় তার ঘরের প্যাটার্ন, বিভিন্ন কারুকাজ অন্যান্য ঘরের তুলনায় কিছুটা ভিন্ন। সে কারণে ঘরের প্যার্টান, বিভিন্ন কারুকাজ দেখেই তাদের সমাজের যে কেউ সেই পবিারটি শনাক্ত করতে পারে। এ কারণে ঐ পরিবারটি এবং তার বংশধরকে সমাজে উচ্চ মর্যাদার চোখে দেখা হয় এবং সে বংশধরদের তাদের ভাষায় ‘রাজগোষ্ঠি’ বলা হয়।
আ-ওয়া-আনা : খুমিদের বহুলভাবে অনুষ্ঠেয় বা পালিত লোকজ অনুষ্ঠান হচ্ছে ‘আ-ওয়া-আনা’ যাকে বাংলায় বলা যায় পাড়াবন্ধ। এ অনুষ্ঠান মূলত জুন-জুলাই মাসের মধ্যেই সম্পন্ন হয়। জুমের ফসল যখন একটু মাথা উঁচু করে দণিা হাওয়ায় দুলতে শুরু করে তখন এ পূজা করা হয়ে থাকে। মূলত এ পূজার উদ্দেশ্য হলো যাতে ঐ জুমের ফসল খুমিদের সাংবাৎসরিক খোরাক যোগাতে পারে। অনুষ্ঠানটি দু’দিন ধরে চলতে থাকে।
আঁ-তাঁইপাঁ : নতুন ভাত খাওয়ার অনুষ্ঠানে যে চিবিদ (যা খুমি ভাষায় ‘আহমু’ বলে) রাখা হয়, দুপুরে খাবার পর এ চিবিদ বা আহমু খাওয়ার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতার সময় যে হাঁড়িতে আহমু থাকে ঠিক তার বরাবার উপর থেকে একটি রশির সাহায্যে বাঁধা একটা লম্বা বাঁশের চোঙা টাঙানো হয়।
রেইনা, আরেচেইনা বা গোহত্যা উৎসব : এ উৎসবটি সাধারণত নভেম্বর হতে জানুয়ারি মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। জুমে যেন অধিক পরিমাণ ফসল ফলে সে লক্ষে এ উৎসব পালিত হয়। এ উৎসব খুমি সমাজে দু’ভাবে পালিত হয়। যারা মধ্যবিত্ত বা নিন্ম-মধ্যবিত্ত তারা যে গোহত্যা উৎসব উদযাপন করে তাকে ‘রেইনা’ বলা হয় আর সমাজের বিত্তবান বা ধনাঢ্য পরিবারের আয়োজনকে ‘আরেচেইনা’ উৎসব। বর্তমান খুমি সমাজের খ্রিস্টান ও ক্রামা অনুসারীরা এ উৎসব করে না।
ক্রামা ধর্মীয় উৎসব: আগস্ট, ডিসেম্বর, জুন ও মার্চ মাসে বছরে চারবার এই উৎসব হয়ে থাকে। নববর্ষ উদ্যাপন, ক্রামদি বনবাসের উপলক্ষে, বর্ষ বিদায় ও বাৎসরিক বিশ্রাম উৎসব হিসেবে ক্রামা ধর্মানুসারী খুমিরাও এ উৎসবসমূহ পালন করে থাকে। অন্যান্য এলাকায় ক্রামাধর্মানুসারী খুমি ছাড়া অন্য খুমিরা সাধারণত এই উৎসব পালন করে না।
সাংগ্রাইং : বৌদ্ধ ধর্মানুসারী খুমিরা এ উৎসব পালন করে থাকে। তবে মাত্র একদিন নববর্ষ উৎসব উদ্যাপন করে থাকে। এ উপলে ঘরে ঘরে পিঠা তৈরি হয় এবং পাড়ার লোকজনকে খাওয়া দাওয়া করানো হয়।৪৬
পার্বত্য চট্টগ্রামের ুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠির ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার এবং লৌকিকতা থেকে উত্তরণের উপায়
বাংলাদেশের বৌদ্ধ ইতিহাস ও পার্বত্য ক্ষুদ্র জাতিসত্তার উন্নয়ন, সমৃদ্ধি ও অগ্রযাত্রার প্রশংসনীয় পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে হিতকর। কিন্তু বৌদ্ধ জাতির সামগ্রিক প্রোপটের অন্তরালে রয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং তা হলো ইসলাম ধর্ম ও খ্রিস্টানধর্মের বিপুল প্রভাবের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের ভবিষ্যৎ কি? ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জীবন-জীবিকা ও অস্তিত্ব রায় কি হবে? বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধধর্মের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রশ্ন এসে যায়। এর কারণ প্রধানত, প্রথমত: বাংলাদেশের সমগ্র বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রায় অর্ধেকের বেশির বসবাস পার্বত্য চট্টগ্রামে। দ্বিতীয়ত: বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সাল থেকে পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জেলা থেকে যে বিরাট বাঙালি জনগোষ্ঠি পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করে তাতে উপজাতীয়দের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে বিরূপ প্রভাব পরিলতি হচ্ছে।৪৭ তৃতীয়ত: ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জীবন-জীবিকা, শিা, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বলয় বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। চতুর্থত: জম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং ভূমি বিরোধসহ নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে ঋদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিলুপ্তির পখে।
তথ্য পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ক্রমাগত অ-উপজাতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতির অধিকাংশই হলো সম্বলহীন ও ভূমিহীন কৃষক। সরকারের বিশেষ তত্ত্বাবধানে বাঙালিদের চাষপোযোগী সমভূমি ও পাহাড়ী এলাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, আর্থিক অনুদান ও ঋণসহ সব ধরণের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। সে কারণে উপজাতি বৌদ্ধরা ভূমি ও পাহাড়ী জমি ব্যবহার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, হচ্ছে দরিদ্র ও নি:স্ব। পার্বত্য শান্তি চুক্তির পর পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলেও বিভিন্ন পদপে ও কর্মকাণ্ডের কারণে আবার অশান্ত হয়ে উঠছে। বিশেষ করে চুক্তি বাস্তবায়ন্, ভূমি সমস্যা, উপজাতি-আদিবাসী স্বীকৃতি প্রসঙ্গ, উপজাতি বাঙালি দ্বন্দ্ব-সংঘাত, জাতিগত বৈষম্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি ও আচার-আচরণের ভিন্নতা বিষয় প্রকট হয়ে উঠচ্ছে।
পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠিকে নানাভাবে ভয় প্রলোভন দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করছে। অনেকেই নামমাত্র মূল্যে তাদের জমি বিক্রি করে দেয়। অনেকে ছলচাতুরি ও প্রতারণার মাধ্যমে জমি ও পাহাড়ী এলাকা দখল করে নিয়েছে। উপজাতি নারীপুরুষ নির্যাতনের স্বীকার হচ্ছে। ফলে সাম্প্রদায়িক ও সামাজিক অপরাধ ও অবিচার বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁরা শিা-দীা ও অর্থনৈতিক কারণে দরিদ্র, নিঃস্ব ও অসহায়। অর্থনৈতিক দৈন্যতা নানাবিধ কারণে তারা আজ নিজেদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও অস্তিত্বকে হারাতে বসেছে। তাদের অনেকেই আর্থিক সুযোগ-সুবিধা ও প্রলোভনের কারণে ইসলাম ধর্ম ও খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করেছে। বিশেষ করে দাতা সংস্থা ও খ্রিস্টানরা পার্বত্য চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন এলাকায় অনগ্রসর ুদ্র জাতিগোষ্ঠিকে সাহায্য সহযোগিতার নামে খ্রিষ্টধর্মে দীতি করছে। ফলে একদিন এমন অবস্থা হবে বাঙালি ও খ্রিস্টান প্রভাবিত হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব থাকবে না। তাই উপজাতিদের রার বিষয়ে সুশীল সমাজ তথা আদিবাসী পার্বত্য বৌদ্ধদের সচেতন ও আরো ঐতিহ্যবান হওয়া প্রয়োজন।
পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী বৌদ্ধদের আলোকপ্রদীপ পরম শ্রদ্ধেয় সাধনানন্দ মহাথের (বনভন্তে)। তিনি ১৯৭৬ সালে রাঙাগামাটিতে স্থায়ীভাবে অবস্থান করতে থাবেন। মহান পুণ্যপুরুষ, পরমপূজ্য বনভন্তে পার্বত্য অঞ্চলে আবির্ভাবের পর হতে বহু সংখ্যক মানুষকে ধর্ম পথে চালিত করেছেন, ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং অগণিত নারী-পুরুষের করুণ আর্তনাদ, শোক, বিলাপ, মুহ্যমানতা বিদূরিত করেছেন। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের বহু সংখ্যক শিষ্য গড়ে উঠে। অন্যদিকে ধর্ম জাগরণের ফলে সদ্ধর্ম দেশনা শ্রবণ ও ধর্ম-পুণ্য কর্ম সম্পাদনের জন্য মানুষের মাঝে ধর্মীয় চেতনা বৃদ্ধি হেতু রাজবন বিহারের শাখা বিহার নির্মাণের প্রয়োজন পড়ে। গত শতকের নব্বই দশকের মাঝামাঝি হতে এ পর্যন্ত রাজবন বিহারের অনুমোদিত ও অননুমোদিত শতাধিক শাখা বিহার, ভাবনা কেন্দ্র ও অরণ্য কুটির গড়ে উঠেছে। পরম পূজ্য বনভন্তের প্রধান শিষ্য শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির, শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ ভৃগু মহাস্থবির, শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ বুদ্ধশ্রী মহাস্থবির প্রমুখ মহান ত্যাগী ভিুগণ বিভিন্ন শাখা বিহারের সাথে সংশিষ্ট থেকে সাধারণ লোকদের সদ্ধর্ম আচরণ ও অনুশীলনে সবিশেষ অবদান রেখে চলেছেন। তাই যারা দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করতে চান তারা দুঃখ প্রদানকারী অকুশল ও পাপ কর্ম সম্পাদনে সতর্কতা অবলম্বন করে স্বীয় স্বীয় এলাকার বিহারের সাথে যুক্ত থেকে ও বাদ-বিবাদ রহিত হয়ে দান-শীল-ভাবনা র্চচা করতে সচেষ্ট থাকা উচিত। দুর্লভ মানব জীবন লাভ করেও যদি জেনে অকুশল কর্ম হতে বিরত থাকতে পারা না যায়, তবে তা অভ্যন্ত পরিতাপের বিষয় হবে। অকুশল বা পাপ কর্ম সম্পাদন করে কেউ বা সুখী হয় না। রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান- তিন পার্বত্য জেলা এবং ভারতে রাজবন বিহারের শাখা বিহার, ভাবনা কেন্দ্র ও কুটির নির্মিত হয়।
রাখাইন বৌদ্ধদের মধ্যেও অনেক কুসংস্কার, ধর্মীয় ও সামাজিক ক্রিয়াকর্ম, লৌকিক পূজা-পার্বণ ও আচার অনুষ্ঠান রয়েছে। বর্তমান সময়ে কক্সবাজার, পটুয়াখালী, বরগুণা অঞ্চলে রাখাইন বৌদ্ধদের বসতি হীন থেকে হীনতর হচ্ছে। এমন সময় আসবে এসব অঞ্চলে কোন রাখাইন বৌদ্ধ পরিবারের বসতি থাকবে না, থাকবে না কোন বৌদ্ধ বিহার ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি। এদের রায় ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি পুনরুদ্ধারে যথাযথ পদপে গ্রহণ করা প্রয়োজন।
সার্বিক পর্যালোচনা মতে, ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার এবং লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান লোকজীবনের এক অত্যাবশ্যকীয় অন্বয়। মানুষের ধীকল্প (idea), চিন্তা, আভ্যাস, রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান ও চর্যাবোধ পুনশ্চভাবে সপর্যাগত সংস্কৃতিতেই পর্যায়ক্রমিক প্রভাবিত। বিধিবদ্ধ নিয়মনীতি ও শাস্ত্রীয় বিধান থাকলেও বিভিন্ন কুসংস্কার ও লৌকিকতা মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এমনকি চর্যার ভিত্তিমূল হিসিবে অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। সকলে আষ্টে পৃষ্টে এই প্রায়োগিক লৌকিক কৃষ্টি সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত। এর মাধ্যমেই একটি জাতিগোষ্ঠির বিকাশ ও আত্মপরিচয়। জনজীবনে এসব কীভাবে বহুমাত্রিকভাবে প্রভাবিত করে এবং চর্যায় নিবিষ্ট হয় তার সম্যক পর্যেষণা। সমতলে বসবাসকারী বাঙালি বড়ুয়া বৌদ্ধ ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী বৌদ্ধ, পটুয়াখালী, বরগুণা, কক্সবাজারের রাখানই বৌদ্ধ এবং উত্তরবঙ্গের ওঁরাও বৌদ্ধদেরও একই অবস্থা। নৃতাত্ত্বিক ক্ষুদ্র জাতিসত্তা হিসেবে সমঅধিকার ও আত্মমর্যাদায় বসবাস করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। দিন দিন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বৌদ্ধরা শিল্প সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক, ভূমি, অস্তিত্ব রা, আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সামাজিক ও ধর্মীয় নানা সমস্যায় জর্জরিত। বর্তমানে ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার এবং লৌকিক আচার অনুষ্ঠান ছাড়াও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকেরা বিশেষত খ্রিষ্টান ও ইসলাম ধর্মে দীতি হয়ে যাচ্ছে। এর জন্য যথাযথ ব্যবস্থা ও সঠিক পদক্ষেপ অত্যন্ত প্রয়োজন।
তথ্যনির্দেশ :
১. আবদুল হক চৌধুরী, কক্সবাজার ইতিহাস সমাজ সংস্কৃতি, (চট্টগ্রাম, ১৯৮৪), পৃ. ৮৩
২. শ্রী শরৎ কুমার রায়, বৌদ্ধ ভারত, (কলকাতা, ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৬৫
৩. আহমদ শরীফ, প্রচ্ছ্ন্ন বৌদ্ধ সাহিত্য, সাহিত্য পত্রিকা, দ্বিতীয় সংখ্যা, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৩৫
৪. অলৌকিক নয় তবুও অলৌকিক (প্রবন্ধ), অধ্যাপক রতি মহাথের, স্মরণিকা, বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশন, (ঢাকা, ১৯৯৫), পৃ. ৪৫
৫. মুরারি ঘোষ, পাক্ আধুনিক বঙ্গ সংস্কৃতি, (কলকাতা, ১৯৮৩), পৃ. ২৩৬
৬. ড. তৃপ্তি ব্রহ্মা, বাংলার ইসলামী সংস্কৃতি, (কলকাতা, ১৯৮৭), পৃ.।
৭. ভিক্ষু সুনীথানন্দ, বাংলাদেশে বৌদ্ধ ভাস্কর্য, (এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৯), পৃ. ১৮-১৯
৮. ড. সুকোমল চৌধুরী, বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, (সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৭৬
৯. বিপ্রদাশ বড়ুয়া, শ্রামণ গৌতম, (জানুয়ারি, ঢাকা, ১৯৯৬), পৃ. ৪৬
১০. 10. Sir Charles Eliiot, Hinduism and Buddhism, (London, 1987)
১১. ভিক্ষু সুনীথানন্দ, বাংলাদেশে বৌদ্ধ বিহার ও ভিক্ষু জীবন, (বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫), পৃ. ২৩৪
১২. বৌদ্ধ মহাসংগীতি (প্রবন্ধ), শান্তি প্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, অর্ঘ্য, (চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহার, ২৩ অক্টোবর, ১৯৯২)
১৩. বঙ্কিম কৃষ্ণ দেওয়ান, চাকমা পূঁজা পার্বণ, (রাঙ্গামাটি, ১৯৮৯), পৃ. ১৮/পূর্বোক্ত, বৌদ্ধ ভারত, পৃ. ৪৮
১৪. পূর্বোক্ত, ড. সুকোমল চৌধুরী, বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, পৃ. ১৯
১৫. এম. তবিবুর রহমান, বেহুলার বাসার ঘরের ইতিহাস, (রাজশাহী, ১৯৮৯) পৃ. ২৫
১৬. ড. আশা দাশ, বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য, (ক্যালকাটা বুক হাউজ, কলকাতা, ১৯৬৯), পৃ. ৯২/৯৩
১৭. পূর্বোক্ত, বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য, পৃ. ৯৪
১৮. বৌদ্ধধর্মের তান্ত্রিকতা (প্রবন্ধ), জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, কৃষ্টি- – Kristi (মে, ঢাকা, ১৯৯৫/ ২৫৩৯ বুদ্ধাব্দ)
১৯. গোপেন্দ কৃষ্ণ বসু, বাংলার লৌকিক দেবতা, (নভেম্বর, কলকাতা, ১৯৯৩), পৃ. ১১২
২০. পুরাণ (হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থ)।
২১. আব্দুল হক চৌধুরী, চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা, (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮), পৃ. ১৮৭
২২. বিশুদ্ধাচার মহাস্থবির, সীবলী ব্রতকথা, (চট্টগ্রাম, ১৯৩৭), পৃ. ১৪
২৩. 23. Dr. Dilip Kumar Barua & Dr. Mitsaru Ando, Syncretism in Bangladeshi Buddhism, (Nagoya, Japan, 2002), pp. 121,150
২৪. সাক্ষাৎকার : সুবল চন্দ্র বড়ুয়া, গ্রাম- বিনামারা, ডাক- চিরিঙ্গা, থানা-চকরিয়া, জেলা-কক্সবাজার
২৫. সাক্ষাৎকার : বেন্জু বড়ুয়া, গ্রাম- শীলকূপ, ডাক- মনকিচর, থানা-বাশঁখালী, জেলা-চট্টগ্রাম
২৬. ধর্মরত্ন মহাথের, মহাপরিনির্বাণ সূত্র (অনু.), (চট্টগ্রাম, ১৯৪৯), পৃ. ১৮৫
২৭. 27. Ibid, Syncretism in Bangladeshi Buddhism, p. 143
২৮. পূর্বোক্ত, বাংলাদেশে বৌদ্ধ বিহার ও ভিু জীবন, পৃ. ২৪৩
২৯. ড. বেণীমাধব জন্মশত বার্ষিক স্মারক গ্রন্থ, জগজ্জ্যোতি, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা, (কলকাতা, ১৯৯২), পৃ. ১৭
৩০. আবদুল হক চৌধুরী, চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা, চট্টগ্রাম, পৃ. ১৮৭
৩১. পূর্বোক্ত, চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা, পৃ. ১৮৮
৩২. 32. Ibid, Syncretism in Bangladeshi Buddhism, p. 172
৩৩. ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া, বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মালম্বী বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর লোক সংস্কৃতির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, পি-এইচ. ডি অভিসন্দর্ভ, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭), পৃ. ২০২
৩৪. ড. দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া, বাঙ্গালী বৌদ্ধদের ইতিহাস, ধর্ম ও সংস্কৃতি, (চট্টগ্রাম, ২০০৭), পৃ. ২৩২
৩৫. দীনেশ চন্দ্র সেন, সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ, (কলিকাতা, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৩৯
৩৬. সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃতি ও সংস্কৃতি, উসাই, (রাঙ্গামাটি, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৪), পৃ. ৪১
৩৭. 37. Ibid, Syncretism in Bangladeshi Buddhism, p. 143-150
৩৮. শরদিন্দু শেখর চাকমা, চাকমা বৌদ্ধ সম্প্রদায় : উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও বর্তমান আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা (প্রবন্ধ), অনোমা, রজত জয়ন্তি সংখ্যা, (চট্টগ্রাম, ২০০৯), পৃ. ২১৩
৩৯. নবকুমার তনচঙ্গ্যা, পার্বত্য চট্টগ্রামের ধর্মের জাগরণে শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাস্থবির ও বর্তমান প্রেতি (প্রবন্ধ), দীপ্তি, (রাঙ্গামাটি, ২০০৮), পৃ. ১২৭
৪০. তনয় দেওয়ান, চাঙমাটারা, প্রত্যয়ন, (খাগড়াছাড়ি পার্বত্য জেলা, ২০০৭), পৃ. ৩০
৪১. বিপ্রদাস বড়ুয়া, পার্বত্য চট্টগ্রামের সাহিত্য ও সংস্কৃতি (সম্পা.), (দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩), পৃ. ১২৪-১২৫
৪২. পূর্বোক্ত, তনয় দেওয়ান, চাঙমাটারা, (রাঙ্গামাটি, ২০০৭), পৃ. ৩৯
৪৩. ভেলাম ভান সেন্দেল (সম্পা.), দক্ষিণপূর্ব বাংলায় ফ্রান্সিস বুখানন, (আইসিবিএস, ঢাকা, ১৯৯৪), পৃ. ৯০
৪৪. ইয়ং রিং ম্রো, ম্রোদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও কয়েকটি উৎসব (প্রবন্ধ), সমুজ্জ্বল সুবাতাস, (বান্দরবান, ২০০৫), পৃ. ৪৭
৪৫. সালাম আজাদ, শান্তি চুক্তি উত্তর চট্টগ্রাম ও আদিবাসী প্রসঙ্গ, (হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০১), পৃ. ১১৩
৪৬. চেীধুরী বাবুল বড়ুয়া, খুমিদের সামাজিক ও ধর্মীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান-উৎসব (প্রবন্ধ), সমুজ্জ্বল সুবাতাস, (বান্দরবান, ২০০৮), পৃ. ১০৭
৪৭. ড. নীরু কুমার চাকমা, বুদ্ধ তাঁর ধর্ম ও দর্শন, (মিনার্ভা পাবলিকেশন, ঢাকা, ১৯৯৬), পৃ. ১৬২
----------------------
নির্বাণা পিস ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত 'নির্বাণা' থেকে
nirvanapeace.com






















No comments